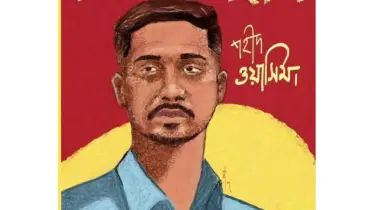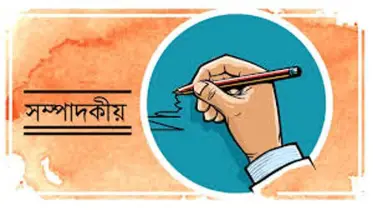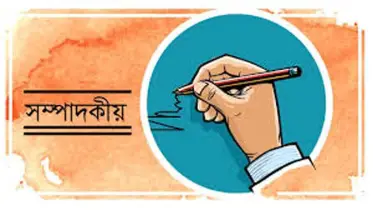শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা
বাণীবন্দনার আজ মাহেন্দ্রক্ষণ। মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী। জৈন মতে জ্ঞান পঞ্চমী। শুক্ল অর্থ সাদা। ভালো গুণের প্রতীক। পবিত্রতার প্রতীক, স্বচ্ছতার প্রতীক, নির্মলতার প্রতীক। হংস বাহনা দেবী অ-জ্ঞানের কুয়াশা ভেদ করেন। জ্ঞানের মশাল জ্বালেন। শুধু বিদ্যা, সংগীত বা চারুকলার দেবী নন, সরস্বতী উর্বতারও প্রতীক। তবে বাংলা জনপদে তিনি প্রধানত বিদ্যার্থীর দেবী, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। জগৎকে জ্ঞান, শিল্প ও সৌন্দর্যের দীপশিখায় আলোকিত করেন এমন প্রত্যাশায় ঘরে ঘরে সরস্বতী পূজা এতটাই জনপ্রিয়।
মনে পড়ে, পূজার আয়োজন হতো দেশের গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, স্কুল-কলেজ, বাড়ি-বাড়ি, পাড়ায়-পাড়ায়। পরম্পরা সাক্ষ্য দেয়- সরস্বতী বিদ্যায়তনেই প্রবলভাবে সমাদৃত। তবে আমাদের অভিজ্ঞতাটা ছিল ভিন্ন। স্কুলে পূজার আয়োজন দেখিনি। হতে পারেÑ সনাতন ধর্মের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে আমাদের স্কুলে অনেক কম ছিল। তবে স্কুল সংলগ্ন মাঠে পূজার আয়োজন হয়েছে মহাসমারোহে। সবচেয়ে বড় কথা, সে আয়োজনের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিসর্জন পর্যন্ত অনুষ্ঠানের সব পর্বে হিন্দু-মুসলমান সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশীদারিত্ব ছিল।
পূজাকে উপলক্ষ করে পূজার আগে-পরে মাসজুড়ে বহু রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী আমাদের মধুর শৈশব। শীতের বিদায় তখন আসন্ন। জগৎজুড়ে নতুনের আগমন বার্তা। সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে উঠছে প্রকৃতি। জেগে উঠছে বনবৃক্ষ। আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলছে সৃষ্টির উল্লাস।
স্কুলের পূজা না হলেও আমাদের হেড স্যার উদ্যাপন কমিটি করে দিতেন। একজন সতীর্থের কথা বারবার মনে পড়ে। গম্ভীর প্রকৃতির বন্ধুটিকে ক্লাস সেভেনে তিন বার থাকতে হয়েছিল। অভিভাবকসুলভ হাবভাব ও চলাফেরার জন্য তার দিকে ছাত্র-শিক্ষক সবারই আলাদা নজর ছিল। স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে একবার ‘স্বরচিত’ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। স্যার তাকে কমিটির ‘মহাসচিব’ করেছিলেন। তার কর্মবণ্টনের কেতাবি ভঙ্গি, কর্মীদের টিএ-ডিএ প্রদান, কঠোর শাসনের আরোপিত মুদ্রা ও কর্মিসভায় গুরুগম্ভীর ভাষণ- নিমেষেই তাকে নির্দোষ আমোদের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিল।
বাঙালি চরিত্রের অন্তর্গত রসবোধ ও স্বভাবগত পরিমিতি সংস্কৃতির এক অনতিক্রম্য ঐশ্বর্য। গ্রিক প-িত অ্যারিস্টটল সাংস্কৃতিক মান নির্ধারণে এই বৈশিষ্ট্যকে নির্ণায়ক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূণ বিষয় হলো, সাম্প্রদায়িক দূষণ তখনও সমাজকে কাবু করতে পারেনি। বিভাজনের বলিরেখা তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমাদের মনেই হয়নি, সরস্বতী পূজা বিশেষ কোন ধর্মের। শিশু হতে বৃদ্ধ, শিক্ষক হতে মজুর, অফিসার হতে কর্মচারী-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই উৎসবের অংশীদার।
হেড স্যার থেকে শুরু করে অনেক সদস্যই ছিলেন ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের। কিন্তু আমরা ছিলাম উৎসবের জয়রথে সবাই সহযাত্রী। কমিটি গঠন, ম-প নির্মাণ, চাঁদা তোলা থেকে বিসর্জন- সবখানেই দেখেছি একাত্মতা। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির এটাই হয়তো সঠিক চিত্র।
প্রস্তুতির প্রথম পর্বেই থাকত প্রতিমা নির্মাণের পরিকল্পনা। বৈদিক যুগে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। তবে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সরস্বতীর প্রাচীনতম মূর্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। শুধু হিন্দু নয়, বৌদ্ধ, জৈনসহ বিভিন্ন ভারতীয় মতাদর্শিক প-িতদের উপাস্য দেবতা হয়ে উঠেছিলেন দেবী সরস্বতী। শতাব্দীর পর শতাব্দী জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধার সাধনায় মগ্ন থেকেছেন ভারতীয় ঋষি, তপস্বী ও যোগীরা। সময়ের বিবর্তনে মূর্তির গঠন ও স্থাপত্য শৈলীতেও আসে বৈচিত্র্য। উৎসবের কাঠামো ও দর্শনেও ছোঁয়া লাগে পরিবর্তনের। রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব এমনকি বাঙলার নবজাগরণও দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিকতা নিয়ে আসে।
আধ্যাত্মিকতা ফিকে হয়ে আসে। উৎসব সামাজিক পরিসরে কর্তৃত্ব শুরু করে। জীবনের উদ্যাপন কার্যত বিস্ফোরিত কলেবরে ধরা পড়ে। ম-প সজ্জা থেকে প্রতিমা নির্মাণÑ সর্বত্রই সাবেকি ভাবনা সরিয়ে আসন গেড়েছে সমকালীন চেতনা। আশপাশের পরিচিত বিষয়ের মাঝেই নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার ব্যাকুলতা। গৎবাঁধা জীবন থেকে মুক্তির আস্বাদ। ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতায় উত্তরণে সঙ্গ দিয়েছে শিল্পভাবনা, কল্পনা ও বিজ্ঞানের মিশেল। কোথাও হস্তশিল্পের চোখ ধাঁধানো জৌলুস, কখনও যুক্তির শৃঙ্খলে আধ্যাত্মিকতা। পশ্চিম বাংলার রুচি, শিল্পমান কিংবা পরিবর্তনের হাওয়া ৮০-এর দশকেই কাঁটাতার পেরিয়েছে অবলীলায়।
মণ্ডপের কারুকাজে কলকাতার ঢেউ আছড়ে পড়লেও প্রতিমার গড়নে আমাদের মডেল ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ট্রেনে চড়িয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিমা আনার সুখকর স্মৃতি আজও এক অপার্থিব কল্পজগতের সন্ধান দেয়।
পূজার প্রসাদও ছিল উৎসবের এক বড় আকর্ষণ। মনে আছে, প্রথাগত খিচুড়ি, মিষ্টি বা ফলমূল আমাদের প্রসাদের আইটেমে থাকত না। নাটোর থেকে আনা হতো অবাক, রাঘবশাহী ও রসকদম্ব। লোভনীয় মিষ্টির এসব কার্টন ট্রেনে করে বয়ে আনায় কারও কোনো ক্লান্তি দেখিনি। পূজার সমাপ্তি পর্যন্ত তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা ছিল নিবেদিত সারস্বতদের পবিত্র দায়িত্ব। একদিকে চলত ম-প শিল্পীর অন্তিম রংতুলির অবিশ্বাস্য কারুকাজ; অন্যদিকে বাহারি আলোর রোশনাই।
প্রযুক্তির কারসাজিতে পূজা প্রাঙ্গণ সত্যিই এক মোহনীয় রূপে আবির্ভূত হতো। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষের বৌদ্ধিক মনোভূমিতে রাজত্ব করেছে নান্দনিকতা। যা সৃষ্টি হয় সহজাত সুকুমার বৃত্তি ও যুগলব্ধ যুক্তিশীলতা থেকে। সব শিল্পকর্মেই জীবন্ত হয়ে ওঠে সমকালীন মানুষের বুদ্ধি, কল্পনা, রুচি, স্বপ্ন এবং সৃষ্টিশীলতার সক্ষমতা। সবচেয়ে বড় কথা সততা। বিমূর্ত দৃশ্যকল্পকে সহসাই বাস্তব জীবনে নামিয়ে আনতে পারেন একমাত্র শিল্পীই।
পূজার জন্য ফুল তুলতে যাওয়া আমাদের জন্য ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। দল বেঁধে সাজানো বাগানে চুপিসারে ফুল তোলা। নিদ্রামগ্ন দারোয়ানদের পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে ফুলবাগানে অভিযান ছিল কৈশোরের এক মস্ত বড় অ্যাডভেঞ্চার। একের পর এক আমরা পরম যত্নে পরিপাটি বাগানগুলো তছনছ করে ফেলতাম। শুধুই কি ফুল, লোভনীয় ফলগুলো যখন হাতের নাগালে এসেছিল, সবাই কি নিজেকে সংযত করতে পেরেছিল-মনে করতে পারি না।
আকাশে মঘা নক্ষত্রগুলোর ঔজ্জ্বল্য ততক্ষণে ফিকে হয়ে এসেছে। পুব আকাশে দিগন্তরেখা ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। আমাদের ফুলের সাজিগুলোও হলুদ গাঁদা, ডালিয়া, গোলাপ, পলাশ- কত নাম না জানা ফুলে ফুলে কানায় কানায় হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ। সুঠামদেহী ক্লান্ত দারোয়ানের নিদ্রামগ্নতা নাকি তাদের পরোক্ষ প্রশ্রয়Ñ ফুলের মিশন কোন জাদুতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতো- বলতে পারি না।
পূজার দিনে পরিপাটি তারুণ্যের অবিশ্রান্ত স্রোত বয়ে চলত মণ্ডপ অভিমুখে। আজও সে দৃশ্য অমলিন। তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিপার্শ্বে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সাজগোজেও বদল এসেছে। সরস্বতী পূজা, বিজয় দিবস কিংবা নববর্ষে বাঙালি আবার ফিরে যায় শেকড়ের টানে। ঢাকা থেকে নিউইয়র্ক- সবখানেই লাল পেড়ে সাদা শাড়িতে বাঁধা পড়েন বাঙালি নারী। যুবকরা গায়ে চড়ান লাল-হলুদ-সবুজ পাঞ্জাবি। সত্যি বলতে কি, অনাদরে পরিত্যক্ত বাঙালি সংস্কৃতির অনেক উপকরণ ফিরিয়ে দেয় এমন সব ধর্মীয় উৎসব।
প্রযুক্তির হাতছানি আর সামর্থ্যরে উল্লম্ফনে চারপাশটা এখন অনেকটাই বদলে গেছে। সংস্কৃতির ওপর এর আঁচ পড়ে বটে, কিন্তু তা টিকে থাকে ঠিক প্রকৃতির মতো। আজও যেমন নির্মল আকাশে ছেঁড়া মেঘগুলো ভেসে চলে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। শিরশিরে বাতাস আর মায়াবি রোদ গায়ে মেখে ঢল নামে মানুষের। ম-পের একপ্রান্তে চলে মায়ের চরণে ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি, অন্যদিকে গল্পপ্রিয় তারুণ্যের বাধাহীন আড্ডা। এরপর প্রসাদ হাতে যার যার ঘরে ফেরা।
সেই চেনা ছক, ক্লান্ত পথ, জানা বৃত্ত। উৎসবের ধারণায় সম্প্রীতির বার্তা নিহিত থাকে, সে বার্তার বাহক প্রকৃতি নিজেই। প্রত্যাশা থাকবে, মানুষ প্রকৃতির মতোই সহনশীল হোক। আর জীবনের জয়রথ এগিয়ে চলুক অনন্তের পথে।
লেখক : ট্রেজারার
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা