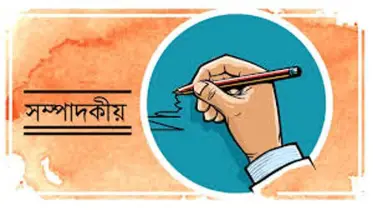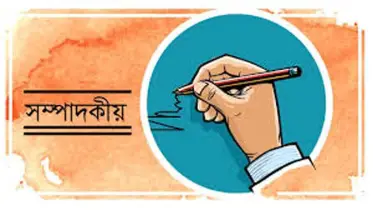যে দাবি ছিল বাংলাদেশের মানুষের বছর কয়েক আগে তাই উঠে এসেছিল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের কণ্ঠে। সাম্প্রতিক বন্যায় প্রায় ডুবে যাওয়া বিহারের বন্যা পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধানের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে ফারাক্কা বাঁধ তুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। বিহারে বছরের পর বছর ধরে এ রকম বন্যা হচ্ছে। সাংবাদিকদের বলেছিলে ন, ‘ফারাক্কা বাঁধের কারণে গঙ্গার বিপুল পরিমাণ পলি জমে। আর এ কারণে প্রতি বছর বিহারে বন্যা হচ্ছে। এর স্থায়ী সমাধান হলো ফারাক্কা বাঁধাটাই তুলে দেয়া’। ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশ এ কথাই বলে আসছে ভারতকে। পদ্মার তলদেশে পলি পড়ে ১৮ মিটারের বেশি ভরাট হয়েছে। এক সময়ে যে পদ্মার ২৫ লাখ কিউসেক পানি ধারণ করার ক্ষমতা ছিল এখন তা অর্ধেকে নেমে এসেছে। পদ্মার বুকে এখন ধু ধু চর। বর্ষায় ভারত থেকে ফারাক্কার গেট খুলে দিলে ধারণক্ষমতার বেশি পানি নিয়ে পদ্মা ভাসিয়ে দেয় আশপাশের এলাকা। বিপন্ন হয় জনজীবন। বিহারের বন্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে ফারাক্কার একশ’ চারটি গেটের একশ’টিই খুলে দেয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। এতে প্রায় ১৫ লাখ কিউসেকের বেশি পানি আসে পদ্মায়। রাজশাহী পয়েন্টে পদ্মার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে। নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়। হাঁস-মুরগি গরু ছাগল নিয়ে পানিবন্দি হন অসংখ্য মানুষ।
নীতিশ কুমার বলেছিলেন, আগে যেসব পলি নদীর প্রবাহে ভেসে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ত এখন ফারাক্কার কারণে সেই পলি নদীর বুকে জমা হয়ে বন্যা ডেকে আনছে। তাই আমি ১০ বছর ধরে বলে আসছি, এই পলি ব্যবস্থাপনা না করলে বিহার কিছুতেই বন্যা থেকে পরিত্রাণ পাবে না। ১০ বছর ধরে পলি ব্যবস্থাপনার কথা বলে বলে বিরক্ত নীতিশ কুমার সেবার বাঁধ তুলে ফেলার কথাই বলে ফেলেছিলেন। আর বাংলাদেশের নদী বিশেষজ্ঞরা বলছেন ৫০ বছর ধরে। খোদ পশ্চিমবঙ্গ থেকেই হয়তো এক সময় এ দাবি উঠবে। কারণ ফারাক্কা বাঁধের মূল উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গার নাব্য বজায় রেখে কলকাতা বন্দর চালু রাখা। তাতে বাংলাদেশের পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও এদের শাখা নদীর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে সেদিকটা তারা উপেক্ষা করে গেছে বরাবর। বাঁধের কারণে গঙ্গার ভাটি এলাকা বাংলাদেশ অংশে শুধু পানিই কমেনি বদলে গেছে পুরো জীববৈচিত্র্য। মরুময় হয়ে পড়েছে পুরো এলাকা। তবে দীর্ঘমেয়াদে বাঁধের বিভিন্ন ফটকে পলি জমে এখন ভারতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে শুরু করেছে। এখন বিহারে, ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গকেও হয়তো এ বৈরী প্রভাব মোকাবিলা করতে হবে।
বন্যার সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের পরিচয় বহু আগে থেকে। পদ্মার সর্বগ্রাসী বন্যা জনজীবনকে বারবার বিপন্ন করেছে। মহাস্থানগড়ের শিলালিপিতে পাওয়া খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বন্যার উল্লেখকে এ অঞ্চলে বন্যার প্রথম ঐতিহাসিক দলিল মনে করেন ইতিহাসবিদরা। এরপর অসংখ্য বন্যা বহু জনপদ ভাসিয়ে নিয়েছে। ড. নীহার রঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্বে উল্লেখ করেছেন, ‘শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগীরথী-পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস অনুসরণ করলেই বোঝা যায়, এই দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতটীয় ভূ-ভাগে, অর্থাৎ নদী দুটির অসংখ্য খাঁড়ি-খাঁড়িকাকে লইয়া কী তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে যুগের পর যুগ, এই দুটি নদী এবং তাহাদের অগণিত শাখা-প্রশাখা বাহিত সুবিপুল পলিমাটি ভাগীরথী-পদ্মা মধ্যবর্তী খাঁড়িময় ভূ-ভাগকে তছনছ করিয়া বারবার তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। তবে সে সময়ে বন্যা ছিল পুরোপুরি প্রাকৃতিক। এখন বেশির ভাগই মানুষের সৃষ্ট।
॥ দুই ॥
উনিশশ’ চুয়ান্ন সালের বন্যার পর ক্রুগ মিশন পূর্ব পাকিস্তান সফর করে পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ওয়াপদা) গঠনের সুপারিশ করে। উনিশশ’ ঊনষাট সালে ওয়াপদা গঠিত হয়। একই সঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প নেওয়া হয় অনেক। এর পাঁচ বছর পর পানি সম্পদ উন্নয়নে ২০ বছর মেয়াদি একটি মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শুরু হয়। ওয়াপদাকে বন্যা, সেচ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়ার সময় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনকে (বিএডিসি) উফশী ধানের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক বিতরণ জনপ্রিয় ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাজগুলো ষাট দশকের ‘সবুজ বিপ্লব’-এর আওতাভুক্ত ছিল। সবই হচ্ছিল বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ মতো। স্বাধীনতার পর এসব প্রকল্পের মূল্যায়নের তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্পের উদ্যোগ ও কার্যপ্রণালী বর্ণনার দলিলদস্তাবেজ রচিত হয়েছে প্রচুর। কিন্তু মেয়াদ শেষে এসব কি সুফল বয়ে এনেছে তা নিয়ে মূল্যায়ন হয়েছে খুব কম। বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এরপর পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ভূমির উপরের পানি প্রকল্প এবং বিএডিসির আওতায় ভূ-গর্ভের পানি প্রকল্পের প্রতি মনোযোগী হয়। কিন্তু এসব প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন হয়েছে একেবারে কম। অর্থাৎ প্রকল্পের পর প্রকল্প নেওয়া হয়েছেÑ তার জন্য প্রচুর ফান্ড এসেছে কিন্তু কাজ হয়নি তেমন কিছুই। ১৯৮৮ সালের বন্যার পর অ্যালেন সি লিন্ডকুইস্ট কিছু বড় প্রকল্পের ৩০ বছরের প্রকল্প সমীক্ষা করতে গিয়ে বড় বড় শুভংকরের ফাঁকি দেখতে পান। তার নিরীক্ষায় বেরিয়ে আসেÑ ঢাকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অফিস পানি সম্পদ উন্নয়নবিষয়ক একটি প্রকল্পেরও সমাপ্তি রিপোর্ট দেখাতে পারেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্থনৈতিক লাভের ওপর নির্ভর করে প্রকল্পের বিন্যাস হয়েছে। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প এবং বরিশাল সেচ প্রকল্পের মতো বড় দুটো প্রকল্পে খরচের ব্যাপক তারতম্য দেখতে পান তিনি। এ দুটো প্রকল্পের খরচ হেক্টরপ্রতি যথাক্রমে চার হাজার মার্কিন ডলার এবং ৩৬০ মার্কিন ডলার। সাহায্যনির্ভর এসব প্রকল্পে দাতারা তাদের পছন্দমতো কনসালট্যান্ট নিয়োগ দেয়। যোগ্যতা মুখ্য নয়, দাতাদের পছন্দই এখানে শেষ কথা। প্রকল্প ব্যয়ের বড় একটি অংশ কনসালট্যান্টদের ফি হিসেবে দেওয়া হতো। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কনসালট্যান্টদের তুলনায় বিদেশি কনসালট্যান্টদের ব্যয় ২৫ গুণ বেশি। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নামে এ ধরনের সাহায্যনির্ভর প্রকল্পের প্রতি কনসালট্যান্ট, আমলা, প্রকৌশলী সবার লোভনীয় দৃষ্টি থাকে। পানি ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে স্বাধীনতার আগে-পরের উদ্যোগ এ ধরনের ধারাবাহিকতাই চলছে।
গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করা পানি সম্পদ রক্ষা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচারের ঢাক-ঢোল উনিশ শ’ সাতাশি ও আটাশি সালের ব্যাপক বন্যার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারেনি। অথচ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে এ খাতে। আশির দশকের ওই বন্যার পর ‘বন্যা নিয়ন্ত্রণ’ এবং পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হয়। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লন্ডনে একাধিক বৈঠকে মিলিত হন। গুরুত্বপূর্ণ নানান আলোচনা, গুরুগম্ভীর পর্যালোচনা শেষে বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যুগান্তকারী দাওয়াই ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) প্রণয়ন করেন এবং অল্প সময়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব বেরিয়ে পড়ায় দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনার মুখে ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান বাতিল করা হয়। অবশ্য এর বদলে যা গ্রহণ করা হয় তা নতুন আঙ্গিকে ওই ফ্যাপেরই ভিন্ন সংস্করণ। সুতরাং বন্যা নিয়ন্ত্রণে কাজ কি হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।
প্যানেল/মো.