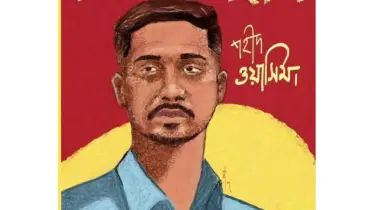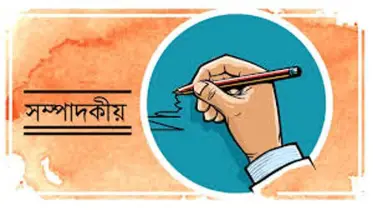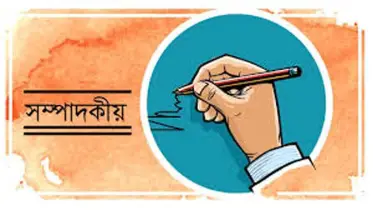“আপনি কি কখনো ‘কার্বন সেল’ বা ‘কার্বন ট্রেডিং’ শব্দটি শুনেছেন?” না শুনলে আপনি একা নন। জলবায়ু আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নতুন প্রজন্মের অনেকেই বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশায়। যদিও এটি জলবায়ু নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে, তবু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি এখনো বেশ রহস্যময়। একবার ভাবুন, কেউ আপনার নামে গাছ লাগিয়েছে, আপনিই জানেন না! কিংবা, আপনি প্রতিদিন হাঁটেন কোনো এক গাছপালা ঘেরা রাস্তায়, আর এই গাছের অস্তিত্ব এখন ‘বিক্রি’ হয়ে গেছে সুদূর ইউরোপের কোনো ইন্ডাস্ট্রির পাপ মোচনের কাজে! অবিশ্বাস্য শোনালেও এটাই হচ্ছে কার্বন ট্রেডিং বা কার্বন অফসেট মার্কেট- এক আজব বৈশ্বিক লেনদেনের গল্প, যেখানে দূষণ হচ্ছে, দায়মুক্তি মিলছে আর আমরা সেই বাজারের একেকটি নিঃশব্দ খুঁটি মাত্র। কার্বন মার্কেটের যুক্তি সোজা- একটি উন্নত দেশ বা কোম্পানি যতটুকু কার্বন নিঃসরণ করে, তার সমপরিমাণ ‘সবুজ’ উদ্যোগ (যেমন গাছ লাগানো, বন সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প) উন্নয়নশীল দেশে করিয়ে নেয়। ফলে হিসাব অনুযায়ী, কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জিত হয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে- এই ব্যালেন্সিংটা কতটুকু ন্যায্য? উন্নত বিশ্ব দিনরাত কারখানায় ধোঁয়া ছাড়বে, আর আমাদের পাহাড়ি বন বা ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ করেই কি তার সমাধান আসবে? এটি কি আসলে ‘বৈশ্বিক সমতা’ না ‘অর্থনৈতিক গ্লোবাল বাণিজ্য’? বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগে অনেক উন্নত দেশ ও করপোরেট প্রতিষ্ঠান একটি বিকল্প পন্থা নিয়েছে। অন্য দেশের বন রক্ষা বা পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ করে নিজেদের অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণকে ‘ক্ষতিপূরণ’ দেওয়া। এভাবেই গড়ে উঠেছে Voluntary Carbon Market (VCM) বা REDD+ প্রোগ্রামের মতো কাঠামো। মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশের দূষণ সামলে নিচ্ছে বন রক্ষা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বা কৃষি-পরিবেশগত উদ্যোগের মাধ্যমে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৬.১ মিলিয়ন কার্বন ক্রেডিট বিক্রির লক্ষ্যে একটি চুক্তি করে, যার সম্ভাব্য আয় প্রায় ১১.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
বাংলাদেশ সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে, যার আওতায় বন সংরক্ষণ করে কার্বন ক্রেডিট বিক্রি করে আয়ের পথ তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালে সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয় ৫০ লাখ ডলার পর্যন্ত আয় সম্ভব এই বাজার থেকে। তবে প্রশ্ন হলো- এই টাকা কাদের কাছে পৌঁছায়? গাছের টাকায় কি গাছ বাঁচছে, না গাছের নিচে কেউ বসেই সব টেনে নিচ্ছে? এই লেনদেনে বন অধিকার, স্থানীয় ভোক্তা অংশগ্রহণ, পরিবেশগত জবাবদিহিতা কোথায়? অনেক সময় দেখা যায়, বন সংরক্ষণের নামে আদিবাসী সম্প্রদায় বা স্থানীয় মানুষদের বনজ সম্পদ ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। অথচ তাদের জীবন ও জীবিকা বনেই নির্ভরশীল। তাদের কোনো পূর্বানুমতি ছাড়াই বন রক্ষার তাদের অধিকার হরণ হয়, বিনিময়ে যা আসে তা হয় সরকারি তহবিলে অথবা বিদেশি সংস্থার পকেটে।
বিশ্বখ্যাত জলবায়ু আন্দোলন ''Fridays For FutureÓ, ÒClimate Justice NowÓ, ÒFriends of the Earth''-এর মতো সংগঠনগুলো কার্বন মার্কেট বা অফসেটিংকে দীর্ঘদিন ধরে ‘ফাঁকি’ (loophole) হিসেবে দেখে। তাদের মতে, এটি দূষণ কমানোর বাস্তব প্রচেষ্টা না করে এক ধরনের ‘লাইসেন্স টু পাল্যুট’, অর্থাৎ দূষণ করার বৈধতা হয়ে দাঁড়ায়। উন্নত দেশগুলো নিজেদের পরিবর্তন না এনে, শুধু টাকার বিনিময়ে দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। তারা আরও বলছে- এটি জলবায়ু ন্যায়বিচার বিরোধী (climate injustice)। কারণ যারা সবচেয়ে কম দূষণ করে (উন্নয়নশীল দেশ), তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ নিজেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দাবি করলেও আন্তর্জাতিক চাপ বা আর্থিক প্রণোদনা প্রাপ্তিতে এখনো অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে অনেক সরব। সভা-সেমিনার, প্রশিক্ষণ, পোস্টার-ক্যাম্পেইন- সব চলছে। কিন্তু বাস্তবতা কি? উন্নত দেশগুলোর জলবায়ু তহবিলের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৃত পরিবেশ সংরক্ষণে তরুণদের অংশগ্রহণ হতাশাজনক। বিভিন্ন ‘সবুজ প্রকল্প’ এর পেছনে পরিবেশ না, বরং পলিসি প্রজেক্ট প্রাধান্য পাচ্ছে। বিশ্ব যখন ঈঙচ সম্মেলনে কার্বন অফসেট নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন আমাদের উচিত আরও স্বচ্ছতা আনা- এই অর্থ কোথা থেকে এলো, কোথায় যাচ্ছে এবং এতে স্থানীয় জনগণ কতটুকু উপকৃত হচ্ছে? বাংলাদেশে বর্তমানে কার্বন ক্রেডিট সংক্রান্ত আইন বা নীতিমালা স্পষ্টভাবে প্রণীত হয়নি। এটাই সুযোগ- আমরা চাইলে একটি ন্যায্য, জনমুখী ও স্থানীয় অংশগ্রহণমূলক কাঠামো তৈরি করতে পারি। নতুন প্রজন্মের অনেকেই ‘জলবায়ু পরিবর্তন’, ‘কার্বন নিউট্রাল’, ‘নেট জিরো’ এসব শব্দ শুনেছে, কিন্তু কতটুকু উপলব্ধি করতে পারছে? গাছ লাগানো মানেই পরিবেশ রক্ষা নয়। কার্বন বাজার, পরিবেশ রাজনীতি, বন সংরক্ষণ বনাম জনগণের অধিকার- এসব বিষয়ে জানা ও প্রশ্ন তোলা এখন সময়ের দাবি। কারণ আগামী পৃথিবীর ভবিষ্যৎ গঠনের লড়াইটা নতুন প্রজন্মের কাঁধেই আসবে। তাই শুধু ‘সবুজ’ হতে চাইলে নয়, ‘সচেতনভাবে সবুজ’ হতে হবে।
আমরা কি জলবায়ু ন্যায্যতার পথে যাচ্ছি? নাকি শুধু ‘সবুজ মার্কেটিং’র অংশ হয়ে উঠছি? বাংলাদেশ কি সত্যিই এক জলবায়ু-নেতৃত্বের মডেল হয়ে উঠবে, নাকি বিক্রি হবে প্রতিদিন একটু একটু করে, কার্বন মার্কেটের বৈশ্বিক বোর্ডে এক ক্ষুদ্র খেলোয়াড় হয়ে। সময় এখন তরুণদের, তাদের এখন প্রয়োজন এই আলোচনায় সরব হওয়া। আমরা যদি পরিবেশবাদী হই, তাহলে আমাদের শুধু গাছ লাগানোর ছবি পোস্ট করলেই চলবে না- এই বাজার ব্যবস্থার ভেতরের সত্যটা বুঝতে হবে। একটা গাছ বাঁচিয়ে কীভাবে একটা দেশে ধোঁয়ার লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে- সেটা বুঝে জবাবদিহিতা দাবি করতে হবে। একটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না। সবুজ অর্থনীতি তখনই টেকসই হয়, যখন তা সবার জন্য ন্যায্য হয়।
লেখক : পরিবেশকর্মী
প্যানেল/মো.