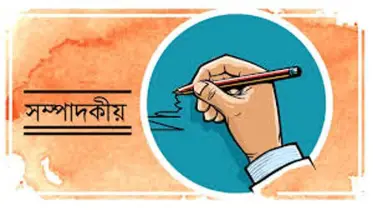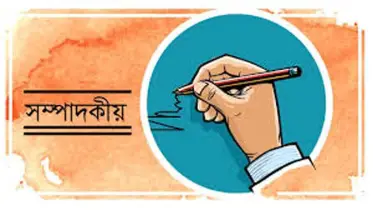বাংলাদেশের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে রয়েছে। তিন বছর ধরে মূল্যস্ফীতির প্রবণতা ঊর্ধŸমুখী। এর মধ্যে দুই বছরের বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। এমন এক প্রেক্ষাপটে বাজার পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র পেতে অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হিসাবের জন্য ‘কোর ইনফ্লেশন’ শীর্ষক নতুন একটি পরিমাপ পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে, যা বিদ্যমান গড় ভোক্তা মূল্য সূচক বা কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) পদ্ধতির পাশাপাশি ব্যবহৃত হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও অর্থ মন্ত্রণালয় নতুন এই পদ্ধতির কর্মধারা প্রণয়নের কাজ করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের মূল্যস্ফীতি পরিমাপ পদ্ধতির এই যুগোপযোগীকরণ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। সাম্প্রতিক সময়ে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য অনেকটাই বেড়েছে। তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), মাথাপিছু জিডিপি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, রাজস্ব খাত (রাজস্ব আহরণ, সরকারি ব্যয়, বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন), মুদ্রা ও আর্থিক খাত (মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, মুদ্রা পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ ঋণ, সুদের হার, পুঁজিবাজার), বৈদেশিক খাতের রপ্তানি ও আমদানি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের মতো সামষ্টিক অর্থনীতির প্রায় সব অনুষঙ্গেই যেহেতু বাংলাদেশ এখন সংকটে রয়েছে এবং অর্থনীতির কাঠামোগত অনেক দুর্বলতাও রয়েছে; সেহেতু জ্ঞানাভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে মূল্যস্ফীতি-জিডিপিসহ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকসমূহ পরিমাপ পদ্ধতি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত পদ্ধতির ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কার্যকর পদ্ধতি কোনটি তা নিশ্চিত করতে হবে।
মূল মূল্যস্ফীতি বা কোর ইনফ্লেশন ধারণাটির বাংলাদেশে প্রয়োগের বিষয়টি বিশ্লেষণের আগে সংক্ষেপে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, বিশ^ অর্থনীতির তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি যে খুব খারাপ, সে কথা বলা যায় না। তবে সমস্যা হচ্ছে, অতীতে রাজনৈতিক সরকারের সময় মূল্যস্ফীতির তথ্য উপস্থাপনে জেনেশুনেই শুভঙ্করের ফাঁক রাখা হয়েছে। ফলে সরকারের ঘোষণার সঙ্গে বাজারে অনুভূত মূল্যস্ফীতির বিস্তর ফারাক সবসময়ই অনুভূত হয়েছে। এরই ফল হিসেবে এখন বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার রেকর্ড বৃদ্ধিসহ ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য নিদানমূলক ব্যবস্থা নিলেও অনেককে বিস্মিত করে মূল্যস্ফীতি কমার চেয়ে বরং বাড়তে দেখা যাচ্ছে। গত অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি ১০.৮৭ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ছিল গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ সময় খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতিও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৬৬ শতাংশে। অনেকে মনে করেন, বন্যা ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থাকলেও কোনোভাবেই মূল্যস্ফীতির চড়া পারদ নিম্নগামী না করতে পারার পেছনে মূল্যস্ফীতির হিসাবে গলদই প্রধানত মূল ভূমিকা রেখেছে। জ্ঞানাভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ ও বক্তব্য নিয়ে মুনাফালোভী ব্যবসায়ী ও আমলাদের প্রণীত নীতিপরিকল্পনার সাফল্য ও যথার্থতা তুলে ধরতেই যে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচকে শুভঙ্করের ফাঁকি রাখা হয়েছে, সে কথা অনস্বীকার্য। ভঙ্গুর একটি অর্থনীতি হাতে পাওয়া বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার মনে করছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসতে অন্তত বছরখানেক লাগবে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারকে স্মরণে রাখতে হবে যে, সমস্যা কিন্তু একের পর এক আসছেই। এ অবস্থায় প্রকৃত আয় বৃদ্ধি না পাওয়ার পাশাপাশি যদি দুই-তিন গুণ হারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তাহলে সাধারণ মানুষ দ্রুতই চরম অধৈর্য ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। যার স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ২০০৭-০৮ সময়কালের ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভীষণ চাপে পড়ে দ্রুত নির্বাচনে যাওয়া এবং ২০২৪ সালে জুলাই-আগস্টের দিন কয়েকের মধ্যেই প্রবল শক্তিধর আওয়ামী লীগ সরকারের হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া। ২০০৮ সালের ১২ জানুয়ারি সরকারের এক বছরপূর্তিতে রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ফখরুদ্দীন আহমদ মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি তাঁর সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে স্বীকার করে দ্রুতই নির্বাচন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বেশকিছু জরুরি সংস্কার ছাড়াই নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মনে করা হয়, সে সময় মূল্যস্ফীতি বিশেষ করে চালের দাম আকাশচুম্বী হওয়ার পেছনে ব্যবসায়ী-আমলা-রাজনীতিবিদ ও করপোরেট গণমাধ্যম সম্মিলিতভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।
সে যাই হোক, কোর ইনফ্লেশনে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, প্রস্তাবিত নতুন এই হিসাব পদ্ধতিতে বাংলাদেশের মানুষ বেশি ভোগ-ব্যবহার করে এমন ৫০-৬০টি পণ্যের দামের ওঠানামার তথ্য নিয়ে মূল্যস্ফীতি নির্ণয় করা হবে। একই সঙ্গে জাতিসংঘের গাইডলাইন অনুযায়ী বিদ্যমান ভোক্তা মূল্য সূচক বা কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) পদ্ধতিও চালু থাকবে, যেখানে ৭৪৯টি পণ্য ও সেবার (২৪২টি খাদ্যপণ্য ও ৫০৭টি খাদ্যবহির্ভূত পণ্য ও সেবা) বাজারদর ওঠানামার ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হিসাব করা হয়। দেশের ৬৪ জেলার ১৫৪টি হাটবাজার থেকে নির্ধারিত সময়ে তথ্য নিয়ে বিবিএস এ যাবত সিপিআই পদ্ধতিতে মূল্যস্ফীতির তথ্য দেশবাসীকে জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অনেকদিন ধরেই বিবিএস তথা সরকারের সিপিআই হিসাবের জন্য গৃহীত ৭৪৯টি পণ্যের ঝুড়িটিতে সমস্যার কথা বলে আসছেন। কারণ, এসব পণ্যের বেশিরভাগই বাংলাদেশে ভোগ-ব্যবহার হয় না। তার ওপর বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি সাধারণত চাহিদার কারণে নয়, বরং সরবরাহজনিত সমস্যার কারণে ঘটে থাকে বলে গবেষণায় স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। উৎপাদক থেকে ভোক্তাপর্যায়ে পণ্য সরবরাহে চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেট ও ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা এবং বিশৃঙ্খল বাজারব্যবস্থার কারণে এখানে মূলত মূল্যস্ফীতি ঘটে। এ ছাড়া সিপিআইয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের ভোগ্যপণ্যের দরের ওঠানামা বিশ্লেষণ করা হয় না বলে সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত নীতিমালা মূল্যস্ফীতির চাপে বেশি থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে খুব একটা ইতিবাচক প্রভাব রাখে না। যদিও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে সিপিআই বিশ্লেষণে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা হয়; কিন্তু বাংলাদেশে সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতায় সিপিআই কখনোই প্রকৃত তথ্য দিতে পারে না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে শুধু কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) পদ্ধতি ব্যবহার করে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা অনেক আগেই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ জাতিসংঘের গাইডলাইনের দোহাই দিয়ে শুধু এই পদ্ধতি অনুসরণ করে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের তথ্য একসঙ্গে হিসাব করা হয় বলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সরকারগুলোর পক্ষে মূল্যস্ফীতির সঠিক চিত্র লুকিয়ে রেখে ধনিক শ্রেণি ও ব্যবসায়ীবান্ধব নীতি-সুবিধা দেওয়া সহজ হয়েছে। সিপিআইর হিসাবে যে বেশকিছু দুর্বলতা রয়েছে সে কথা বাংলাদেশের আমলা-রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারকরা ভালো করেই জানেন। কিন্তু ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যান। অনেক আগেই গবেষণায় প্রমাণিত, বাংলাদেশে সিপিআইর অসংখ্য পণ্যের ঝুড়ি কার্যত মূল্যস্ফীতির সঠিক তথ্য দিতে পারছে না। এতে ভোগ্যপণ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। ফলে নতুন পণ্য ও সেবার অন্তর্ভুক্তি এবং পুরনো পণ্য বাদও দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সাধারণভাবে খাদ্য-জ্বালানির মতো অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সবসময় অস্থির ও অনিশ্চিত থাকে। এ রকম পণ্যের মূূল্য পরিবর্তন সিপিআইর হিসাবে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে, যা মূল মূল্যস্ফীতির উপাত্তকে বিকৃত করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে চালের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এর পরেই রয়েছে মাছ। এদের দাম সামান্য বাড়লেই মূল্যস্ফীতিও অনেক বেড়ে যায়। এ ছাড়া সিপিআই সাধারণত উচ্চ ও মধ্য আয়ের মানুষের ভোগ্যপণ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, যা নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য মোটেও প্রাসঙ্গিক নয়। আর এ কারণেই বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণাÑ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচকের প্রকৃত তথ্য প্রকাশে নির্ধারকরা কখনোই স্বচ্ছ নন, কারণ এতে করে ধনী তোষণনীতি আরোপ সহজ হয়।
কোর ইনফ্লেশন পদ্ধতির উদ্ভাবন ও যুগোপযোগী করতে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদ মার্ক নি, মার্টিন ফিলিপস ও জেমস টোবিনের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ, কানাডার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইউরোপীয় অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোর ইনফ্লেশনকে সর্বদা মনিটরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ সূচক বিবেচনা করে। খাদ্য ও জ্বালানির দাম পরিবর্তনের প্রভাব বাদ দিয়ে অর্থনীতির মূল প্রবণতা বুঝতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এই পদ্ধতির ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারণ করতে পারে। এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির জন্যে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে বলে দেশগুলো মনে করে। তবে এই পদ্ধতির সমালোচকেরা মনে করেন, কোর ইনফ্লেশন শুধু কিছু পণ্যের দাম পরিবর্তনকে বিবেচনায় নেয় বলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। তাদের মতে, সংকটের সময় খাদ্য ও জ্বালানির দাম বাড়লে কোর ইনফ্লেশন কম হতে পারে, যা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এর ফলে সাধারণ জনগণের বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ও সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এসব সমালোচনা আমলে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার স্পেশাল সিপিআই পদ্ধতির কার্যকরতাও খতিয়ে দেখতে পারে। উল্লেখ্য, কানাডার কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোর ইনফ্লেশনকে কার্যকরী নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করতে তিনটি পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমত সিপিআই ট্রিম, যেখানে সবচেয়ে অস্থির ২০ শতাংশ পণ্যের দাম বাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, সিপিআই মিডিয়াম, যা মধ্যম দামের পরিবর্তনকে ধরে রাখে এবং অস্থিরতার প্রভাব কমিয়ে দেয়। তৃতীয়ত, সিপিআই কমন, যেখানে বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে সাধারণ প্রবণতাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। কানাডার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোর ইনফ্লেশন পদ্ধতি অনুসরণের মূল লক্ষ্য হলো, মূল মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা বোঝা এবং সাময়িক পরিবর্তনসমূহ বাদ দিয়ে একটি স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য অর্জন করা। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অস্থির মূল্য পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকতে পারে, যা অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে, স্পেশাল কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স বা বিশেষ ভোক্তা মূল্য সূচক (এসসিপিআই) হলো একটি বিশেষ সূচক, যা সাধারণ সিপিআইর তুলনায় নির্দিষ্ট পণ্যের বা পরিষেবার মূল্য পরিবর্তনকে হিসাবে রাখে। এটি সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট খাত বা পণ্যের জন্য তৈরি করা হয়, যা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও নীতিনির্ধারণে সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে, এসসিপিআই নির্দিষ্ট খাতের মূল্য পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম, যা সাধারণ সিপিআইর তুলনায় আরও বিস্তারিত ও নিখুঁত তথ্য প্রদান করে। এর মাধ্যমে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট খাতের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। ভোক্তাদের আচরণ ও তাদের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন বুঝতেও এসসিপিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এসসিপিআই পদ্ধতিরও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমনÑ এটি শুধু নির্দিষ্ট পণ্য-পরিষেবার ওপর আলোকপাত করে। এতে করে সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্র পাওয়া কিছুটা কষ্টকর হয়ে যায়। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে এসসিপিআই পদ্ধতি অস্থির একটি চিত্র ও সিপিআইর তুলনায় তথ্য সংগ্রহের জটিলতা তুলে ধরতে পারে। এসব সমালোচনা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতের মূল্যস্ফীতি বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সহায়ক নীতিপ্রণয়নে স্পেশাল সিপিআই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, দরিদ্র শ্রেণির প্রকৃত জীবনমান বোঝা, দরিদ্র শ্রেণির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও ভর্তুকি নীতির উন্নয়ন, দরিদ্র শ্রেণির খরচের ধরন অনুধাবন এবং সামাজিক ন্যায় ও বৈষম্য নিরসনে স্পেশাল সিপিআই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে বলে গবেষণায় দেখা গেছে।
পরিশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশের সামষ্টিক ও সামগ্রিক অর্থনীতির বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যুক্তিসংগত ও পরীক্ষিত নীতি-কৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও গতি ত্বরান্বিত করতে সবচেয়ে ভালো হবে ধার করা দর্শন বাদ দিয়ে যদি সংবিধানে বিধৃত ‘বৈষম্য হ্রাসকারী দেশজ উন্নয়নদর্শন’ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এতে করে শত শত শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবার অকাতরে আত্মত্যাগের পর পরিবর্তন-উন্মুখ বর্তমান পরিস্থিতিতে আপামর জনগণের স্বার্থহীন অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা যাবে। কারণ, নতুন ও অনাগত প্রজন্মের জন্যে শোভন-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে এখন পর্যন্ত মানুষ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি