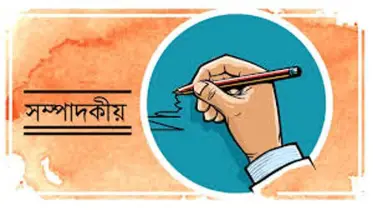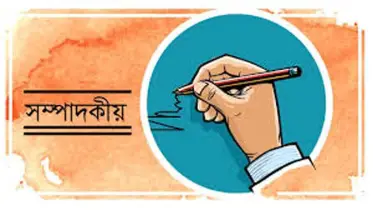বাংলাদেশের সুন্দরবন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য
জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে না পারলে এমন আগুন বারবার লাগতে পারে। অনিচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগতে পারে আবার ইচ্ছাকৃতভাবেও আগুন লাগতে পারে। তাই বাওয়ালি বা মৌয়াল যারা রয়েছেন, তাদের আগুনের ব্যবহারে সচেতন থাকা দরকার। সব ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সর্বোপরি অগ্নিকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নিতে হবে
বাংলাদেশের সুন্দরবন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য। এটি বাংলাদেশের অক্সিজেন ভা-ার। এই বন শুধু নির্মল অক্সিজেনই সরবরাহ করছে না, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষকে আগলেও রাখে। ভয়ংকর সব ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করছে সুন্দরবন। দেশের জীববৈচিত্র্য নীরবে, নিভৃতে রক্ষা করে চলছে।
দেশের বৃহত্তম এই বনটি বিভিন্ন পরিবেশকেন্দ্রিক দিবস ছাড়াও নানা সময়ে আলোচনায় উঠে আসছে। সর্বশেষ আলোচনায় উঠে এসেছে পূর্ব সুন্দরবনে লাগা আগুনের মাধ্যমে। গত ৪ মে দক্ষিণাঞ্চলীয় বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার সুন্দরবনের আমুরবুনিয়া এলাকায় আগুন লাগে।
ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় জনগণ, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার, কোস্টগার্ড ও বন বিভাগের নিজস্ব ফায়ার ইউনিটের প্রচেষ্টায় ৭ মে আগুন নেভানোর কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
ওই এলাকায় কাছাকাছি খাল বা নদী না থাকায় আগুন নেভানোর জন্য পানিও নিতে হয়েছে বেশ দূর থেকে। দেড় থেকে দুই কিলোমিটার দূর থেকে পাওয়ার পাম্পের মাধ্যমে পানি এনে ব্যবহার করা হয়েছে। রাতের অন্ধকারে সুন্দরবনের ওই এলাকায় বন্যপ্রাণীর ঝুঁকির কারণে রাতে আগুন নেভানোর কাজ করা যায়নি।
তবে ফায়ার সার্ভিস সুন্দরবনের গভীরে লাগা আগুন নেভাতে পুরো এলাকা ঘিরে ফায়ার লাইন করে, অর্থাৎ আগুনের চারপাশের এলাকায় গাছপালা এবং মাটিতে নালা কেটে পানি ছেড়ে আগুন নেভানোর কাজ করেছে। এতে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে আগুন ছড়াতে পারেনি। তারপরও চাঁদপাই রেঞ্জের আমুরবুনিয়ায় লাগা আগুন দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ পূর্ব সুন্দরবনের দুই কিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আগুনে।
২৪ বছরে ২৫ বার আগুন
সুন্দরবনে আগুন এবারই প্রথম নয়। গত ২৪ বছরে এই বনে ২৫ বার আগুন লেগেছে। প্রতিবারই আগুন লেগেছে পূর্ব লোকালয়-সংলগ্ন বনের পূর্বাংশে। অংশটি ভোলা নদীর তীরে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই ও শরণখোলা রেঞ্জে পড়েছে। দুই যুগের এসব আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ১০০ একর বনভূমির গাছপালাসহ বিভিন্ন লতাগুল্ম। যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জীববৈচিত্র্যের। ক্ষতির মুখে পড়েছে বন্যপ্রাণীর বিচরণ কেন্দ্র ও আবাসস্থল।
বন বিভাগের তথ্যমতে, দুই যুগের এসব অগ্নিকা-ের সব ঘটনাই ঘটেছে পূর্ব সুন্দরবন বিভাগে ভোলা ও মরা ভোলা নদীসংলগ্ন এলাকায়। এসব অগ্নিকা-ের অন্তত ২৪টির হিসাব পাওয়া যায়। এরমধ্যে ২০০২ সালে চাঁদপাই রেঞ্জের কটকায় একবার, একই রেঞ্জের নাংলী ও মান্দারবাড়িয়ায় ২ বার। ২০০৫ সালে পচাকোড়ালিয়া, ঘুটাবাড়িয়ার সুতার খাল এলাকায় দুবার, ২০০৬ সালে তেরাবেকা, আমুরবুনিয়া, খুড়িয়াবাড়িয়া, পচাকোড়ালিয়া ও ধানসাগর এলাকায় পাঁচবার।
২০০৭ সালে পচাকোড়ালিয়া, নাংলী ও ডুমুরিয়ায় তিনবার। ২০১০ সালে গুলিশাখালীতে একবার, ২০১১ সালে নাংলীতে দুবার, ২০১৪ সালে গুলিশাখালীতে একবার, ২০১৬ সালে নাংলী, পচাকোড়ালিয়া ও তুলাতলায় তিনবার, ২০১৭ সালে মাদ্রাসারছিলায় একবার ও ২০২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ধানসাগরে একবার। ২০২১ সালের ৩ মে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের দাসের ভারানি এবং সর্বশেষ চাঁদপাই রেঞ্জের জিউধারা স্টেশনের আমুরবুনিয়া টহল ফাঁড়ির লতিফেরছিলা এলাকায় আগুনের ঘটনা ঘটে।
প্রতিবারই আগুনের ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠন হয়। আসে সুপারিশও। তবে সেগুলো খুব একটা আলোর মুখ দেখে না। ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে সে সকল সুপারিশ। ফলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে বছরের পর বছর। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে আগুন লাগার কারণ হিসেবে মৌয়ালদের ব্যবহৃত আগুনের কু-লী, জেলেদের সিগারেট, দাবদাহ, অনাবৃষ্টি, খরা, বন অপরাধে সাজাপ্রাপ্তদের প্রতিশোধমূলক আচরণ, দুষ্কৃতকারীদের দিয়ে বনের মধ্যে আগুন ধরানোকে দায়ী করা হয়। আগুনের স্থায়িত্বের কারণ হিসেবে বিভিন্ন গাছের পাতার পুরু স্তরকেও দায়ী করেছে তদন্ত কমিটি।
প্রশ্ন হলোÑ একই অঞ্চলে বারবার কেন আগুন লাগে? আগের ২৪টি অগ্নিকা-ের ঘটনায় বন বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদনে আগুনের সূত্রপাতের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ১৫ বার ‘অসাবধানতাবশত বনজীবীদের ফেলে যাওয়া আগুনের কথা’ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জেলে-মৌয়ালদের ফেলে আসা আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে অন্তত ১৫ বার। জেলে ও মৌয়ালদের বিড়ি-সিগারেট বা মধু সংগ্রহের সময় মৌমাছি তাড়ানোর ধোঁয়ার মশাল থেকে আগুন লেগেছে।
এছাড়াও সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দাবদাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৪ বার, মাছ ধরার জন্য ৪ বার, আক্রোশবশত অগ্নিসংযোগের আশঙ্কার উল্লেখ রয়েছে ৪ বার। তবে স্থানীয় ও পরিবেশবাদীদের অভিযোগ, বন বিভাগের একশ্রেণির কর্মকর্তার যোগসাজশে ইচ্ছাকৃতভাবে গহিন বনে আগুন ধরিয়ে দেয় অসাধু মাছ ব্যবসায়ীরা। পরে বর্ষা মৌসুমে এসব স্থান প্লাবিত হলে জাল দিয়ে সহজেই লাখ লাখ টাকার মাছ ধরতে পারে তারা।
তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়াও বারবার অগ্নিকা-ের একটি কারণ। এছাড়া অসাধু বন কর্মকর্তা ও মাছ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য, মৌয়ালদের অদক্ষতাসহ বিভিন্ন কারণে বারবার সুন্দরবনে অগ্নিকা-ের ঘটনা ঘটছে।
কতভাবে বনে আগুন লাগে
বনে দুইভাবে আগুন লাগতে পারে। এক. ইচ্ছাকৃত এবং দুই. প্রাকৃতিক তথা দাবানল। পাশের দেশ ভারতের বনে আগুনের যে কয়টি খবর পাওয়া যায়, তারমধ্যে ২০১৭ সালে বান্দিপুর বনের আগুনে এক হাজার হেক্টরের বেশি বন ধ্বংস হয়ে যায়। ২০১৬ সালে উত্তরাখ-ের ভয়াবহ অগ্নিকা-ে প্রায় ৪ হাজার হেক্টর বন ছাই হয়ে গিয়েছিল এবং সাত জনের মৃত্যু হয়েছিল। ভারতের হিমালয় অঞ্চল, অন্ধ্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার শুকনো বন এই দাবানলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বনে আগুনের কারণ চিহ্নিত করার গবেষণা বলছে, বনের আগুন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট হতে পারে। প্রাকৃতিক বনের আগুনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো- বজ্রপাত থেকে শুকনো গাছপালায় আগুন লাগা। তাদের পর্যবেক্ষণ বলছে, অগ্নিকা-গুলোর বেশিরভাগই মানুষের উপস্থিতি থেকে দূরবর্তী স্থানে ঘটে।
গাফিলতির কারণে যে অগ্নিসংযোগ ঘটে, তার প্রকৃত শাস্তি হলে অগ্নিসংযোগের সংখ্যা কমবে। বনের মধ্যে ক্যাম্প ফায়ার, রান্না, উষ্ণতা, আগুন জ্বালানো বন্ধ করতে হবে, সিগারেট, সিগার, পাইপ এবং তামাক, আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত ম্যাচ বা লাইটার ব্যবহারে সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে।
সুন্দরবনে আগুন লাগার কারণ
সুন্দরবনের আগুন ‘মানবসৃষ্ট ও পরিকল্পিত’ উল্লেখ করে দীর্ঘদিন ধরে বন বিভাগ ও সরকারকে এ নিয়ে আরও গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন ও বন সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশবাদীদের অভিযোগ, বন বিভাগের একশ্রেণির কর্মকর্তার যোগসাজশে ইচ্ছাকৃতভাবে গহিন বনে আগুন ধরিয়ে দেন অসাধু মাছ ব্যবসায়ীরা। পরে বর্ষা মৌসুমে এসব স্থান প্লাবিত হলে জাল দিয়ে সহজেই লাখ লাখ টাকার মাছ ধরতে পারেন তারা।
শ্বাসমূলীয় বন হিসেবে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে দিনে-রাতে জোয়ারে দুবার প্লাবিত হয়। ব্যতিক্রম শুধু ধানসাগর ও জিউধারা এলাকা। স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, বর্ষায় ওই এলাকা ডুবে যায়। তার আগে শুষ্ক মৌসুমে দুষ্কৃতকারীরা আগুন দিলে বড় বড় গাছ পুড়ে যায়। তখন বড় বড় গর্ত তৈরি হয়, যাতে বর্ষায় পানি জমলে শিং, কই, মাগুরসহ নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। ছাই ও পাতার পোড়া জৈব অংশে খাবারের খোঁজে মাছ উপরে উঠে আসে। তখন প্রভাবশালীরা সেখানে মাছ ধরে।
বনসংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারাও বলছেন, কিছু অসাধু মানুষ আছেন, যাদের আশকারা দেয় বন বিভাগ। বন বিভাগের লোকজন টাকা নিয়ে তাদের বনে ঢোকার অবৈধ সুবিধা দেয়। এ সুবিধা কাজে লাগায় কিছুসংখ্যক মানুষ। তারা ভাবে শুকনা মৌসুমে যদি আমরা আগুন লাগিয়ে দিতে পারি, তাহলে বৃষ্টির মৌসুমে কিছু মাছ পাব।
এ জন্যই তারা বারবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটায়। স্থানীয় নিশানবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামও একই ধরনের মন্তব্য করেন। অগ্নিকা-ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের বিষয়টি উঠে এসেছে। অন্তত পাঁচটি প্রতিবেদনে অগ্নিকা-ের কারণ হিসেবে পাঁচবার ‘মাছ মারার সুবিধার জন্য দুষ্কৃতকারীরা আগুন দিতে পারে’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
নেভানোর সক্ষমতা কতটুকু
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের ফায়ার সার্ভিসেরও আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম রয়েছে। তবে দাবানলের মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞতা কিংবা সরঞ্জাম নেই। বিশেষ করে, অন্য দেশে ফায়ার ফাইটিং হেলিকপ্টার থাকে, যা আমাদের নেই। এছাড়া বন-জঙ্গলে আগুন নিয়ন্ত্রণে স্পেশাল টিম থাকে ফায়ার সার্ভিসের। সেটিও নেই বাংলাদেশে।
সুন্দরবনের মতো জায়গায় আগুন লাগলে গাড়ি ও সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো রাস্তাও নেই। বিশেষ করে বনের আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার ফাইটিং হেলিকপ্টার গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ হেলিকপ্টারে বাতাস নিচের দিকে আসে। তখন অক্সিজেনের সরবরাহ পেলে আগুন আরও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার কমপক্ষে ৪০ ফুট ওপর থেকে পানি ছিটায়।
ফায়ার ফাইটিং হেলিকপ্টার হলে আরও নিচ থেকে পানি ছিটানো যাবে। ফায়ার ফাইটিং হেলিকপ্টারের বাতাস নিচের দিকে সরাসরি না গিয়ে হরাইজন্টালি দুই পাশে যায়। ফলে বাতাস লেগে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে না। তাই মডার্ন ফায়ার ব্রিগেডের জন্য ফায়ার ফাইটিং হেলিকপ্টার অবশ্যই প্রয়োজন। বনাঞ্চলের আগুন নেভানো হেলিকপ্টার ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়া সুন্দরবনের আগুন নেভানোর জন্য বিশেষায়িত ফায়ার ফাইটিং টিম গঠন করা যেতে পারে।
স্পেশাল ফায়ার ফাইটিংয়ের জন্য একাডেমিও নেই আমাদের, যা জরুরি। তাই সুন্দরবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের দক্ষতা বাড়াতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে এমন আগুন লাগলে ট্রেইন করে। সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও ট্রেইন করতে হবে। তাহলে আগুন ছড়াতে পারবে না। বুশ ফায়ার ফাইটিং দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন। সেখানে যারা আগুন নেভাবে, তাদের জঙ্গলে আগুন নেভানোর জন্য অভিজ্ঞ হতে হবে। তাদের স্টেশন হবে জঙ্গলেই।
সমাধান কোন পথে
পূর্ব সুন্দরবনের আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হলো পানির প্রাপ্যতা। অগ্নিনির্বাপণে দূরবর্তী নদী ছাড়া পানির কোনো উৎস ছিল না সেখানে। পানির উৎস থেকে আগুনের দূরত্ব ছিল প্রায় আড়াই কিলোমিটার। চলাচলের রাস্তা ছিল হাঁটা ও দুর্গম। পূর্ব সুন্দরবনের কাছে রয়েছে ভোলা নদী ও দুটি খাল। কিন্তু ওই নদী ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি থাকে না। কেবল জোয়ারের সময় ভোলা নদীতে পানি পাওয়া যায়।
ফলে আগুন নেভাতে পানি পেতে জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। এতে আগুন নেভাতে বিলম্ব হয়েছে। তাই ভরাট হয়ে যাওয়া ভোলা নদী ও খাল দুটি খনন করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে।
শুধু পূর্ব সুন্দরবনই নয়, পুরো সুন্দরবনের অনেক নদী-খাল ভরাট হয়ে গেছে। নদী-খালে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনা জরুরি। এসব নদী-খাল পরিবেশসম্মতভাবে খনন করতে হবে।
খননের মাটি বনে বা পাড়ে ফেলা যাবে না। আবার ঢালাওভাবে খনন করা যাবে না। যেখানে জরুরি সেখানে খনন করা যেতে পারে। মাটি টাগবোট দিয়ে দূরে মূলভূমিতে ফেলতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চল একটু উঁচু। সেখানে পাড়ে মাটি ফেললে জোয়ারের পানি বনে ঢুকবে না। পরিকল্পিতভাবে প্রকল্পটি নেওয়া দরকার। আগের মতো প্রকল্প নিয়ে যদি মাটি বনের মধ্যে ফেলা হয় এবং বনকে যদি উঁচু করে দেওয়া হয়; তবে ম্যানগ্রোভের জন্য যে পরিবেশ লাগে, সেটা নষ্ট হবে।
তখন নতুন প্রকল্পেও কোনো লাভ হবে না। আবার সুন্দরবনে উত্তর-দক্ষিণমুখী খাল খনন করতে হবে। পূর্ব-পশ্চিমমুখী খাল কেটে কোনো লাভ হবে না। কারণ সুন্দরবনের সব নদীর ফ্লো উত্তর-দক্ষিণে। জোয়ারের পানি উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকেই ওঠে। সব খালের মুখ খুলে দিতে হবে। এপ্রিল ও মে সবচেয়ে স্পর্শকাতর মাস। বিশেষ করে এই দুই মাসে পাঁচটি অঞ্চলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিসপ্তাহে।
তবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে না পারলে এমন আগুন বারবার লাগতে পারে। অনিচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগতে পারে আবার ইচ্ছাকৃতভাবেও আগুন লাগতে পারে। তাই বাওয়ালি বা মৌয়াল যারা রয়েছেন, তাদের আগুনের ব্যবহারে সচেতন থাকা দরকার। সব ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সর্বোপরি অগ্নিকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নিতে হবে।
লেখক : প্রধান প্রতিবেদক, নগর সম্পাদক
দৈনিক জনকণ্ঠ