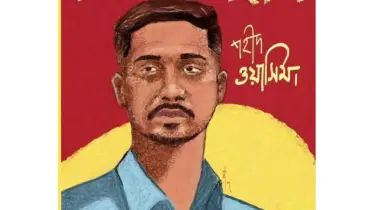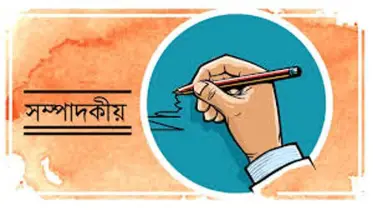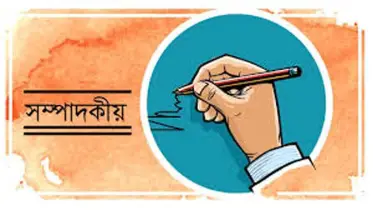প্রায় ৪০ হাজার পরিবার প্রত্যক্ষভাবে জুমচাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত
বিচিত্র পাহাড়ের ইকোসিস্টেম এবং বিচিত্র পাহাড়ি জনগণের জীবন-জীবিকার ধরন ও গতি-প্রকৃতি। প্রায় এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের আমাদের এই দেশটির শতকরা ১২ ভাগ পাহাড়ি এলাকা যার শতকরা ৯ ভাগ শুধু রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এই তিন পার্বত্য এলাকাজুড়ে অবস্থিত এবং এর পরিমাণ প্রায় ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার। এই পাহাড়ি এলাকার শতকরা ২ ভাগ জমি জুমচাষের আওতাধীন হলেও এখানকার প্রায় ৪০ হাজার পরিবার প্রত্যক্ষভাবে জুমচাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আধুনিক কৃষি উন্নয়নে এখন যে ইকোসিস্টেম ভিত্তিক গবেষণার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সেটি পাঁচ দশক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার দেশের জমির মধ্যে পার্থক্য আছে।
এখন আমি যদি সুনামগঞ্জের জমি, যেখানে তিন বৎসর বন্যা হয়, এক বৎসর ফসল হয়, নর্থ বেঙ্গলের জমি আর বরিশালের জমি, চিটাগাং হিল ট্রাক্টসের জমি, আর অন্য সব জমি এক পর্যায়ে দেখতে চাই, তাহলে অসিুবিধা হবে। আমার স্টাডির প্রয়োজন আছে।’ জাতির পিতার সেই দিকনির্দেশনামূলক বাণী আজও এদেশের আধুনিক কৃষির মূলমন্ত্র। অনুকূল এলাকায় কৃষির উন্নয়ন দ্রুতগতিতে হলেও বরেন্দ্র, হাওড়, চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশ অঞ্চলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ দৃষ্টি এখন সময়ের দাবি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড় নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন গবেষণা সূত্র অনুযায়ী এ পর্যন্ত প্রায় শতকরা ২০ ভাগ সম্পদকে আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং বিদ্যমান এ বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন পাহাড়ি জনগণের মাঝে নতুন আশার আলো সঞ্চার করবে।
পাহাড়ে জুমচাষের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। পার্বত্য চট্টগ্রাম, গারো ও খাসীয়া পাহাড়ের বাইরে ভারতের অরুণাচল, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা ‘সেভেন সিস্টার্স’ খ্যাত এই সাতটি রাজ্যে জুমচাষ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এছাড়া চীন, নেপাল, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর পাহাড়ি অঞ্চলে জুমচাষের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। মাত্র পাঁচ-ছয় দশক আগেও একবার কোনো পাহাড়ে জুমচাষ করার পর অন্তত ১৫-২০ বছর সেখানে আর জুম করা হতো না। এই দীর্ঘ সময়ে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল গড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হতো সেখানে; রক্ষা পেত পাহাড়ি জমির উর্বরতা।
কিন্তু ৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধের কারণে বিপুল সংখ্যক পাহাড় পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় সংকুচিত হয় জুমের জমি। আর ৮০’র দশক থেকে এখনো পাহাড়ে সমতল অঞ্চল থেকে অপরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের অভিবাসন গড়ে উঠেছে। এছাড়া পাহাড়ে ছয়টি সেনানিবাস ও প্রায় সাড়ে চারশ’ অস্থায়ী সেনা ছাউনি এবং বিডিআর, র্যাব, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি, বনবিভাগসহ নিরাপত্তা বাহিনীর অসংখ্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী ছাউনির কারণেও বিপুল সংখ্যক পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
উল্লেখিত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবহাওয়া ও মাটি জুমচাষের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও জুমের জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। একবার চাষ করার পর অন্তত ৫ থেকে ১০ বছর জমি অনাবাদি অবস্থায় রাখতে হয়, বিশেষত অধিকতর ফসল উৎপাদন ও মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য যা অত্যন্ত প্রয়োজন। এক সময় জুমিয়ারা জুম থেকে সারাবছরের প্রয়োজনীয় খোরাকি জোগাড় করতে সক্ষম হতো। এমনকি পরিবারের ভরণপোষণের পর খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকত। জুমিয়াদের মতে, আজকাল জুমচাষ আর আগের মতো নেই, ফলন ভাল হয় না। বলা বাহুল্য, জুমিয়ারা হচ্ছেন সকলেই প্রান্তিক চাষী ও সাধারণভাবে হতদরিদ্র।
অধিকাংশ জুমিয়াদের পুরো সপ্তাহের আয়ে ৪/৫ দিন চলে এবং বাকি সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় না খেয়ে থাকে এবং অপুষ্টিতে ভোগে। তারা হচ্ছেন গ্রামীণ সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত অংশ, যারা রাজনৈতিক বঞ্চনা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতির শিকার। তাই জুমচাষ ছাড়া অন্য কোনোভাবেই তাদের টিকে থাকার উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়েই জুমিয়ারা এখন মাত্র ৪-৬ বছরের ব্যবধানে এবং কোনো কোনো জায়গায় ২-৩ বছরের ব্যবধানে একই পাহাড়ে আবারও জুমচাষ করছে। যদিও পার্বত্য তিন জেলার মধ্যে বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু এসব জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সব সময়ের জন্য বছরের একটা সময় খাদ্য সংকটে পড়ে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এ খাদ্যঘাটতি সাধারণত চরমভাবে দেখা দেয়।
জুমচাষ আমাদের দেশের পাহাড়ি উপজাতিদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্য ধরে রাখতে বংশ পরম্পরায় জুমচাষ করে আসছে। এটা লক্ষণীয় যে, এখন পর্যন্ত ধান, সবজি, অর্থকরী ফসল, ফল, মসলা ইত্যাদির জন্য বছরের বেশিরভাগ সময় জুমিয়ারা জুমের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পাহাড়ি এলাকার স্থানীয় জনগণ জুমচাষকেই খাদ্য ও জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছে। জুমচাষে আদিবাসীদের জ্ঞান ও প্রযুক্তি নানাভাবে জড়িয়ে আছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ, জুমভূমি নির্বাচন প্রতিটি ক্ষেত্রে আদিবাসীরা সিদ্ধহস্ত। তারা বংশানুক্রমিকভাবে জুমচাষী বিধায় মাটি দেখে বুঝতে পারে কোন্ জমিতে কোন্ ফসল ভাল ফলন দেবে।
জুমিয়ারা জুমে একসঙ্গে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টি ফসলের আবাদ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে দানাজাতীয় যেমন- ধান, ভুট্টা, চীনা, কাউন; সবজি যেমন- মারফা, শসা, বেগুন, পুঁইশাক, বরবটি, ঢেঁড়স, মিস্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, করল্লা, টকপাতা, কাকরোল, চিনার; মসলা জাতীয় যেমন- মরিচ, ধনিয়া, আদা, হলুদ; ডালজাতীয় যেমন- অড়হর; তৈল জাতীয় যেমন- তিল, সরিষা; ফল জাতীয় যেমন- পেঁপে, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি; কন্দাল জাতীয় যেমন- কেশুর, জুমআলু, পেস্তাআলু, ক্যাসাভা এবং আঁশ জাতীয় তুলা অন্যতম। বর্তমানে অধিকাংশ জুমচাষী তাদের জুমে মাত্র ১৭/১৮টি ফসল করে থাকেন। জুমে তাদের এই উৎপাদনযজ্ঞ সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয় এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। মে-জুন মাসে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরপরই মাটি যখন জো অবস্থায় আসে, তখন তারা ফসলের বীজ বপন করে থাকে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি এই তিন জেলাতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, পাংখো, বম, ম্রো, খিয়াং, খুমি, চাক এই ১১টি নৃগোষ্ঠীসহ বাঙালিরা বাস করে আসছে, যাদের প্রধান পেশা কৃষি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে ভাত। এছাড়া প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীর যে নিজস্ব উৎসব পার্বণ রয়েছে, তাতে তারা নানা রকম পিঠাপুলি তৈরি করে থাকে, যা তাদের নিজস্ব জুমচাষ থেকে করে থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, লুসাই এবং পাংখোয়া নৃ-গোষ্ঠী তাদের জীবন-জীবিকার জন্য ১০০% জুমের ওপর নির্ভরশীল। খুমি, ম্রো এবং বম নৃগোষ্ঠী গড়ে ৮৫% এবং ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা নৃগোষ্ঠী গড়ে ৫০% জুমের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া মারমা, চাকমাসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য জুমের ওপর নির্ভরশীল।
পারিবারিক খাদ্য চাহিদা এবং উৎসব উদ্যাপনের জন্য পার্বত্য নৃগোষ্ঠী জুমে সাধারণত কক্রো, খামারাং, কানবুই, গ্যালন, মংথংন, বাদুই, র্যাংকুই, বিন্নি, খবরক, কোম্পানি, পিডি, চড়ুই, আমেধান, মধুমালতি, চাংমা, লেংদা, লিয়াচাই, গু-া, মেমা, মাইচং, ইয়াং, কুপালি, সূর্যমনি, বেটি, পাত্তি, লংগুর, লংকাপোড়া ইত্যাদি প্রায় ৭০টি স্থানীয় জাতের চাষ করে থাকেন। ইতোমধ্যে জুমিয়ারা প্রায় ১০০টি জুমধানের জাতকে বিলুপ্তপ্রায় জাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে রেংগুই, তুর্গী, লংলং, বাদি, রাঙ্গা, টারকো, আংফো, পুরু, পুংনি, লেসাই, কাদিয়া, বান্দরনখ, টোক্যা, লেংদা, লামলং, সিলি, গুদি, চাদা, টালো, সকালং, চাংমুই, টংথে, মেয়েং, মিলেং, কাদিয়া, সিলি, চুলুম, ক্রেনিং ইত্যাদি।
এ সকল জুমধানের ফলন কম হলেও এদের মধ্যে অনেক সমৃদ্ধ গুণাবলি রয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখে গেছে, জুমচাষীদের জুমে উৎপাদিত ধানে তাদের বছরের ৫-৭ মাস চলে, বাকি ৭-৫ মাসের খাদ্যের সংস্থানের জন্য বিভিন্ন কাজকর্ম যেমন- বয়ন, হস্তশিল্প, দিনমজুরি, রাজমিস্ত্রি, গাড়িচালনা, নার্সারি ইত্যাদি করে অন্তত কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়। অনুকূল পরিবেশ এলাকার মতো পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সারাবছরের খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করতে এবং জুমচাষ পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার এখন সময়ের দাবি। এমতাবস্থায় পাহাড়ি বিশাল এলাকাকে খাদ্য উৎপাদনের যথাযথ অংশীদার করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় ধানের উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি এবং লাগসই ধানভিত্তিক শস্যবিন্যাসের উন্নয়ন ঘটানো অতিব জরুরি।
লেখক : প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর