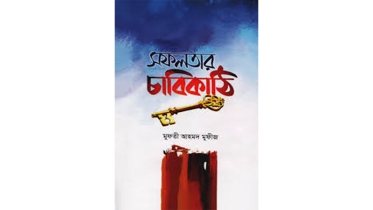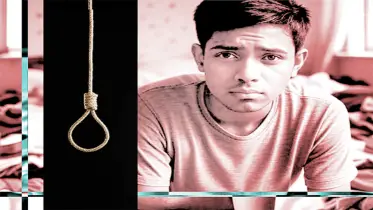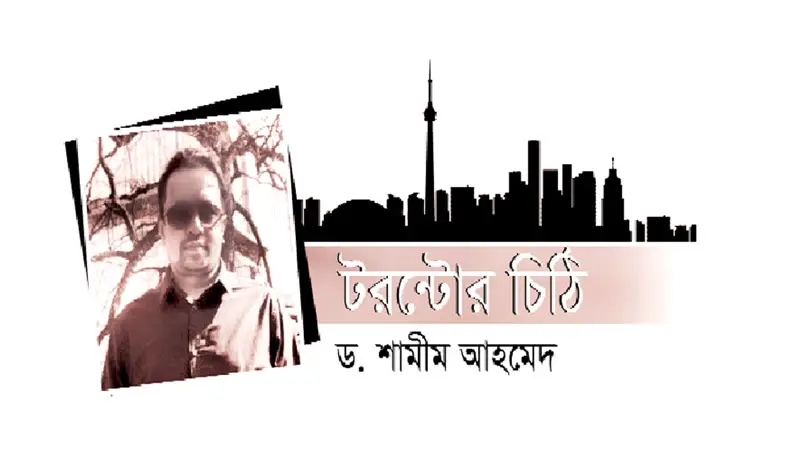
ইংরেজি Truth and Reconciliation-এর তেমন ভালো বাংলা পাওয়া যায় না। সাংবাদিক বন্ধু ইশতিয়াক খানের সঙ্গে আলাপ করে সবচেয়ে কাছাকাছি এবং গ্রহণযোগ্য বাংলা যেটি পাওয়া গেল তা হচ্ছে সত্যের প্রকাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আমি আমার পুরো লেখায় এই বাংলাটিই ব্যবহার করব Truth and Reconciliation বোঝানোর জন্য। সত্যের প্রকাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারণাটি মানব ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। যুদ্ধ, গণহত্যা, ঔপনিবেশিকতা কিংবা রাজনৈতিক নিপীড়নের মাধ্যমে মানুষ যখন মানুষকে আঘাত করে, সেই আঘাত শুধু ব্যক্তিগত নয়- তা জাতির গভীরতম স্তরে গেঁথে যায়। এবং যদি সেই ক্ষত স্বীকৃতি না পায়, তবে তা নীরবে বাড়তে থাকে এবং একসময়ে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়। তবে যদি তা যত্নসহকারে, সততার সঙ্গে এবং নিঃস্বার্থভাবে মোকাবিলা করা যায়, তবে সত্যের প্রকাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া এমন ক্ষত সারাতে পারে যা রাজনীতি কিংবা শাস্তি কখনো পারে না। এই পথেই হাঁটার চেষ্টা করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, রুয়ান্ডা- আরও কিছু দেশ। এদের কারও কারও সাফল্য আংশিক, তবে পুরোপুরি সফল কেউই হয়েছে, এমনটা দাবি করা অনুচিত হবে। প্রশ্ন শুধু এই নয় যে এই প্রক্রিয়া কাজ করে কি না- প্রশ্ন আরও জটিল: এই পদ্ধতি কি বাংলাদেশে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে? যেখানে আজকের রাজনৈতিক বিভাজন কেবল স্পষ্ট নয়, শ্বাসরুদ্ধকর রকমের সংবেদনশীল?

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের ছায়ায়, একটি অমানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ১৯৪৮ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত জাতিগত বৈষম্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা এবং লাখ লাখ কৃষ্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানকে সম্মানহীন করে রাখে। এই ব্যবস্থার পতনের পর, যখন নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বাধীন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রথমবারের মতো সব জাতির অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে, তখন দেশটি একটি গভীর নৈতিক সংকটে পড়ে- কীভাবে সামনে এগোবে রক্তপাত ছাড়াই? ১৯৯৫ সালে 'Promotion of National Unity and Reconciliation Act'-এর অধীনে গঠিত হয় Truth and Reconciliation Commission (TRC), যার নেতৃত্বে ছিলেন আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু। এটি হয়ে উঠেছিল ট্রানজিশনাল জাস্টিস বা সংক্রমণকালীন ন্যায়বিচারের একটি আন্তর্জাতিক মডেল। এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯৬০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের সত্য উন্মোচন করা, যাতে ভুক্তভোগীরা তাদের গল্প বলতে পারেন এবং অপরাধীরা পূর্ণ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ক্ষমার আবেদন করতে পারে। এই শুনানিগুলো টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হতো এবং সারাদেশের মানুষ নির্যাতনের, খুনের এবং জোরপূর্বক উচ্ছেদের বাস্তব কাহিনী শুনত। উদ্দেশ্য ছিল ঘরের ভেতরেই যেন এক জাতীয় স্বীকারোক্তির আবহ তৈরি হয়। ৭০০০-এরও বেশি অপরাধী স্বীকারোক্তি দিয়েছে এই প্রক্রিয়ায়; ২০০০০-এর বেশি ভুক্তভোগী তাদের বর্ণনা দিয়েছেন, কমিশন ৭০০০ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং প্রায় ১৯০৫০ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য নথিভুক্ত করেছে। ৭১১১ জন ক্ষমার আবেদনকারীর মধ্যে ৮৪৯ জনকে শর্তসাপেক্ষে ক্ষমা দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটি ছিল restorative justice ভিত্তিক- শাস্তিমূলক নয়, বরং সমাধানমুখী। এর অনুপ্রেরণা ছিল Ubuntu- একটি আফ্রিকান দার্শনিক ধারণা, যেখানে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। TRC-এর সাফল্য ছিল এর স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তির মধ্যে, কিন্তু তা নিখুঁত ছিল না। ক্ষুদ্র দৈনন্দিন অপরাধগুলো কমিশনের ''gross violations'' সংজ্ঞার বাইরে ছিল এবং ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও অনেকেই হতাশ হন। অনেকে মনে করেন, অপরাধীদের পূর্ণ দায়মুক্তি দেওয়ায় সত্যিকারের বিচার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে এটি গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি গড়ে দিলেও, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও জাতিগত উত্তেজনা আজও বিরাজমান-ইঙ্গিত দেয় যে সত্যের প্রকাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ এখনো অসমাপ্ত।
রুয়ান্ডার পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ। ১৯৯৪ সালের গণহত্যা- যেখানে মাত্র ১০০ দিনে প্রায় দশ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিলেন- মানব ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্ট হত্যাযজ্ঞ। হুতু ও তুতসিদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ, যা উপনিবেশিক শাসন এবং দীর্ঘদিনের বৈষম্যের ফলে তীব্র হয়ে উঠেছিল, তা প্রেসিডেন্ট জুভেনাল হাবিয়ারিমানার হত্যার পর বিস্ফোরিত হয়। হাতে হাতুড়ি, দা আর লাঠি নিয়েই পাশের বাড়ির মানুষ পরিণত হয় খুনিতে। এই হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটায় পল কাগামের নেতৃত্বাধীন Rwandan Patriotic Front, কিন্তু তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এক প্রায় অতিমানবীয় কাজ- যেখানে অপরাধী ও ভুক্তভোগী একই পাড়ায় থাকে, সেখানে কীভাবে গড়ে উঠবে পুনর্গঠিত রাষ্ট্র? রুয়ান্ডার বিচারব্যবস্থা তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত, ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি আসামিকে সামাল দেওয়ার মতো অবকাঠামো ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালে গঠিত হয় National Unity and Reconciliation Commission এবং ২০০৩ সালে পুনর্জীবিত হয় Gacaca আদালত- একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ বিচারব্যবস্থা। প্রায় ২০ লাখ মামলা নিষ্পত্তি করে এই কাঠামো, যেখানে নির্বাচিত স্থানীয় বিচারকরা ক্ষমা, স্বীকারোক্তি এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নির্ধারণ করতেন। প্রায় ৬৫ শতাংশ মামলায় আসামিদের দোষ প্রমাণ হয়, শাস্তি হয় কারাদণ্ড থেকে সমাজসেবা পর্যন্ত। Itorero ry'Igihugu-এর মতো আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি যুবকদের মধ্যে সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম গড়ে তোলার চেষ্টা করে, জাতিগত পরিচয়ের পরিবর্তে ‘বনিয়ারোয়ান্ডা’ পরিচয়কে সামনে আনে। এই মডেলের শক্তি ছিল এর স্থানীয়করণে- মানুষ নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে স্বীকারোক্তি পেয়েছে, প্রতিকার পেয়েছে। কিন্তু এর দুর্বলতাও ছিল : চাপ প্রয়োগ করে স্বীকারোক্তি আদায়, অসম শাস্তি, হুতু ও টোয়া জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করার অভিযোগ উঠেছে। কাগামে সরকারের দমনমূলক চরিত্রের কারণেও এই সত্যের প্রকাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তবু রুয়ান্ডা আজ আর্থিকভাবে সফল, রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল, যদিও গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগ এখনো রয়ে গেছে।
অন্যান্য দেশও চেষ্টা করেছে সত্য ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে অতীতের ক্ষত সারাতে। সিয়েরা লিওনের ঞজঈ, যা ১৯৯১-২০০২ সালের নির্মম গৃহযুদ্ধের পর গঠিত হয়, অনেক ভুক্তভোগীর কণ্ঠ তুলে ধরলেও রাজনৈতিক বিভাজন ও অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ এই প্রক্রিয়াকে অসম্পূর্ণ রেখেছে। কানাডায় ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত TRC পরিচালিত হয় আদিবাসী শিশুদের আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ভুলিয়ে দিতে সেখানে যে অত্যাচার নিপীড়ন চালানো হয় সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। এই স্কুলগুলোতে তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ধ্বংস করা হতো, এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চালানো হতো। TRC ৯৪টি পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে, যার বাস্তবায়ন চলমান। এই প্রক্রিয়াগুলো দেখিয়ে দেয়- সত্যের প্রকাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা একটি সমাধানের সূত্রপাত মাত্র, কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ সঠিক না হলে এগুলো শুধুই শব্দ ও পুস্তকে সীমাবদ্ধ থাকে।
এবার আসি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। ১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে নানা মতো নানা পথ ঘোলা করার চেষ্টা করেছে। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড, সামরিক শাসন, রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান এবং বিরোধী দলের দমন- সব কিছুই সময়ে সময়ে বিকৃত হয়েছে। ইতিহাস এখানে অধ্যয়নের বিষয় নয়, বরং রাজনৈতিক হাতিয়ার। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তৎকালীন সরকার পতনের মাধ্যমে এই পুরানো ক্ষত আবার নগ্নভাবে সামনে চলে আসে। দীর্ঘদিনের কর্তৃত্ববাদী শাসন, গুম-খুন, মিডিয়া দমন এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের অবসান ঘটানোর আপাতত লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠা এক ছাত্র আন্দোলনে বহু মানুষ নিহত হয়। এরপর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু দেশ আজও গভীরভাবে বিভক্ত। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং আওয়ামী সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-এই ক্ষত এখনো তাজা।
এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে- বাংলাদেশে কি সত্য ও পুনর্মিলনের প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব? কঠিন হলেও উত্তর সম্ভবত- এখনো নয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে কল্পনা করা যেমন যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি জরুরি। কারণ বিকল্প হচ্ছে প্রতিশোধ, অস্থিতিশীলতা এবং এমন এক ভবিষ্যৎ যা ভয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, আশার ওপর নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভুক্তভোগীভিত্তিক মডেল এবং রুয়ান্ডার গ্রামভিত্তিক বিচারব্যবস্থা থেকে আমরা শিখতে পারি। বাংলাদেশেও এমন একটি TRC গঠন করা যেতে পারে, যেখানে সব সরকারের সময়ে গুম, নির্যাতন এবং রাজনৈতিক দমন-নিপীড়নের শিকার মানুষেরা নিরাপদে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবেন। অপরাধীদেরও আহ্বান জানানো যেতে পারে সত্য বলার জন্য, বিনিময়ে শর্তসাপেক্ষ ক্ষমা বা পুনর্বাসনভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে। কিন্তু রাজনৈতিক বিভাজনের বাস্তবতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়- যদি এই উদ্যোগ অনির্বাচিত কোনো সরকারের নেতৃত্বে শুরু হয়, তবে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। জাতিগত ও ধর্মীয় উত্তেজনাও স্থানীয় পর্যায়ে জটিলতা তৈরি করতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা, যেমন- Human Rights Watch যেভাবে প্রস্তাব দিয়েছে, তা সহায়ক হবে কিনা সে প্রশ্ন রয়েই যায়। বাংলাদেশে জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেন- বিশেষ করে যখন ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে রুশ গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন থেকে যা জানা যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি এমন প্রক্রিয়া শুরু হয়, তবে তা অবশ্যই হতে হবে বাংলাদেশের নেতৃত্বে- বিদেশি হস্তক্ষেপের ছায়াও যাতে তাতে না পড়ে।
এর লক্ষ্য হতে হবে সহিংসতা ঠেকানো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং এই পরিবর্তনকে শুধু সরকার পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি নৈতিক নবযাত্রায় রূপ দেওয়া। সত্য ও সহানুভূতি, বিচার ও অন্তর্ভুক্তির মধ্যে সুষম সমন্বয়ই হবে এই প্রক্রিয়ার সফলতার চাবিকাঠি। একজন প্রবাসী কানাডিয়ান বাংলাদেশি হিসেবে দূর থেকে দেখলেও, আমি দেশের ভিতরকার কম্পন অনুভব করি। তাই বলছি-এই বীজ রোপণ করার সময় এখনই। হয়তো এখনই তা অঙ্কুরিত হবে না, কিন্তু একদিন হবেই। কারণ যে জাতি নিজের সত্যের মুখোমুখি হতে পারে না, সে জাতি চিরকাল নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করে যায়। আর সে যুদ্ধে কখনই প্রকৃত বিজয় আসে না।
৬ জুলাই ২০২৫, টরন্টো, ক্যানাডা
[email protected]
প্যানেল/মো.