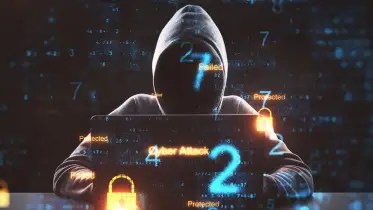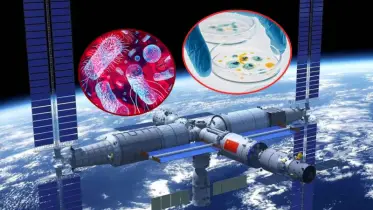ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেছে। মঙ্গলবার এ সেবা চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার। একই দিনে স্টারলিংক তাদের এক্স (আগে টুইটার) অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে বাংলাদেশে সেবা চালুর ঘোষণা দেয়।
বাংলাদেশে স্টারলিংকের সেবা পেতে হলে সরাসরি তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘রেসিডেনশিয়াল’ প্যাকেজ নির্বাচন করতে হবে। এরপর ‘অর্ডার নাউ’ অপশন থেকে নিজের অবস্থান বেছে নিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে পেমেন্ট সম্পন্ন করে ‘প্লেস অর্ডার’ অপশনে ক্লিক করতে হয়। পেমেন্টের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সরঞ্জামসহ পুরো সেটআপ গ্রাহকের ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ব্যবহারকারী খুব সহজেই নিজেই ডিভাইসটি ইনস্টল করতে পারবেন।
বর্তমানে বাংলাদেশে স্টারলিংক দুটি প্যাকেজ চালু করেছে— রেসিডেন্স এবং রেসিডেন্স লাইট। রেসিডেন্স প্যাকেজে মাসে খরচ হবে ৬ হাজার টাকা, অন্যদিকে রেসিডেন্স লাইট প্যাকেজে খরচ ৪ হাজার ২০০ টাকা। তবে এ সেবার জন্য এককালীন সরঞ্জাম ক্রয়ে খরচ করতে হবে ৪৭ হাজার টাকা। এই সেটআপের মধ্যে রয়েছে অ্যানটেনা, কিকস্ট্যান্ড, রাউটার, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তার।
গ্রাহক একজন হলেও এটি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। একটি ডিভাইস থেকে ২০ থেকে ৫০ মিটার দূরত্বে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাবে। গ্রামীণ এলাকায় এই পরিসর ৫০ থেকে ৬০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ফলে কেউ চাইলে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতে পারবেন, আবার একাধিক ব্যক্তি মিলেও ব্যবহার করতে পারবেন।
উচ্চগতির কারণে স্টারলিংক বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটি প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৩০০ মেগাবিট গতির সীমাহীন ইন্টারনেট সেবা দিতে সক্ষম। বিশেষ করে যেসব দুর্গম বা প্রত্যন্ত এলাকায় এখনো ফাইবার সংযোগ বা শক্তিশালী মোবাইল নেটওয়ার্ক পৌঁছায়নি, সেসব এলাকায় স্টারলিংক কার্যকর সমাধান হিসেবে কাজ করতে পারে।
সরকারের মতে, দেশে এখনো মাত্র ৩০ শতাংশ মোবাইল টাওয়ার ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে সংযুক্ত। বাকিগুলো এখনো মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল, যা কম সক্ষমতার। স্টারলিংকের মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতা দূর করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও রাজধানীসদৃশ উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।
সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিরাপত্তার বিষয়েও নজর রাখা হচ্ছে। স্টারলিংককে স্থানীয় গেটওয়ে ব্যবহার করতে বাধ্য করা হবে। বর্তমানে এটি বিদেশি গেটওয়ের মাধ্যমে ৯০ দিনের পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরপর তাদের দেশের ভেতরে স্থাপিত গ্রাউন্ড স্টেশনের মাধ্যমে স্থানীয় গেটওয়ের সাহায্যে সেবা চালাতে হবে।
জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছে যে, দেশের ডেটা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্টারলিংককে আইনগত আড়িপাতার বিধান মানতে হবে এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, স্টারলিংকের যন্ত্রপাতি দেশে আনতে হলে সরকারের ছাড়পত্রও নিতে হবে।
স্টারলিংক বাংলাদেশে বাজার ধরার চেষ্টা করছিল ২০২১ সাল থেকেই। তবে শুরুতে সরকারি পক্ষ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে তারা বাংলাদেশ সফরে এসে বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করে। পরে প্রযুক্তি পরীক্ষাও করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর স্টারলিংকের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগোয়। ২৯ মার্চ প্রতিষ্ঠানটিকে বিনিয়োগ নিবন্ধন দেয় বিডা এবং এর এক মাস পর ২৯ এপ্রিল বিটিআরসি থেকে ১০ বছরের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়।
প্রসঙ্গত, দক্ষিণ এশিয়ার ভুটান ও শ্রীলঙ্কায় ইতিমধ্যে স্টারলিংক তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশে তারা এখন বিদেশি গেটওয়ে ব্যবহার করে পরীক্ষা চালালেও ভবিষ্যতে স্থানীয় গেটওয়ের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালাতে হবে। স্টারলিংক ছাড়াও অ্যামাজন কুইপার, ওয়ান ওয়েব, স্যাটেলয়েট ও টেলিসেটসহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সরকার বলেছে, এসব কোম্পানি স্টারলিংকের মতোই একই ধরনের সুবিধা পাবে।
রাকিব