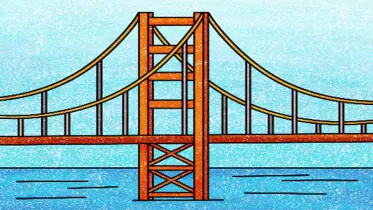বাংলাদেশের ইতিহাস, অর্থনীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত একটি শব্দ- পাট। একে বলা হয় ‘সবুজ সোনা’, কারণ একসময় পাটই ছিল দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭০ শতাংশই আসত পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে। অথচ আজ, যাদের হাতে এই সোনালি আঁশের জন্ম, সেই পাট চাষিরা বারবার অবহেলার শিকার হচ্ছেন, পাচ্ছেন না তাদের ন্যায্য দাম। এই চিত্র শুধু হতাশাজনক নয়-জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের এক গুরুভার দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ। এক সময়ের গর্ব, আজ সংকটে, ১৯৭০-এর দশকে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ১০ লাখ টন পাট রপ্তানি করত। বর্তমানে এই পরিমাণ নেমে এসেছে সাড়ে ৭ লাখ টনের নিচে (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পাট অধিদপ্তর, ২০২৩)। বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির পরও বাংলাদেশের পাটশিল্প ঠিকমতো পুনরুজ্জীবিত হয়নি। একটি বড় কারণ-পাট উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ ক্রমেই কমে যাচ্ছে, কারণ তারা উৎপাদন খরচের তুলনায় ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না।
বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০২৪ সালে এক বিঘা জমিতে পাট উৎপাদনের খরচ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৪ হাজার টাকা, কিন্তু হাটে সেই পাট বিক্রি করে পাওয়া গেছে সর্বোচ্চ ১২-১৩ হাজার টাকা। এতে কৃষকের প্রতি বিঘায় লোকসান হয়েছে ১ হাজার টাকার বেশি। এই লোকসান সরাসরি কৃষকের খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে। অথচ কৃষকের ঘাম ও শ্রমের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে দেশের বহুমুখী শিল্প ও রপ্তানি সম্ভাবনা। পাট মৌসুম আসন্ন, এখনই সময় বর্তমানে বাংলাদেশে পাট কাটার মৌসুম জুলাই-আগস্টে শুরু হয়। অর্থাৎ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন পাট বাজারে আসবে। এই সময়ে মধ্যস্বত্বভোগী ও অসাধু ব্যবসায়ীরা চাষিদের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে দরপতনের কারসাজি করে থাকেন। সরকারি সংস্থাগুলো দৃশ্যত ‘ক্রয় কেন্দ্র’ খুললেও বাস্তবে তা হয় প্রদর্শনমূলক ও সীমিত পরিসরে, যা অধিকাংশ চাষির নাগালের বাইরে। মধ্যস্বত্বভোগী নয়, সরাসরি কৃষকের হাতে লাভ। বাংলাদেশ পাট অধিদপ্তরের তথ্যমতে, প্রতি মৌসুমে পাট উৎপাদনে ৩০ লক্ষাধিক কৃষক পরিবার যুক্ত থাকেন। কিন্তু কৃষকের হাতে লাভ পৌঁছায় না। একদিকে খরচ বেশি, অন্যদিকে মিল মালিকরা দাম নির্ধারণ করেন নিজেদের সুবিধামতো। অধিকাংশ চাষি পাট সংরক্ষণের জায়গা ও উপায় না থাকায় উৎপাদনের পরপরই বাধ্য হন নিম্নমূল্যে বিক্রি করতে। ফলে লাভ তো দূরে থাক, উৎপাদনের মূলধনও উঠে আসে না। সরকারের উচিত- হাট পর্যায়ে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা, কৃষক পর্যায়ে সরাসরি ডিজিটাল, কেনাবেচার প্ল্যাটফর্ম চালু করা, সরকারি পাট গুদাম বা মিলকে বড় পরিসরে পাট সংগ্রহে বাধ্য করা, বিআরডিবি, কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এর মাধ্যমে কৃষিঋণ সহজীকরণ, পাট সংরক্ষণের জন্য স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ কেন্দ্র ও শেড নির্মাণ, পাটশিল্পের অবস্থা: কিছু চিত্র
বর্তমানে দেশে সক্রিয় পাটকল রয়েছে প্রায় ৯০টি, যার মধ্যে সরকার পরিচালিত ১৮টি মিল ২০২০ সালের পর বন্ধ বা বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় রয়েছে। (তথ্যসূত্র: পাট অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ২০২৩) অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারত, যেখানে বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানি করে- তারা একে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে দেখছে। তাদের সরকার প্রতি বছর পাটচাষিদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (গঝচ) নির্ধারণ করে, যা কৃষক নিশ্চিন্তে বুঝে পান। অথচ বাংলাদেশে এমন কোনো কাঠামো নেই।
পাটশিল্প কেবল কৃষি নয়, এটি শিল্প, পরিবেশ ও রপ্তানি খাতের সংযোগকারী সেতু। আজ বিশ্ব যখন প্লাস্টিক বর্জনের আন্দোলনে, তখন বাংলাদেশ পাটকে সামনে রেখে পরিবেশবান্ধব পণ্যের বিশ্ব বাজার দখল করতে পারে। পাট চাষে ফেরাতে হবে সম্মান, দিতে হবে আর্থিক নিরাপত্তা। তাহলেই এই সোনালি আঁশ আবারও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে। পাট চাষিকে বাঁচাতে পারলে পাট শিল্প বাঁচবে। আর পাট শিল্প বাঁচলে রক্ষা পাবে দেশের কৃষি অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি। তাই সময়ক্ষেপণ নয়, এখনই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নিতে হবে। পাট মৌসুমের আগেই ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে না পারলে আগামীতে এই ঐতিহ্যবাহী খাতকে টিকিয়ে রাখা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। পাট চাষিকে তার শ্রমের দাম দিন-কারণ সোনালি আঁশ মানেই বাংলাদেশের আত্মমর্যাদা।
মো. শামীম মিয়া
জুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা
প্যানেল/মো.