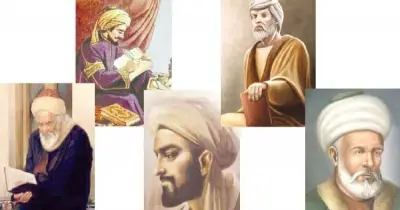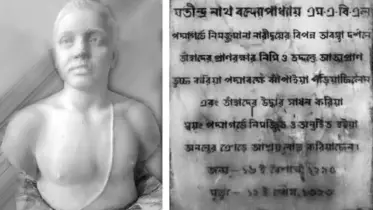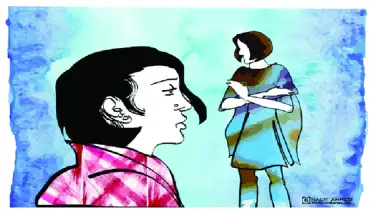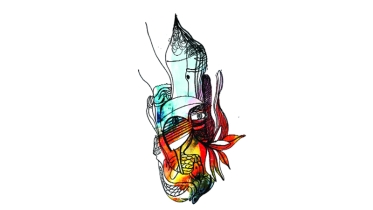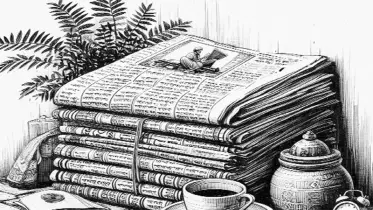মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার্থে গুহা বা ছাদে চিত্র আঁকত। মানুষের মনের এ আদি প্রচেষ্টার উপজীব্য বিষয় ছিল পশু-পাখি। যুগের পরিবর্তনের এ ক্রমধারায় মানুষ আদিকাল পেরিয়ে মধ্যযুগের চিত্রকলার পরিধিতে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি যোগ করতে সমর্থ হয়। এ যুগের চিত্রকলার বিষয় ছিল পরলোকমুখিতা। এরপর রেনেসাঁর উত্তরণের ফলে চিত্রকলার অগ্নিপুরুষদের রং তুলির সংস্পর্শে চিত্রকলা হয়ে ওঠে আধুনিক। আর এর বিষয় হয় মানুষের জাগরণ ও মানবতাবাদ বা হিউম্যানেজিম। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি মনে করতেন, ‘মানুষের চোখ হলো আত্মার জানালা’। চিত্রকরদের চোখ আর আত্মার সম্মিলন আধুনিক যুগে চিত্রশিল্পে মানবতাবাদের বিপ্লব ঘটেছে। ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হয় শিল্পের এ শাখাটি।
রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণ ফরাসি (জবহধরংংধহপব/র্যনেসঁস) ইতালির জবহধংপরসবঃড় মধ্যযুগের পরে এবং রিফর্মেশনের আগে বিশেষ করে ইতালিতে এবং সাধারণত গোটা ইউরোপের এক ঐতিহাসিক যুগকে বোঝায়। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীকাল পর্যন্ত শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য বিদ্যায় মানুষের চিন্তার বিস্তার ঘটে। মানুষের বুদ্ধিবিত্তিক শক্তির বিকাশ প্রসারিত হয়ে মধ্যযুগের গতানুগতিক সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। চিত্রকলায় শুরু হয় মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার। আর একটু ব্যাপকভাবে বলতে গেলে পুনর্জাগরণ সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, রাষ্ট্র ও সমাজের চিন্তা-চেতনায় সর্বোপরি ক্লাসিকাল বিদ্যাচর্চার পুনারাম্ভ হয়। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির উন্মেষ ইউরোপ বিশেষ করে ইতালিতে মানুষের মনের নবীন প্রেরণার কর্মশক্তির উদ্বোধনই ইতিহাসে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ নামে পরিচিত। রেনেসাঁকে ব্যাপক অর্থে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা কালও বলা যায়।
চিত্রকলায় প্রাথমিক পর্যায়ে রেনেসাঁ- ইতালিতে ১৩শ শতকের শেষভাগে ও ১৪শ শতকের প্রথমভাগে নিকোলা পিসানো ও তাঁর পুত্র জোভান্নি পিসানো পিসা তাঁদের ভাস্কর্যের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ক্ল্যাসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ এই শিল্পীরা প্রাচীন রোমান সভ্যতাগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া খচিত অলঙ্কিত প্রস্তরনির্মিত শবাধারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ‘পালপিটস অফ দ্য ব্যাপ্টিসটেরি’ এবং ‘ক্যাথেড্রাল অফ পিসা’। জোভান্নি পিসানোর সমসাময়িক ফ্লোরেন্সিয় চিত্রশিল্পী জত্ত, রূপকধর্মী চিত্রাঙ্কনের রীতির উদ্ভাবন করেন যা তার গুরু শিমাবুয়ে ও সমসাময়িকদের তুলনায় বেশ প্রকৃতিবাদী, ত্রিমাত্রিক, জীবন্ত, বাস্তবধর্মী এবং ক্লাসিসিস্ট ছিল। জত্ত যার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ‘ দ্য সাইকেল অফ দ্য লাইফ ক্রাইস্ট’ যা এরেনা চ্যাপেল পাড়ুয়া, ইতালিতে অবস্থিত। প্রাথমিক পর্যায়ে রেনেসাঁর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও লুকচেম্ভার। এই সময়ের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে, ভন আইক, তাঁর ভাই হুবারট ভন আইক, রবাট ক্যাম্পিন, হ্যান্স মেস্লিং প্রমুখ তাঁদের চিত্রকলা আদি ইতালীয় রেনেসাঁ চিত্রকলার অধীনে গড়ে ওঠে। তাঁদের শৈলী মধ্যযুগীয় চিত্রকলার অন্তর্ভুক্ত রঙিন প্রলেপ, রঙিন কাঁচ ও আলোকসজ্জা থেকে গড়ে ওঠে। চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে তারা ব্যবহার করে তেল রং যা বহুকাল থেকেই আনুষঙ্গিক বস্তু রঙিন চিত্রাঙ্গনে ব্যবহার হয়ে আসছিল। কারণ তা ছিল নমনীয় ও অপেক্ষাকৃতভাবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপৃত। নেদারল্যান্ডসের চিত্রশিল্পীগণ রৈখিক, পরিপ্রেক্ষিত, বিভিন্ন অংশে সুসমতাকে মাথায় রেখে একটি চিত্র প্রস্তুত করেনি, তাঁরা অনুক্রমিক কাঠামোর সমানুপাত ও ধর্মসংক্রান্ত প্রতীকসমূহের ওপর মধ্যযুগীয় অভিমত কেই বজায় রেখেছেন। পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও মনুষ্যনির্মিত উপাদানগুলোকে বাস্তবধর্মী দিক থেকে বর্ণনা করেই আহল্লাদ হয়েছেন। ইতালিতে ব্রুনেলেস্কি যিনি ফ্লোরেন্সে ক্যাথেড্যার এর গম্বুজের স্থাপতি হিসেবে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন তাঁর নির্মিত ভাস্কর্য ‘সান্টা মারিয়া’ পরিপ্রেক্ষিতের ওপর গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা চিত্রশিল্পী মাসাচ্চিকেও প্রভাবিত করেছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল মানবতাবাদী এবং যৌন উদ্রেককারী ডেভিডের খোদাই করা প্রতিকৃতি এবং গাত্তামেলার স্মৃতিস্তম্ভ। মাসাচ্চিও বেশ কয়টি প্যানেল পেইন্টিং চিত্রাঙ্কন করেন তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্ম ‘ফ্রেস্কো সাইকেল-সমূহ’ যা তিনি ব্র্যাঙফাচ্চি চ্যাপেলে বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী ম্যানোলিনোর সঙ্গে শুরু করেন এবং পরবর্তী চিত্রশিল্পীদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এদের মধ্যে মাইকে এঞ্জেলো অন্যতম। ফ্রান্সে আদি রেনেসাঁর যুগে রাজসভার চিত্রশিল্পী জ-ফুফে ইতালি পরিদর্শন করেন (১৪৩৭) সালে ফলে তাঁর চিত্রাঙ্কনে ফ্লোরেন্সীয় চিত্রশিল্পরা যেমন: পাওলো উচ্চেলোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি সপ্তম চার্লস প্রমুখের প্রতিকৃতিসমূহের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক আর একজন শিল্পী ছিলেন যিনি বিখ্যাত কাজ ‘গির্জাবেদী চিত্র’ অঙ্কন করেন যা শৈলীগত দিক থেকে ইতালির থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এঈুয়ের কোয়ারত তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম, ‘পিয়েতা অব অল্টার পিস’ এবং জ হেই আঁকেন ‘মউলিন্স অব অল্টার পিস’ এই শিল্পকর্মগুলোতে বিয়েলিজম এবং আলোকসজ্জা প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এক মধ্যযোগীয় নিয়মানুগত্য যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্বর্ণখচিত। ইতালি ছাড়াও আমরা বিশে^র বিভিন্ন প্রান্তে আদি রেনেসাঁর উত্তরণের সন্ধান পাই। ১৫শ শতকে ফ্লোরেন্স ভূখ-ের মধ্যেই শৈল্পিক ও প্রতিভাবান যেমন: মাসাচ্চিও, ব্রুনেলেস্কি, গিবারটি, পিয়োরো ডেলা ফ্রান্সেস্কা, ডোনাটেল্লো ও মাইকেলোতাসো প্রমুখের উপস্থিতি শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মেজাজের ভাবধারার জন্ম দেয় যার দ্বারা অভিভূত হয় হাই রেনেসাঁ বা অন্তিম রেনেসাঁর মহান ব্যক্তিরা।
১৫শ শতকের ফ্লোরেন্সিয় চিত্রশিল্পীদের কাছে পরিপ্রেক্ষিত, আলোকসজ্জা প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চিত্রশিল্পী উচ্চেলো তাঁর অঙ্কনে ‘পরিপ্রেক্ষিতের’ প্রকাশ করতে এতটাই আচ্ছন্ন ছিল যে-চিত্রশিল্পী ভাসারীর মতে, ‘তাঁর নিদ্রা পর্যন্ত বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছিল’ তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ‘দ্য ব্যাটল অব স্যান ও রোম্যানো’। ইতালির চিত্রকলায় আদি রেনেসাঁর প্রভাবের সমাপ্তি তাঁর শুরুর মতোই একটি কমিশনের মাধ্যমে হয়, যেটি শিল্পীদের একীভূত করে। তবে এবার শিল্পীরা প্রতিযোগী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। সহযোগিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পোপ সিক্রটাস। এই ফ্রেস্কো সাইকেল।
দ্য ফোরথ ‘পেপাল চ্যাপেল’ পুনর্নির্মাণ করেন যা তাঁর সম্মান রক্ষার্থে সিস্টাইন চ্যাপেল নামকরণ করা হয়। পোপ সিক্রটাইস দ্য ফোরথ সান্দ্রো বত্তিসেল্লি, পিয়েত্রো পেয়জিনো, দমেনিকো গিরল্যান্দাইয়ো ও ফসিনো রোসেলি প্রমুখ শিল্পীদের একটি দল গঠন করে তাঁরা একাত্রে ফ্রেস্কো সাইকেল দিয়ে পেপাল চ্যাপেলের দেয়াল সজ্জিত করেন। এই ফ্রেস্কো সাইকেল লাইফ অব ক্রাইস্ট এবং লাইফ অব মোসেস তুলে ধরে। ষোলোটি বিশালাকার চিত্রে চিত্র শিল্পীরা প্রত্যেকে নিজস্ব শৈলীতে কাজ করা সত্তেও বিন্যাসের নীতির ওপর তাঁরা একমত হয়েছিলেন। এবং আলোকসজ্জিত করার পদ্ধতি, রৈখিক, পারিপার্শিক পরিপ্রেক্ষিত, দৈহিক গঠনতন্ত্র, ফোরসরটেনিং, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করেন। চিত্রশিল্পী গিবারটি, ভেরোচ্চিও, গিরল্যান্দাইয়ো ও পেরুজিনোর ফ্লোরেন্সিয় চিত্রকলায় এগুলোকে এক উন্নত পর্যায় নিয়ে যায়। ইউরোপের দেশে দেশে চিত্রকলায় রেনেসাঁর আদি পর্ব থেকে (১৪৭৫-১৫২৫) আরো উচ্চতায় পৌঁছে যায় যার প্রভাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বজনবিদিত ও প্রতিভার অধিকারী শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তাঁর জীবন ভর অধ্যায়ন ও নির্ভুল লিপিবদ্ধকরণের ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। চিত্রশিল্পের বিভিন্ন দিকগুলো যেমন-আলোকসজ্জা, রৈখিক, পারিপাশির্^ক পরিপ্রেক্ষিত, দৈহিক গঠনতন্ত্র, ফোরসরটেনিং এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রদান। তিনি তেল রং তাঁর চিত্রাঙ্গনের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে অবলম্বন করেন। ফলে আলো ও পারিপাশির্^ক পটভূমির উপর তাঁর অনেক স্বাভাবিক ও নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হন। তাঁর মোনালিসায় তার প্রমাণ মেলে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি চিত্রকলায় এক নবজাগরণের সূচনা করেন। চিত্রকলায় শবব্যবচ্ছেদ কঙ্কাল ও পেশীসংক্তান্ত দৈহিক গঠনতন্ত্রের বিষয় নিয়ে আসে। পরবর্তীতে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর চিত্রিত ‘ দ্য লাষ্ট সাপার’ এ মানব অনুভূতির রূপায়ণ, ধর্মসংস্কার, চিত্রাঙ্কানের মানদ- খুঁজে পাওয়া যায়। লিওনার্দোর কনিষ্ঠ সমসাময়িক মাইকেলেঞ্জেলো সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিপথে যান। মাইকেল অ্যাঞ্জোলো তাঁর চিত্রকলা কিংবা ভাস্কর্য কোনোটাই মানবদেহ ছাড়া অন্য কোনো প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। তিনি তাঁর কৌশলকে নিখুঁত করে গড়ের তুলেন রোমের ডেভিডের বিশালাকার মার্বেল মূর্তি ও বেশ কয়েকটি পিয়েতা তৈরির ম্যাধমে। এর পর তিনি মানবের দৈহিক গঠনতন্ত্রের বিশেষ অভিব্যক্তির সম্ভাবনা অনুসন্ধান করেন। তিনি সিস্টাইন চ্যাপেলের এর ছাদ অলঙ্করণ করেন রূপকধর্মী রচনার সেরা শিল্পকর্ম হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। পরবর্তী ইউরোপীয় প্রজন্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
লিওনার্দো ও মাইকেলঞ্জেলোর পাশাপাশি ছিলেন উচ্চতর রেনেসাঁর তৃতীয় কনিষ্ঠ চিত্রশিল্পী রাফায়েল, যিনি তার স্বল্প সময়ের জীবনে সংখ্যক জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক প্রতিকৃতি আঁকেন। দ্বিতীয় পোপ জুলিয়াস , দশম পোপ নিও এর প্রতিকৃতি এবং ম্যাডোনা ও ক্রাইস্ট চাইল্ড এর বহু সংখ্যক চিত্র আঁকেন যার মধ্যে সিস্টাইন ম্যাডোনার চিত্রও রয়েছে। উত্তর ইতালির উচ্চতর রেনেসাঁর প্রতিনিধি হলো জোভাননি বেলিনির ধর্মসম্বন্ধীয় চিত্রসমূহ ‘সাক্রেড কনভার্সেশন’, ‘দ্য টেম্পেস্ট’ যার বিষয় বস্তু নিয়ে এখনো জল্পনা কল্পনা চলছে।
জার্মান চিত্রকলায় রেনেসাঁ উত্তর ইউরোপের বৃহত্তর শ্রেণির আওতায় পড়ে থাকে যাকে উত্তরাঞ্চলীয় রেনেসাঁও বলা হয়। জার্মান চিত্রকলায় রেনেসাঁর দৃষ্টিগোচর হয় ১৫শ শতকে তবে রেনেসাঁর এই ঝোঁক বহু বিস্তৃতি ছিল না। জার্মানির চিত্রশিল্পী গার্ডনার এর ‘আট থ্রু দি এজেস’। মাইকেল প্যাচারের চিত্রকর্ম ইতালীয় রেনেসাঁর প্রভাব মুক্ত ছিল। ১৫শ শতকে জার্মানির চিত্রশিল্প আরো সুলভ হয়ে ওঠে। চিত্রশিল্পী গার্ডনারে কথায় ‘ষোড়শ শতকের উত্তর ইউরোপীয় চিত্রশিল্পে ইতালিয় রেনেসাঁর উন্নয়নসমূহের প্রতিটি আকস্মিক সচেতনতা এবং এই নতুন শৈলীটিকে যত দ্রুত সম্ভব অঙ্গীভূত করার একটি অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়’ সবচেয়ে পরিচিত জার্মান রেনেসাঁর চিত্রকলা চর্চাকারীদের মধ্যে আব্রেখট ডিউবার (১৪৭১-১৫২৮) ক্লাসিকাল চিন্তাভাবনার প্রতি আকাবনের দ্বারা চালিত হয়ে ডিউবাধ চিত্রকলার ওপর অধ্যায়ন করেন। জার্মান চিত্রশিল্পীরা ইতালির রেনেসাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদের চিত্রকলার ব্যাপক উন্নতি সাধন করে।
রেনেসাঁর উত্তরণে গোটা পৃথিবীর চিত্রকলায় আধুনিকতার স্পর্শ লাগে। চিত্রকলায় সংযোজিত হয় ক্লাসিকাল ধারা আর ধ্রুপদী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ হলো এই ক্লাসিকাল বা আধুনিকতাবাদ যা শাস্ত্রীয় চিত্রকলাকে বুনিয়াদি করে গড়ে উঠেছে। যার বিকাশ শিল্পের শৈল্পিক মানদ- আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে রূপান্তর কর নেয়া। সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ‘ক্ল্যাসিসিজমের বৈশিষ্ট্য হলো পরিমিতিবোধ, ভারসম্যবোধ, সংযম এবং আঙ্গিক সচেতনতা। চিত্রকলায় আধুনিকতার বা রেনেসাঁর সংযোজনে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রারম্ভিক রেনেসাঁর অন্যতম মহান চিত্রশিল্পী সান্দ্রো বাত্তিচেল্লি (১৪৪৫-১৫১০) তাঁর চিত্রকর্মের বিষয় ছিল নারী তাঁর বিখ্যাত কাজ ছিল ‘ ম্যাডোনা অব দ্য ম্যাগনিফিক্যাট’, ‘এ্যাডোরেশন অব দ্য মেজাই’ ‘দ্য বার্থ অব ভেনাস (১৪৮৫) ’। ইতালীয় রেনেসাঁর কালজয়ী চিত্রশিল্পী, বিংশ শতাব্দীর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নেপথ্য জনক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) এক সুদীর্ঘ ও অক্লান্ত কর্ম সাধনার জীবন তাঁর। গির্জা ও রাজপ্রসাদের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন এবং রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের ভাস্কর্য নির্মাণের পাশাপাশি বেসামরিক ও সামরিক জ্ঞানের প্রয়োগ চিত্রকলায় অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যার ব্যবহারে মৌলিক ও গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করেন যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করে। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলো চিত্রকলায় রেনেসাঁর উত্তরণে ভূমিকা রাখে। ‘মোলিসা’ (১৫০৩-১৫০৬) তাঁর একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম যা চিত্রকলার আধুনিকতার সকল মানদ-ে উত্তীর্ণ। গোটা পৃথিবীর চিত্রকরদের উৎসাহ ও কৌতূহলের বিষয় মোনালিসা। ‘দ্য লাস্ট সাপার’ (১৪৯৫-১৪৯৮) মোলিসার পর লিওনার্দোর সেরা কীর্তি হিসেবে মনে করা হয়। ‘ভিট্রুভিয়ান ম্যান’ (ঠরঃৎাঁরধহ গধহ -১৪৮৭) এ আঁকার মধ্য দিয়ে তিনি মানব দেহের বিভিন্ন অংশের গঠনগত দিক উন্মোচন করেন যা অঙ্গব্যবচ্ছেদ হিসেবে পরিগণিত হয়। ‘লেডি উইথ অ্যান আরমিন’ (১৪৮৯-১৪৯০) সময়কালের মাঝে আঁকা একটি তৈলচিত্র। ছবিটির বিষয় একজন নারী যিনি ছিলেন মিলানের ডিউক লুভোভিকো স্করযারের প্রিয় স্ত্রী। ‘ভারজিন অব দ্য রকস’ (১৪৮৩-১৪৮৬) । এবং মানব সভ্যতাকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যায়। তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মানুষ ও মানুষের জয়গান যা ছিল রেনেসাঁর মূলমন্ত্র। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) ইতালিও রেনেসাঁর মহান ভাস্কর ও স্থপতি তাঁর শিল্পকর্ম ‘দ্য ক্রিয়েশন অব আদম’ (১৫১১-১৫১২) আঁকা ছবিটি সংরক্ষিত আছে ভ্যাটিকান সিটির সিসটাইন চ্যাপেলের সিলিংয়ে। তাঁর আর একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম, ‘দ্য লাস্ট জাজমেন্ট’ (১৫৩৬-১৫৪১)। রাফায়েল/রাফায়েল্লো (১৪৮৩-১৫২০) চিত্রশিল্পের রেনেসাঁ যুগের অন্যতম প্রধান চিত্রকর ছিলেন। ‘দ্য স্কুল অব এথেন্স’ (১৫১০-১৫১১) , ‘উইডেনিং অব দ্য ভারজিন’ তাঁর জনপ্রিয় সৃষ্টিকর্ম। ভিনসেন্ট ভ্যান গগ (১৮৫৩-১৮৯০) একজন প্রধান পোস্ট ইমপ্রেশনিজমবাদী ওলন্দাজ চিত্রশিল্প। রুক্ষ সৌন্দর্যের এবং আবেগময় সততার প্রকাশে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। সপ্রতিভর রং এর ব্যবহারের কারণে তাঁর কাজ বিখ্যাত ছিল যা বিংশ শতাব্দীর চিত্রকলায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ‘দ্য স্টারি নাইট’ তাঁর সেরা শিল্পকর্ম। আরিমাতিস (১৮৬৯-১৯৫৬) ইমপ্রেশনিস্ট ও উত্তর ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পের জনক বলা হয়। পল সেজান (১৮৩৯-১৯০৬) ফরাসি চিত্রশিল্পী ও পোস্ট ইমপ্রেশনিজম ধারার নেতৃস্থানীয় শিল্পী তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্ম ‘কার্ড প্লেয়ারস (১৮৯২)’ সালভাদোর দালি (১৯০৪-১৯৮৯) ছিলেন একজন খ্যাতিমান স্পেনীয় পরাবাস্তববাদী চিত্রকর। ‘দ্য পেরসিসটেন্স অব মেমোরি’ (১৯৩১) ছাড়াও তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্মের মাধ্যমে চিত্রকলায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। জ্যাকসন পোলাক (১৯১২-১৯৫৬) বিমূর্ত ছবির জগতে সে বেশ বিখ্যাত নাম তাঁর শিল্পকর্ম ‘নাম্বার ১৭’। এ্যাডভার্ড মাঞ্চর ‘দ্য স্ক্রিম’ জোহানস ভারমিয়ার ‘গার্ল উইথ এ্যা পার্ল ইয়ারিং’। পাবলো পিকাসোর ‘দ্য ড্রিম (১৯৩২)’। বিশ^খ্যাত এই চিত্রকরদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে চিত্রকলা আজ আধুনিকতার শীর্ষে পৌছে গেছে। কয়জন ডাচ চিত্রশিল্পী: ইয়ান ভন আইক, রোখইয়ের ভন দ্যর ঔদেন ও হিউগো ভন দ্যর খুস (১৪৭৫) ইতালিতে উন্নত তেল চিত্রের কলাকৌশল ব্যবহারের যে সূচনা করেন যা শেষ পর্যন্ত বিশ^ব্যাপী চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। এডগার দেগাস, ফ্রান্স; রেমব্রান্ট, নেদারল্যান্ডস; হেনরি মাটসি; ক্লদ মনেট, ফ্রন্স চিত্রকলায় আধুনিকায়নে ভূমিকা পালন করেন। বাংলা/ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রকলার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা কঠিন। তবে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় যে বাংলার প্রাচীন চিত্রকলা নিদর্শন পাল আমলের (৭৫০-১১৬২ বাংলা) বিষয় ছিল লতাপাতা/বৃক্ষ। এর পর মধ্যযুগে দেবদেবীকে উপলক্ষ করে চিত্র অঙ্কন করা হয়। তারপর ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশিক অর্থনীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে স্থানীয় শিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এদেশে ‘আট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে বাংলা/ ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রকলায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়। চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন (১৯১৪-১৯৭৬) বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত বাঙালি চিত্রকর যিনি দুর্ভিক্ষ বিষয় নিয়ে ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলো হলো ‘দুর্ভিক্ষ চিত্রমালা (১৯৪৩)’, ‘সংগ্রাম (১৯৫৯)’, ‘সাওতাল রমণী’, ‘ঝড়’, ‘কাক’ তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘নবান্ন (১৯৭০)’, ‘মনপুরা ৭০’। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এস এম সুলতান গ্রামীণ মানুষের জীবনের দ্রোহ-প্রতিবাদ, বিপ্লব-সংগ্রাম এবং বিভিন্ন পরিস্থিতে টিকে থাকার ইতিহাস তাঁর চিত্রশিল্পের প্রতিপাধ্য। তাঁর শিল্পকর্ম ‘হত্যাযজ্ঞ (১৯৮৭)’, ‘চরদখল (১৯৮৮)’। কাফিল আহামেদ, সফিউদ্দিন আহামেদ, শাহাবুদ্দিন আহামেদ, নভেরা আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া, নিতুন কুন্ড, হাসেম খান ও কাইয়ুম চৌধুরীর মতো বিদগ্ধজনেরা বাংলাদেশের চিত্রশিল্পকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
ঢাকা, বাংলাদেশ রোববার ২৫ মে ২০২৫, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২