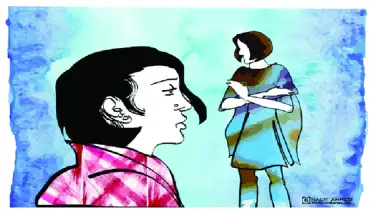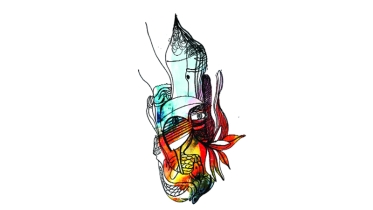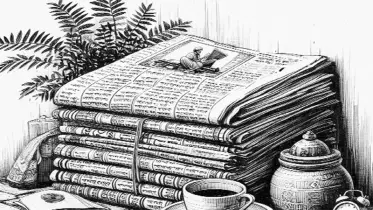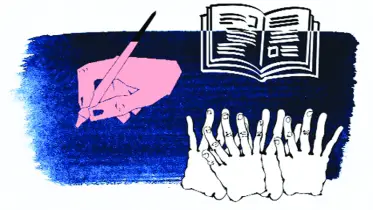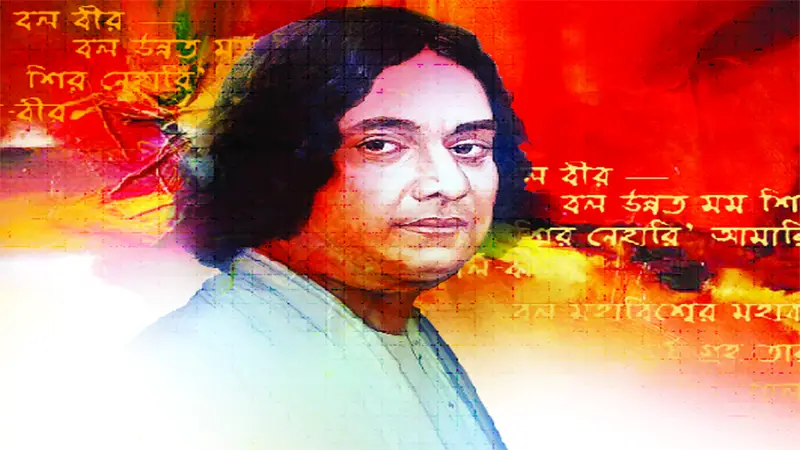
বাংলা ১৩২৮ সালের ২২ পৌষ সংখ্যায় ‘সাপ্তাহিক বিজলী’ পত্রিকাতে কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন কবিতাটিকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশে সাড়া পড়ে যায়। অবশ্য কবিতাটি তখনকার জনপ্রিয় মাসিক ‘মোসলেম ভারত’ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে ‘বিজলী’র সম্পাদক পাঠকদেরকে অবহিত করেছিলেন, যদিও ‘বিজলী’র মাধ্যমেই পাঠকবর্গ এ মূল্যবান কবিতাটির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন।
এ সম্পর্কে একটি সরস তথ্য রয়েছে।
১৩২৮ সালের পৌষ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই কবিতাটি লিখে কবি পাঠান ‘মোসলেম ভারত’-এর কার্তিক সংখ্যাতে ছাপার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ‘মোসলেম ভারত’ প্রকাশে বিলম্ব হতে থাকে। এ সময় কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রী নলিনীকান্ত সরকার ছিলেন ‘বিজলী’র সম্পাদক। তার পক্ষ থেকে শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কবির কাছে এসে অনুরোধ করলেন ‘বিজলী’র জন্য একটা ভালো কবিতা লিখে দেওয়ার জন্য। ঘটনাক্রমে কবির ‘বিদ্রোহী’ কবিতার পাণ্ডুলিপি তার নজরে পড়লো। কবিতাটি পড়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। কবির কাছে অনুরোধ জানালেন উক্ত কবিতাটির জন্য। নজরুল তাকে বললেন, কবিতাটি ইতোমধ্যেই ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকাতে পাঠানো হয়ে গেছে। কিন্তু ভট্টাচার্য মশাই নাছোড়। কবিতাটি তার চাই-ই। কবি পড়লেন উভয় সংকটে। অবশেণে সমাধান করে দিলেন ভট্টাচার্য মশাই নিজেই। ঠিক হল, ‘বিজলী’ পত্রিকাতে ছাপা হবে কবিতাটি। তবে তার পাদটীকায় লেখা থাকবে যে, ‘মাসলেম ভারত’ থেকেই এটি গৃহীত হয়েছে। নিরুপায় হয়ে কবি তাতেই রাজি হলেন।
কবিতাটি এত বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, সেই সংখ্যা ‘বিজলী’ দু’বার করে ছাপতে হয়েছিল এবং এরপর ‘প্রবাসী’সহ কয়েকটি পত্রিকাতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, পত্রিকাগুলো বিপুলভাবে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিল।
এ কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর গোটা বাংলায় নজরুলের পরিচিতি আর সুনাম বেড়ে যায় শত গুণে। দেশের সর্বশ্রেণির জনসাধারণের মুখে ধন্য ধন্য হয়ে ফিরতে লাগলো তার খ্যাতি। এমনকি তাকে ছাড়া কোনো জলসার কল্পনাই করা যেত না। ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটির জনপ্রিয়তার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, এর বক্তব্য বা আবেদন। কবিতাটি এমন এক সমকালীন পরিবেশে রচিত, যখন দেশের আপামর জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল বিদেশি অত্যাচারী শাসকের অশুভ আর নির্মম শাসন-নিগড় থেকে মুক্তিলাভের জন্য। ঠিক এমনি একটি বলিষ্ঠ, তেজদীপ্ত আর জ্বালাময়ী শপথের আশাই যেন সেদিন করেছিল এ দেশের নিপীড়িত মানুষ।
দ্বিতীয়ত, এ কবিতাটির মধ্যে রয়েছে নজরুল-চরিত্রের বিশেষ ছাপ। এর একস্থানে নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি বলেছেন- ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হতে রণ-তূর্য্য’। অর্থাৎ কোমলতা আর কঠোরতা সমন্বয়ে যে তার জীবন, এ কথা নজরুল স্বমুখে স্বীকার করেছেন এ কবিতাতেই। বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি বলেছেন-
‘আমি চির দুর্দম, দুর্বীনিত নৃশংস,
মহাপ্রলয় আমি নটরাজ,
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথিবীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি মানি নাকো কোনো আইন,
আমি ভরাতরী করি ভরাডুবি
আমি টর্নেডো আমি ভিম ভাসমান মাইন!’
এতবড় উচ্ছেৃঙ্খল কঠোর কবি আবার ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন একটুখানি কোমলতার পরশ নিয়ে ধন্য হওয়ার জন্য। তাই তিনি বলেন-
‘আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী তন্বী নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম উদ্যম আমি ধন্যি।’
শুধু কুমারীর বন্ধনহারা বেণী আর তার হৃদয়ের উদ্যম প্রেমরূপে বিকশিত হয়েই কবি সন্তুষ্ট নন। একটু আগে নিজকে নটরাজ, টর্নেডো আর মাইন বলে গর্ব করেছিলেন, মুহূর্তকাল মধ্যেই সেই কবি আবার হয়ে পড়লেন-
‘টির শিশু চির কিশোর
যৌবন ভীতু পল্লীবালার জীবন আচর কাঁচলি নিচোর।’
তৃতীয়ত, বিদ্রোহী কবিতাটির মধ্যে কোনোরকম ধর্মীয় গোঁড়ামিকে কবি প্রশ্রয় দেননি। খোদা, ভগবান, ইস্রফিলের সিঙ্গা, কৃষ্ণের বাঁশরি- সকলই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে তার শপথের প্রেরণা হয়ে। অথচ কোনো বিরোধ নেই তাদের মধ্যে। সবাইকে সমানভাবে আসন দিয়েছেন তার হৃদয়ে।
চতুর্থত, কবিতাটির ছন্দ তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অতি মূল্যবান ব্যতিক্রম। এখানে ‘যত নিয়ম-কানন শৃঙ্খল’কে ভেঙে ফেলে কবি প্রবর্তন করলেন এক শ্রুতিমধুর নতুনমাত্রার ছন্দ্রের। এ প্রসঙ্গে কবি আবদুল কাদের বলেন- ‘বিদ্রোহী সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। বাংলা ভাষায় তিনি এই ছন্দের প্রবর্তক।’
কিন্তু পরিতাপের কথা, নজরুলের এ অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক জনপ্রিয়তা সহ্য হলো না অনেকেরই। তাই মুগ্ধচিত্তে বিশ^কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করেছিলেন পবিত্রচিত্তে, সেই নজরুলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কলম ধরেছিলেন এ দেশেরই কয়েকজন কবি।
‘বিদ্রোহী’র একস্থানে কবি বলেছেন- ‘আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ’। বিকৃত ব্যখ্যা করা হল এ ছত্রটিরও। অভিযোগ করা হল, কবি নিজকে খোদার চেয়েও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী।
বলাবাহুল্য, এখানেও ‘কাহারে’ অর্থে কবি সেই নকল ভগবানকেই বুঝিয়েছেন। এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি তার যে পরম আস্থা ছিল, তার স্বাক্ষর রয়েছে তৎকালীন ‘জেহাদ’ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লেখা একটিচিঠিতে। চিঠির একস্থানে তিনি লিখেছিলেন- ‘আমার মন্ত্র, ইয়াকানাবুদু ওয়া ইয়াকানাস্তাইন। কেবল আল্লাহর আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব আমি স্বীকার করি না।’
‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি পড়ে যে সব গোঁড়া মুসলমান কবিকে ‘কাফের’ বলে গালি দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশে দুঃখ করে কবি বলেন- ‘আমার ‘বিদ্রোহী’ পড়ে যারা আমার উপরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন. তারা যে হাফিজ, রুমীকে শ্রদ্ধা করেন- এও আমার মনে হয় না। আমি তো আমার চেয়ে বেশি বিদ্রোহী মনে করি তাদের। এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম মুখে নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে?’
‘বিদ্রোহী’ কবিতার মধ্যে ‘আমি’ শব্দের প্রয়োগ অসংখ্যবার।
এক শ্রেণির গোঁড়া মুসলমানগণ কবির এ ‘আমিত্ব’কে স্বীয় শক্তির অহঙ্কার বলে দোষারোপ করেন। কিন্তু তারা জনেন না যে, মায়াক্ভস্কির ‘আমিত্ব’ যেমন ছিল গণতন্ত্রী আমেরিকার আত্মঘোষণা, তেমনি নজরুলের ‘আমিত্ব’ ছিল এ দেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি-কণ্ঠ।
‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রকাশের পর ‘বিদ্রোহী কবি’ বলে কবির একটি খ্যাতি রটে যায়। আর এক শ্রেণির লোক তা ‘সুখ্যাতি’র বদলে ‘কুখ্যতি’ হিসেবেই প্রচার করেছিল বেশি। তাকে ‘বিদ্রোহী’ আখ্যা দিয়ে অনেকে গালি দিতে থাকে, ভয় ধরিয়ে দিতে থাকে সাধারণ লোকের মনে।
বিদ্রোহ তিনি করেছিলেন ঠিকই। নিজরে জবানিতে কবি নিজেইতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সে বিদ্রোহের স্বরূপ ছিল সমালোকদের দেওয়া স্বরূপ থেকে স্বতন্ত্র। তা বর্ণনা করতে যেয়ে কবি স্বীকার করেন-
‘আমি বিদ্রোহ করেছি- বিদ্রোহের গান গেয়েছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে- যা মিথ্যা, কলুষিত পুরাতন পচা সেই মিথ্যা- সনাতনের বিরুদ্ধে- ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।- এর প্রয়োজন ছিল মনে করেই।’
কথাটিতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। তখন এমন বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল ঠিকই এবং তা অনেক বেশিও। সব রকম ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ এবং সমালোচনাকে উপেক্ষা করে ‘জাহান্নামের আগুনে বসে’ এমনি ‘পুষ্পের হাসি’ হাসতে পেরেছিলেন বলেই এ দেশের কোটি নিপীড়িত মানুষকে দুর্বার শক্তি নিয়ে অনেকখানি উজ্জীবিত করতে তিনি সহায়ক হয়েছিলেন।
এ প্রসঙ্গে নজরুল-জীবনীকার আজাহারউদ্দীন খান যথার্থই বলেছেন- ‘ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে জগতজুড়ে যে লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছিল, সেই হাওয়া ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মারফত বাংলা সাহিত্যে প্রথম এনেছিলেন নজরুল।’
প্যানেল