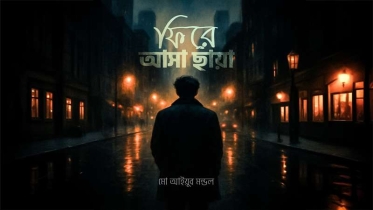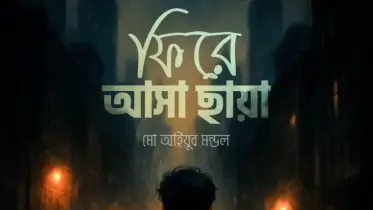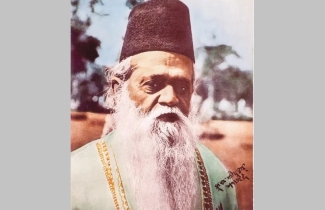আমরা বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষায়ই আমরা কথা বলি, আমাদের মনের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করি। মাতৃভাষা প্রত্যেক জাতির কাছেই অতি আদরের। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের সূর্যসন্তানরা প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ। আর সে রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রিয় স্বাধীনতা, পেয়েছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তাই বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালী জাতিসত্তার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি, লড়াই করেছি তার উন্নতি ও প্রসার ঘটানো আমাদের কর্তব্য। কিন্তু দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি মাস এলেই যেন বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দরদ বেড়ে যায়। লেখকদের লেখার মৌসুমও যেন এই ফেব্রুয়ারি মাস। বাংলা ভাষার উন্নতি বিধান করতে হলে এ ভাষার উৎস ও উপাদান জেনে তাকে আরও কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষও বাংলা ভাষার বানান সম্পর্কে একবারেই উদাসীন। পরীক্ষার খাতায় ছাত্রছাত্রীরা যে বানান লেখে এবং যেভাবে বাক্য গঠন করে তা দেখে লজ্জা পেতে হয়। ইংরেজরা নাকি তাঁদের মাতৃভাষায় কোন কিছু লিখতে গিয়ে সামান্যতম ভুলও করেন তাহলে লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে যায়। আমাদের অনেক শিক্ষক মহোদয়ও বলে থাকেন, এখন বানান নিয়ে অত চিন্তা-ভাবনার দরকার কী! আমাদের বানান সংস্কারেরা আবার প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত ও শুদ্ধ বানানটিকে পরিবর্তন করে দিয়ে ভাষার মধ্যে একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছেন।
আমরা বাঙালীরা যে ভাষায় কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি তাকে বলা হয় বাংলা ভাষা। বাংলা শব্দটি এসছে বঙ্গ শব্দ থেকে। বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী (বাঙালী/বাঙালি) প্রভৃতি শব্দ বঙ্গ শব্দেরই রকমফের।
১। এখন লিখন-কাজে এবং ভদ্রসমাজে মুখের ভাষায় আমরা যে শিষ্ট বাংলা ব্যবহার করি তার অধিকাংশই নদীয়া-চব্বিশ পরগণা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথ্য ভাষার পরিশীলিত রূপ। বাংলাদেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আঞ্চলিক বা উপভাষার সঙ্গে তার বিস্তর পার্থক্য। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভাষার দুটি রূপ চলে আসছে- একটি শিষ্ট বা প্রমিত রূপ, অন্যটি অশিষ্ট বা প্রাকৃত রূপ। বাংলা ভাষার শিষ্ট রূপকে আমরা প্রমিত বাংলা এবং অশিষ্ট রূপকে আঞ্চলিক বা উপ-ভাষা বলি। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাকৃত বা সাধারণ জন দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে শিষ্ট বা প্রমিত বাংলার অনেক পার্থক্য। ঐ সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা আমরা লিখন-বাংলায় খুব কমই ব্যবহার করি। এমনকি ভদ্রসমাজে মুখের ভাষায়ও তা ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করি। এক অঞ্চলের কথ্য ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষেরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারেন না। এসব ভাষা আমাদের উন্নত ভাব প্রকাশেও ততটা সহায়ক হয় না। বস্তুত আমরা শিষ্ট বা প্রমিত বাংলাকে লিখন-কাজে এবং ভদ্রসমাজে মুখের ভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি। বাংলা ভাষার পরিধি এখন অনেক ব্যাপক। বর্তমানে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং তার বাইরে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছেÑ একটি সাধু ভাষা, অন্যটি চলিত ভাষা। সাধু ভাষা সংস্কৃত বা তৎসম শব্দবহুল। চলিত ভাষা তদ্ভব এবং দেশী-বিদেশী শব্দবহুল।
প্রমিত বা লেখ্য বাংলার আবার দুটি রূপ- সাধু ও চলিত। সাধু ভাষা অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদে আড়ষ্ট। এর ক্রিয়াপদ দীর্ঘ। অপরপক্ষে, চলিত ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ। এর ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গদ্যরীতি সাধু ভাষায় গড়ে উঠেছে। কারণ বাংলা গদ্য সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে সংস্কৃতজ্ঞ প-িতেরা সাহিত্য সৃষ্টির দায়িত্বে ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাগর প্রভৃতি প-িতদের হাতে সাধু রীতিতে বাংলা গদ্যের সূত্রপাত। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এর বিকাশ। বর্তমানে সাধুরীতির চল ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে; সব ক্ষেত্রে চলিত রীতি তার স্থান দখল করে নিচ্ছে। কারণ চলিত ভাষা অনেকটা সহজ-সরল ও আড়ষ্টতাহীন। শিষ্ট মুখের ভাষা বলে এই ভাষা এখন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয়। তবে উচ্চতর ভাব প্রকাশে, দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সাধু ভাষার রয়েছে অসাধারণ ক্ষমতা। এখানে কিছু সাধু ভাষার উদাহরণ তুলে ধরা হলো।
১। সে চলিতেছিল দুর্গম কাঁটাভরা পথ দিয়া। পথ চলিতে চলিতে সে একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখির অনিমিখ দৃষ্টি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টিতে আশা-উন্মাদনার যে ভাস্বর জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল, তাহাই ঐ দরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতাভরা গৌরবে ভরপুর করিয়া দিল। সে প্রাণভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল- ‘হ্যাঁ ভাই! তোমাদের এমন শক্তিভরা দৃষ্টি পেলে কোথায়?’ অযুত আঁখির নিযুত দীপ্ত চাউনি বলিয়া উঠিল- ‘ওগো সহসী পথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই ওই চলার পথ চেয়ে।’ উহারই মধ্যে এক-রেখা ম্লানিমার মতো সে কাহার স্নেহ-করুণ চাহনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল- ‘হায়, এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু অনিবার্য!’ অমনি লক্ষ কণ্ঠে লক্ষ হুঙ্কার গর্জন করিয়া উঠিল- ‘চোপরাও ভীরু, এইতো মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ।’ একলা পথিক দু’চোখ পুরিয়া এই কল্যাণ-দৃষ্টির শক্তি-অমিয় পান করিয়া লইল। তাহার সুপ্ত যতকিছু অন্তরের সত্য, এক অঙ্গুলি-পরশে সারা বীণায় ঝঞ্ঝার মতো সাগ্রহ সাড়া দিয়া উঠিল- ‘আগে চল!’ বনের সবুজ তাহার অবুঝ তারুণ্য দিয়া পথিকের প্রাণ ভরিয়া দিয়া বলিলÑ ‘এই তোমার যৌবনের রাজটীকা পরিয়ে দিলাম; তুমি চির-যৌবনময় চির-অমর হলে!’ পথের আকাশ অবনত হইয়া শির চুম্বন করিয়া গেল। দূরের দিগ¦লয় তাহাকে মুক্তির সীমারেখার আবছায়া দেখাইতে লাগিল। (কাজী নজরুল ইসলাম, দুরন্ত পথিক)।
২। বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাইÑ যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘœ, শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অচল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; আলোক-পিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কল-কোলহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে; জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার, বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। (কাজী নজরুল ইসলাম, যৌবনের গান)
৩। বিস্তীর্ণ নির্জন বালুতটে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিন ধীরে ধীরে অবসান হইয়া গেল। মহেন্দ্র চক্ষু অর্ধেক মুদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখুর-ধুলিজালের মধ্যে বৃন্দাবনের ধেনুদের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের হাম্বারব শুনিতে পাইল। বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অপরিচিত স্থানের অন্ধকার কেবল কৃষ্ণবর্ণের আবরণ মাত্র নহে, তাহা বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া যেটুকু আভা যেটুকু আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অজ্ঞাত অনুচ্চারিত ভায়ায় কথা কহে। পরপারবর্তী বালুকার অস্ফুট পা-ুরতা, নিস্তরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ণ কালিমা, বাগানে ঘনপল্লব বিপুল নিম্ববৃক্ষের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা, তরুহীন ম্লান ধূসর তটের বঙ্কিম রেখা, সমস্ত সেই আষাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকারে বিবিধ অনির্দিষ্ট অপরিস্ফুট আকারে মিলিত হইয়া মহেন্দ্রকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চোখের বালি)।
লেখ্য ভাষার চলিত রূপের মধ্যেও তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তি কত প্রবল তার কিছু উদাহরণ।
১। নিয়তির স্বভাব অতি তরল। সুখের বিধান নিয়ে, মানুষের সংসারে প্রথম তিনি আসেন। তাপপরে তিনি আনেন অকস্মাৎ এক নিদারণ দুঃখ। তরল বিদ্যুতের এ যেন,
প্রথমে আলোর ঝলকান্,
অবসানে বজ্রের পলক-প্রলয়।
কাল-! অনন্ত নাগের মতো। অনন্ত নাগের ফণার দোলায় যেমন ছোট বড় সব পাহাড়ই টলে যায়, তেমনি মহাপুরুষরাও টলেন, রক্ষা পান না। সব ধসে পড়ে, যখন মহাকাল ছোট-বড় বিচার না করে স্পর্শ করে যান সকলের কেশ।
২। একদা তখন রাত্রির চতুর্থ যাম্। বাতাস বইছে ভোরের, স্বপ্ন দেখলেন হর্ষদেব।
দেখলেন- অরণ্যজুড়ে দুর্নিবার দাবানল উঠেছে জ্বলে, আর সেই চটুল শিখা হলুদ-বরণ আগুনে পুড়ে মরছে প্রকা- এক কেশর-ফোলা সিংহ। সিংহিনী শাবকদের ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে পড়ছে সেই দাবদহনের মধ্যে। স্বপ্নের মধ্যেই হর্ষদেব শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে-
‘জগতের বন্ধন নিশ্চয় লোহার চেয়েও কঠিন, তা না হলে তির্যগযোনির জীবেরা বা এমন ব্যবহার করবে কেন?’ হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল হর্ষের। হঠাৎ কেন বারংবার নেচে ওঠে তাঁর বাম নয়নের পল্লব? কেঁপে ওঠে গা, অঞ্চিত হয় রোম?’ (প্রবোধেন্দু ঠাকুর কর্তৃক হর্ষচরিতের বঙ্গানুবাদ)।
চলিত বাংলা ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মার্জিত কথ্য রূপ। তবে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা থেকে তা অনেকটা ভিন্ন। চলিত বাংলা ভাষায় তদ্ভব শব্দের ব্যবহার হয় বেশি। চলিত ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততা।
উদাহরণ-
১। কিসে হয় মর্যাদা? দামী কাপড়ে, গাড়ি-ঘোড়ায়; না ঠাকুরদাদার উপাধিতে? না- মর্যাদা এই সব জিনিসে নাই। আমি দেখতে চাই তোমার ভিতর, তোমার বাহির, তোমার অন্তর। আমি জানতে চাই তুমি চরিত্রবান কিনা। তুমি সত্যের উপাসক কিনা। তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয় কিনা, তোমায় দেখলে দাসদাসী দৌড়ে আসে, প্রজারা তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাত কর। বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ী তোমায় আদর করেন, আমি তোমায় বলবো- যাও।
২। মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলে থাকেন। কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে টাকা না থাকলে তার স্থান কোথাও নেই, সমাজে নেই, স্বজাতির নিকটে, জ্ঞাতি, ভ্রাতা-ভগিনীর নিকটে নেই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে, বলতো জগতে আর এমন কে আছে? টাকা না থাকলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নেই। টাকা না থাকলে কারও নিকটে সম্মান নেই। টাকা না থাকলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তে টাকা, জগতে টাকারই খেলা।
উপভাষা আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতির ভিত্তিতে গঠিত। ৫৫ হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক বহু উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয়, প্রতি ১০ মাইল অন্তর ভাষার পরিবর্তন হয়। এর কারণ উচ্চারণগত পার্থক্য। কয়েকটি আঞ্চলিক বা উপভাষার উদাহরণ-
১। মুই আও করব্যার জইন্যে এ্যাক কামলার গোরোত গেনু। অঁয় মোক সোউগ বুজি দেইল। স্যাটে আরো দুইজন আইছলো। সগাই অবাক হইল্ ওর বুজ্যা দেখি। অঁর বাড়িত হামার দাওয়াত আছিল্। মুরগির বড়বড় আন্ডা দিয়্যা খাওয়াও হইলো। শ্যষে কইল ছার, ত্যামন কিছু খিল্যাবার পারনো না। (রংপুরের উপভাষা)
২। একজন মাইন্সের দুগা হোলা আছিল্। হির্য়া মধ্যে ছুডুগায় হেইতার বাফেরে কইল্ আব্বা আঁর ভাগে মাল্ যিগিন্ হড়ে হিগিন্ আঁরে দেও। আর হেইতেও হেইতার ব্যাকবিত্ত হোলাইনেরে ভাগ করি দিল্। হিয়ার কদিন বাদে ছোড হোলা ব্যাকগিন অত্তর করি লই এক দূর এক দেশে বেড়াইতে গেল; হিয়ানে হেইতে ষ-ামি করি হেইতার ব্যাক বিত্ত উড়াই দিল্। (নোয়াখালির উপভাষা)।
৩। এক জনের দুই পুৎ আছিল। তার ছুডু পুতে বাপেরে কইলো, বাজি, মাল-ব্যাসাতের যে বখরা আমি পাইবাম্ তা আমারে দেউখাইন। হে তারারে মালপাতি বাট কৈরা দিল্। থুরা দিন বাদে ছোট্কা তার হগ্গল মাল-ব্যাসাৎ থুবাইয়া দূর মুল্লুকে গেল্। হেইখানে ফৈলামী কৈরা হগ্গল খোয়াইল্।
প্রমিত বাংলার অধিকাংশ শব্দ বৈদিক-সংস্কৃতের অবদান। আমরা যখন কোন কিছু সাধু ভাষায় লিখি তখন তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সংখ্যা আসে প্রায় ৫৫% থেকে ৫৫% ভাগ। আর যখন চলতি ভাষায় লিখি তখন তদ্ভব (সংস্কৃত থেকে উদ্ভব) শব্দের সংখ্যা আসে ৬০% থেকে ৬৫% ভাগ। অন্যান্য শব্দ (আরবী, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি) মিলে। বাংলা ভাষায় কোন্ শব্দের প্রভাব কতটুকু তার একটি হিসেব ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দিয়েছেন তাঁর Origin and Development of Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে। হারটি এরূপ- তৎসম ৪৪%, তদ্ভব ও দেশী ৫১.৪৫%, বিদেশী ৪.৫৫%। তবে আঞ্চলিক বাংলার বা উপভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অনার্য শব্দ (কোল, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মু-া প্রভৃতি) বিদ্যমান। তার অনেকগুলো আবার সংস্কৃতায়ন হয়ে আর্যভাষার রূপ নিয়েছে। যেমন, কদলী, কার্পাস, তাম্বুল, নীর, ফল, লাঙ্গল, গুবাক, নারকেল, সর্ষপ প্রভৃতি শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে সংস্কৃতে স্থান পেয়েছে। আবার ময়ূর, খল, বিল, কু-, দ-, অলস, অর্ক, প-িত, শব, অণু, অরণি, কপি, কলা, কাল, গণ, নীল, পুষ্প, পূজা, ফল, বীজ, রাত্রি প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত। যেগুলো সংস্কৃতায়ন হয়নি সেগুলোকে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে অপ-ভাষা বা দুষ্ট শব্দ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
পূর্বে অধিকাংশ বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে সাধু ভাষায়। কিন্তু এখন কথ্য বা চলিত ভাষায়ই সাহিত্য রচিত হচ্ছে। তাই ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা কমে আসছে। বাড়ছে তদ্ভব বা খাঁটি বাংলার ব্যবহার। বিশ্বায়নের এ যুগে এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও বহুজাতিক কোম্পানীর বদৌলতে বাংলা ভাষায় এখন প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি শব্দ ঢুকে পড়ছে। তবুও প্রমিত বাংলার অধিকাংশ শব্দই যে বৈদিক-সংস্কৃতের অবদান তা অস্বীকার করা যাবে না। তবে আঞ্চলিক বাংলার বা উপভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাগার্য শব্দ (কোল, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মুণ্ডা প্রভৃতি) বিদ্যমান। সেগুলোই বর্তমানে আমাদের আঞ্চলিক বা উপভাষার শব্দাবলী। এসব শব্দ সাধারণত আমরা লিখন কাজে এবং শিক্ষিত ভদ্র সমাজে মুখের ভাষায় ব্যবহার করি না। কারণ উচ্চতর ভাব প্রকাশে তা ততটা সহায়ক নয়। চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর গ্রাম্য ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বুঝতে পারেন না। আবার সিলেট, রংপুর, বরিশাল, রাজশাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষদের বুঝতে কষ্ট হয়। তাই লেখার কাজে এবং ভদ্র সমাজে মুখের ভাষায় আমরা সর্বজন স্বীকৃত একটি স্ট্যান্ডার্ড ভাষা ব্যবহার করি, যাকে প্রমিত বাংলা বলা হয়। আর এই প্রমিত বাংলা বৈদিক-সংস্কৃতেরই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ।
অনেকে এখন আঞ্চলিক বা উপভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সাহিত্যে তার ব্যবহারও কম-বেশি দেখা যায়। কিন্তু উচ্চতর ভাব প্রকাশে উপভাষার প্রকাশ ক্ষমতা অনেক কম। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের প্রকাশ ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,
“সংস্কৃত ভাষা বিগত তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতবর্ষের চিন্তা ও সভ্যতার সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া আছে। প্রায় সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া, পুষ্টি লাভ করিয়াছে। নূতন যুগের নূতন ভাব, নূতন চিন্তাধারা, নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতির কথা- এসব বিষয়ে কিছু বলিতে হইলেই, যেখানে পূর্ণ ভাবদ্যোতক শব্দের আবশ্যকতা ঘটে, ভাষায় প্রচলিত প্রাকৃত-জ শব্দের সাহায্যে সেই আবশ্যকতা পূর্ণ করা সহজসাধ্য হয় না, প্রাকৃত-জ শব্দগুলি নূতন ভাব প্রকাশের উপযোগী হয় না; এবং বিদেশী শব্দও বহু স্থলে ব্যবহার করিতে কেহ চাহে না। এ জন্য, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মূল-স্থানীয় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতের অক্ষয় ও অনন্তভা-ার, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী (হিন্দী), পাঞ্জাবী, মারহাট্টী, গুজরাটী এবং তেলুগু, কানাড়ী, তামিল, মালয়ালম্ প্রভৃতি আর্য ও অনার্য ভারতীয় ভাষাসমূহের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেশের লোকের মনে যতই নূতন ভাব-সম্পদ আসিতেছে, ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তা ততই বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে। ... এবং এই ভাষার শব্দ দ্বারা মানুষের মনের তাবৎ চিন্তা অতি সুচারুরূপে প্রকাশিত হইতে পারে; এই হেতু কালোপযোগী ভাবসমূহের প্রকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক বলিয়া, সকলেই সংস্কৃত শব্দাবলীর আবশ্যকতা এবং অপরিহার্যতা স্বীকার করেন।”
বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত পরিভাষা কোষের প্রতি দৃষ্টি দিলে সে সত্যতা ধরা পড়ে। উক্ত পরিভাষা কোষের প্রায় সবই নেয়া হয়েছে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ থেকে। তাই আমাদের সংকীর্ণতা পরিহার করে প্রমিত দেশী, বিদেশী শব্দকে আত্মসাত করে তৎসম বা সংস্কৃতের ঋণ স্বীকার করে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য কাজ করে যেতে হবে।
কেবল ফেব্রুয়ারী এলেই বাংলা ভাষার প্রতি দরদ দেখালে চলবে না। ভাষার শুদ্ধতা ও সৌকর্ষের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বাংলা ভাষার বিকৃতি রোধ করতে হবে। অহেতুক ভাষার বানান পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।
ঢাকা, বাংলাদেশ বুধবার ১৬ জুলাই ২০২৫, ১ শ্রাবণ ১৪৩২