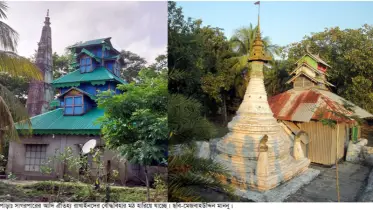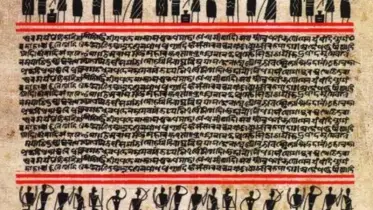ছবি: সংগৃহীত
একটি লাল বাক্স! একটি হলুদ খাম! একটি চিঠি! অনেক খানি অপেক্ষা! একটি হাক- 'চিঠি আছে'/ 'চিঠি নেন'! এর সবই একেকটি অনুভূতির নাম, একেকটি আবেগের নাম এবং একটি সময়ের প্রতিনিধি যেন!
হ্যাঁ, ডাক বিভাগের কার্যক্রমের কথাই বলছি। একটি সময় ছিল যখন যানবাহন ব্যবস্থা ভালো ছিল না, ছিল না মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেটের ব্যবহার। টেলিফোন ব্যবস্থা হয়তো ছিল, তবে সেটা ছিল অপ্রতুল, হয়তো জেলা সদর পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ উপজেলা সদর পর্যন্ত। গ্রামগুলোতে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠানো চিঠি গুলো।
প্রাচীনকাল থেকেই চিঠি চালাচালির রেওয়াজ ছিল, বিশেষ করে রাজারা অন্য রাজার সাথে বা অন্য কারও সাথে যোগাযোগের জন্য চিঠি লিখতো, তবে সেগুলো পাঠাতে হতো লোক মারফত। আরেকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রযুক্তি (!) ছিল- কবুতর মারফত চিঠি প্রেরণ! ভারতীয় উপমহাদেশে শের শাহ সুরি আমলে চালু হয় প্রথম ডাক ব্যবস্থা। ঐতিহাসিকদের মতে, সম্রাট শের শাহ সুরি দিল্লির মসনদে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দ্রুত যোগাযোগের জন্য প্রায় ১৭০০ ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৪০০ ঘোড়সওয়ারী বার্তাবাহক নিয়োগ করেন। এটি 'ঘোড়ার ডাক' বলে সুপরিচিত। এই ডাক ব্যবস্থায় কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় চিঠি আদান প্রদান করা হতো।
এরপরে ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৭৬৬ সালে কাঠামোবদ্ধ ডাক ব্যবস্থা শুরু হয়। ১৮৫৪ সালে চালু হয় সাধারণ জনসাধারণের জন্য ডাক ব্যবস্থা। ডাক টিকিটের ব্যবহারও শুরু হয় তখনই। পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে ডাক ব্যবস্থা চলত। এটি নিয়ন্ত্রিত হতো করাচি থেকে।
স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে ডাক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হয়। ডাক বিভাগকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশির দশকে গ্রাম পর্যায়ে ডাক বিভাগের সেবা বিস্তৃত হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি বেসরকারি কুরিয়ার চালু হয়। এতে ধীরে ধীরে একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার ডাক বিভাগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তবে ২০১০ এর আগ পর্যন্ত ডাক বিভাগের মোটামুটি জৌলুস ছিল।
ডাক বিভাগ লোকসানে পড়ে গেলে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন সেবা ডাক বিভাগের মাধ্যমে চালু করে একে লাভজনক খাতে উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে প্রায় ১০০০০ ডাকঘর নিয়ে সেবা চালিয়ে যাচ্ছে ডাক বিভাগ। তারপরেও এটি একটি লোকসান খাত।
অতীতের সেই চিঠির জায়গা বর্তমানে প্রায় সবটুকুই দখল করে নিয়েছে যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন রূপ- ই-মেইল, মোবাইল ফোন, টেলিফোন ইত্যাদি। এক সময় চিঠি লেখা হতো আয়োজন করে, চিঠি এলে তা পড়াও হতো আয়োজন করে। গ্রামে বসবাসকারী বৃদ্ধ মা রাস্তার পানে চেয়ে থাকতেন কখন পোস্ট অফিসের পিয়ন আসবে আর হাক ছাড়বে- 'চিঠি আছে'/ 'চিঠি নেন'। পড়তে না জানা ওই মা সন্তানের কাছ থেকে আসা চিঠিটি নেড়েচেড়ে হাতে দিতেন পড়া জানা তার কোন নাতি-নাতনিকে বা কোন প্রতিবেশীকে, পড়ে শোনানোর জন্য। উত্তর লেখাও কম ঝক্কির ছিল না। মা বলতেন, সেই কথাগুলো লিখে দিত ওই পড়ালেখা জানা কেউ! তারপরে পোস্ট অফিসের লাল বাক্সে ফেলে দিয়ে আবার অপেক্ষা!
মায়ের জন্য সন্তান হয়তো ডাক বিভাগের মাধ্যমে 'মানি অর্ডার' করে কিছু টাকা পাঠিয়েছে। তবে মায়ের আকর্ষণ টাকাতে নয়, বরং 'মানি অর্ডার' ফর্মের নিচের ছোট্ট চিঠিতে!
কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও ছিল। কোন আত্মীয় হয়তো বেড়াতে আসবেন বলে চিঠি লিখেছেন, তিনি আসার পরে হয়তো চিঠিটা প্রাপকের কাছে পৌঁছেছে! অনেক ক্ষেত্রে এটি বিব্রতকর অভিজ্ঞতা হতো, তবে এর আনন্দ ও কম ছিল না!
ডাক বিভাগের স্বর্ণযুগে যখন টেলিভিশন বা অন্য কোন ডিজিটাল মাধ্যম ছিলনা, তখন দেশ-বিদেশের খবর জানার একমাত্র উপায় ছিল সংবাদপত্র। সেই সংবাদপত্র গ্রামগঞ্জে বই নিয়ে আসতো ডাক বিভাগের কর্মীরা!
বিশ্ব আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই মুহূর্তে দ্রুত এবং সহজ যোগাযোগের বিষয়টি সময়ের দাবি হওয়ার কারণে, সঙ্গতভাবেই ডাকবিভাগ উপেক্ষিত হচ্ছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সচেতনতা এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখতে পারে। কয়েকদিন আগে পাবনা থেকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম ঢাকাতে। ওই চিঠিটি বেসরকারি কুরিয়ারে পাঠানোর জন্য আনুমানিক ৫০ টাকার মত লাগতো। আমি ওই চিঠিটি ডাক বিভাগের 'রেজিস্টার্ড পোস্টাল সার্ভিস' এর মাধ্যমে ৮/১০ টাকায় পাঠিয়ে দিয়েছি! পণ্য ও কাগজপত্র পাঠানোর জন্য এবং আর্থিক লেনদেনে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সেবা এখনো প্রচলিত যে কোন বেসরকারি সেবার চেয়ে কম মূল্যে পাওয়া যায়।
আমরা একটু চেষ্টা করলেই এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখতে পারি। না হয় লিখলাম দু-একটি চিঠি প্রিয় মানুষগুলোকে, পাঠালাম লাল বাক্সে ফেলে!
লেখক:
এস এম নাহিদ হাসান,
শিক্ষক, সাংবাদিক ও কবি, ফরিদপুর, পাবনা
সাব্বির