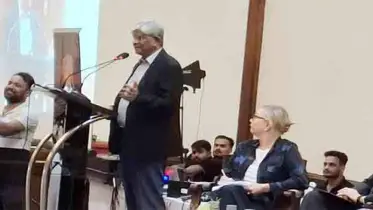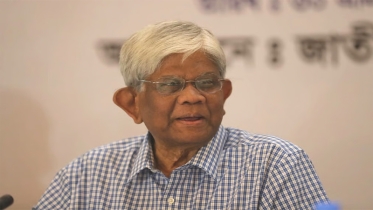অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) অনুমোদনে উল্টো পথে হাঁটছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। দেশের অর্থনীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আইপিও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক হলেও কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বাধীন ৯ বছরে সবচেয়ে কম অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় শেয়ারবাজারের আকারকে ক্রমান্বয়ে ছোট করে তুলছে। দেশের অর্থনীতির সঙ্গে শেয়ারবাজার এগোতে পারছে না বলে সব মহলেই সমালোচনা করা হয়। এই সমস্যা কাটিয়ে তুলতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিবর্তে শেয়ারবাজারকে উৎস করার পরামর্শ বিশ্লেষকদের। কিন্তু গত ৯ বছরে তার বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। বরং উল্টো পথে হেঁটেছে কমিশন। এই সময় শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা বাড়ানোর দরকার পড়লেও কমিয়েছে।
দেখা গেছে, বিএসইসি গঠনের ২৭ বছরে (১৯৯৩) শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে ২৮৫ কোম্পানি। এর মধ্যে কমিশন গঠনের প্রথম ৯ বছরে তালিকাভুক্ত হয়েছে ১০০ কোম্পানি। আর দ্বিতীয় ৯ বছরে তালিকাভুক্ত হয়েছে ৯৪টি। বাকি ৯ বছরে অর্থাৎ খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বাধীন সময়ে তালিকাভুক্ত হয়েছে ৯১টি। অথচ এই সময়ে দেশের অর্থনীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে।
বর্তমান কমিশনের সময়ে নানা আইনী সংস্কার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছিল চ্যালেঞ্জের। নানা আইনী সংস্কারের কারণেই ড. এম খায়রুল হোসেনের সময়ে আইপিও ছেড়ে টাকা উত্তোল কমেছে।
বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে এবং অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু দেশের শেয়ারবাজার সেভাবে এগোচ্ছে না। এই সমস্যা কাটিয়ে তুলতে শেয়ারবাজারের অংশগ্রহণ বাড়ানো দরকার। এক্ষেত্রে বেশি বেশি করে ভাল কোম্পানি শেয়ারবাজারে আনতে হবে।
গত ৯ বছর আগে জিডিপির তুলনায় শেয়ারবাজারের আকার ছিল ৫০.৭০ শতাংশ। যা এখন ১৩.৩৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এর অন্যতম কারণ হিসাবে রয়েছে দেশের অর্থনীতি যে হারে এগোচ্ছে, সে হারে শেয়ারবাজারে কোম্পানি তালিকাভুক্ত হচ্ছে না। এছাড়া ২০১৯ সালে শেয়ারবাজারের মন্দার কারণেও অনুপাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
এদিকে জিডিপিতে শেয়ারবাজার পিছিয়ে পড়ার আরেকটি অন্যতম কারণ হিসেবে রয়েছে আর্থিক খাতের মন্দাবস্থা ও শেয়ারবাজার থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেয়া। একসময় ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানির শেয়ার চাঙ্গা থাকলেও এখন তলানিতে। অথচ শেয়ারবাজারে এই খাতের অংশগ্রহণ বেশি। যাতে চাঙ্গা মুহূর্তে জিডিপির তুলনায় শেয়ারবাজারের অনুপাত বেশি ছিল। কিন্তু ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানির শেয়ারের তলানিতে নেমে আসায় অনুপাতও কমেছে। এছাড়া ২০০৯-১০ সালে ব্যাংকগুলোর শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করার সুযোগ ছিল বেশি। আর সেই সুযোগের থেকেও অনেক ব্যাংক বেশি বিনিয়োগ করে। আর এখন বিনিয়োগের সুযোগ প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগে কমিয়ে আনার পরেও অনেক ব্যাংকের বিনিয়োগ ঘাটতি রয়েছে। ২০১০ সালে ডিএসইর বাজার মূলধন ও জিডিপির অনুপাত ছিল ৫০.৭০ শতাংশ, ২০১১ তে ছিল ৩৩.২০ শতাংশ, ২০১২ সালে ২৬.৩০ শতাংশ, ২০১৩ সালে ২৫.৫০ শতাংশ, ২০১৪ সালে ২৪.১০ শতাংশ, ২০১৫ সালে ২০.৬০ শতাংশ, ২০১৬ সালে ১৯.৭০ শতাংশ, ২০১৭ সালে ২১.৬২ শতাংশ, ২০১৮ সালে ১৭.২১ এবং ২০১৯ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩.৩৯ শতাংশে।
এদিকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের শেয়ারবাজারের মূলধন জিডিপির তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এমনকি পাকিস্তানের থেকেও পিছিয়ে বাংলাদেশ। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনা রয়েছে।
বিএসইসির আরেক সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, শেয়ারবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ একটি বড় বাধা। কিন্তু কোন ডায়নামিক উদ্যোক্তা শেয়ারবাজার থেকে ফান্ড সংগ্রহের জন্য ২ বছর অপেক্ষা করবে না। তাদের জন্য ব্যাংক ঋণ দেয়ার জন্য বসে রয়েছে। এমতাবস্থায় তারা ব্যাংক ঋণ নিয়ে কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই ভাল কোম্পানিকে শেয়ারবাজারে আনার জন্য এই সমস্যার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তার প্রয়োজন।
বাংলাদেশে এখনো পুঁজির উৎস হিসেবে উদ্যোক্তারা শেয়ারবাজারের চেয়ে ব্যাংক ঋণের ওপর বেশি নির্ভরশীল। সামগ্রিকভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা শেয়ারবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের চেয়ে অনেক বেশি। গত কয়েক বছরে শেয়ারবাজারের অবস্থা আগের তুলনায় শক্তিশালী হলেও এখান থেকে মৌলিক খাতে মূলধন স্থানান্তরের প্রবণতা অনেক কম।