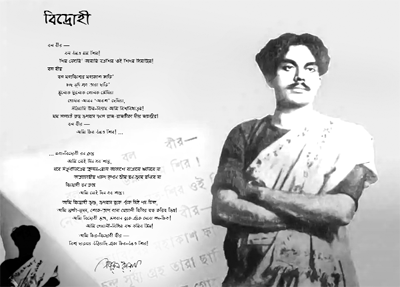
‘বিদ্রোহী’ কবিতা মূলত আত্মজাগরণের কবিতা। মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এমন একটি সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের জয়গান ‘বিদ্রোহী’ কবিতার চরণে চরণে সুস্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান। আত্মমুক্তির মাধ্যমে জগত ও জীবনকে স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করানো যায়। কবিতাটিতে ১২১ বার ‘আমি’ শব্দ ব্যবহার করে কবি একটি কথারই প্রতিধ্বনি করতে চেয়েছেন যে, মানুষ অসম শক্তির অধিকারী। সাধনা ও সংগ্রামে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বপ্নের স্বাধীন দেশ বিনির্মাণ সম্ভব। সাম্য, সত্য, সততা, অসাম্প্রদায়িকতা ও ন্যায়নির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠায় এ কবিতার অবদান বিশ্ববিশ্রুত। ২০২১ সালের ডিসেম্বর ‘বিদ্রোহী’ কবিতার শত বছর পূর্তি। কবিতাটি সৃষ্টির পর থেকে ১০০ বছর সমভাবে জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক থাকাটা রীতিমতো বিস্ময়কর! বাংলা ভাষার কবিতা হিসেবে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বিশ্ব দরবারে কবিতাটির জন্য সাংস্কৃতিক বিবেচনায় গর্ব করতেই পারে।
কবিতার রচনাকাল ও প্রাসঙ্গিকতা
‘বিদ্রোহী’ কবিতা ১৯২১ সালে লিখিত হয়েছিল এ বিষয়ে দ্বিমত না থাকলেও রচনার সময়কাল নিয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। বেশি সংখ্যক সাহিত্য সমালোচক ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনার সময়কাল ১৯২১ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বলে মত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর রচিত ‘কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘শান্তি নিকেতন থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে নজরুল ও মুজফ্ফর আহমেদের ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাড়িতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ঘটনা ঘটে। একটি হলো ভারতের ‘কমিউনিস্ট পার্টি’ গঠন। অপরটি ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনা। তালতলা লেনের এ বাড়িতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুজফ্ফর আহমদ ও তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।’
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং নজরুলের ‘ভাঙ্গার গান’ ও ‘বিদ্রোহী’ রচনা একই বাড়িতে একই সময়ের ঘটনা। কবিতাটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এটি মূলত সাম্যবাদের ওপর রচিত। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও এই কবিতা রচনার সময়কাল একই হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক। মুহম্মদ নুরুল হুদা তাঁর রচিত ‘নজরুলের শিল্প সিদ্ধি ও বিদ্রোহী’ গ্রন্থে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশ পরবর্তী ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন এভাবে, ‘১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি কবিতাটি সাপ্তাহিক ‘বিজলী’ পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। প্রকাশের পরই কবিতাটির পাঠকপ্রিয়তার কারণে পত্রিকাটি পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। দুবারে পত্রিকাটি মোট ২৯০০০ কপি ছাপা হয়, যা তৎকালে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা কবিতাটি পাঠ করেন, অনেকে কণ্ঠস্থ করেন। ঠিক এই সময়ে প্রায় দুই লাখ লোক কবিতাটি পাঠ করেন বলে অনুমিত হয়। পৃথিবীর অন্য কোন কবির অন্য কোন কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর এমন ঘটনা ঘটেছে কি না আমাদের জানা নেই। সে সময় ঘরে ঘরে, হাটে-ঘাটে, মাঠে-তটে, শহরে-বন্দরে, গ্রাম-গঞ্জে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা পঠিত হয়। কবিতায় বিমুগ্ধ ভারতজাতি সংগ্রামমুখর হয়ে ওঠে ও স্বাধীনতার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের পর ভারতবাসী আন্দোলন-সংগ্রামে রাজপথ কাঁপানো কবিতা পেয়েছিল। যেটি আবৃত্তি করে অর্ধচেতন জাতিকে সর্বচেতন করা যায়।’
বিদ্রোহী কবিতা রচনার পটভূমি ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ
১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা পৃথিবী। ভারতীয় উপমহাদেশ তখন ব্রিটিশ শাসনে ও শোষণে ক্ষত-বিক্ষত। কাজী নজরুল ইসলামের বয়স তখন ১৯ বছর সাত মাস। তিনি সেনাবাহিনীর এক তেজোদীপ্ত সৈনিক তখন। কুচকাওয়াজের সঙ্গে শত্রুকে ধ্বংস করার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণে ব্যস্ত। প্রতিটি মানুষই যে বীর যোদ্ধা, অসম-সাহস ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী এ বোধ তখনই সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর। আত্মসচেতন কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল অদম্য সাহস। চিরস্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল, নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত-উপেক্ষিত বঞ্চিত মানুষের ব্যথা বেদনামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। যে কারণে তিনি মানব সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে ওঠেন নিজে নিজেই। অন্তরাত্মার এই অব্যক্ত অভিপ্রায়ই তাঁকে অসাধারণভাবে আন্দোলিত করেছিল। আর তখনই ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মতো এমন কালজয়ী কবিতা সৃষ্টি হয়।
নজরুল কিশোর বয়সেই দেখেন বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) আন্দোলন। অর্থাৎ একটি সংগ্রামী সময়ে তাঁর জন্ম (১৮৯৯) ও শৈশব-কৈশোর এবং যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ ‘বিদ্রোহী’ কবিতার রচনাকাল ছিল সারা পৃথিবীর জন্য অস্থির সময়। তা ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার জন্য তখন ঘরে ঘরে দুর্দমনীয় আন্দোলন চলছে। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য ধর্মমত নির্বিশেষে সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত। এমনি এক মুহূর্তে পরাধীন দেশের সময়ের প্রয়োজনে কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করলেন তাঁর অমর কবিতাখানি, যে কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতি পেল বিদ্রোহের নতুন ভাষা। যুদ্ধ জয়ের নেশায় উন্মত্ত হলো আবালবৃদ্ধবনিতা। আত্মবিশ্বাসের অভাবে যে জাতির চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস ছিল না, যে জাতি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বিনা প্রতিরোধে স্বাধীনতা হারিয়েছিল, সেই জাতি ‘বিদ্রোহী’ কবিতা পড়ে অসীম আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। কবি কণ্ঠের দৃপ্ত উচ্চারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভারতবাসী গেয়ে উঠল-‘আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমারে খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।’
১. স্বাতন্ত্র্যবোধ
‘বিদ্রোহী’ কবিতার অন্যতম বিশেষত্ব এটি কারও অনুকরণ করে গড়ে ওঠেনি। কবি মনের একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তার বাধাহীন স্রোতধারা হচ্ছে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা। কবিতাটিতে অসংখ্য ‘মিথ’ ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত বীরত্বের সৌকর্য্যকে অবিসংবাদিতরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে হাজার বছরের ইতিহাসে কোন কবিতা, গীতিকবিতা বা প্রবন্ধে বিদ্রোহের স্বরূপ কোনক্রমেই এমন প্রবলভাবে সুপ্রকাশিত হয়নি। অনেকে হয়ত মোহিতলাল মজুমদারের ‘আমি’ প্রবন্ধকে নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলপাঠ মনে করেন। অর্থাৎ নজরুল সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই প্রবন্ধের অনুকরণে ‘বিদ্রোহী’ রচনা করেছেন বলে অনেকে প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে নজরুল লেখক আজহারউদ্দীন খান তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যে নজরুল’ গ্রন্থে এই বিতর্কের একটি সহজ সমাধান উল্লেখ করেছেন। তিনি সপ্রমাণ দেখিয়েছেন যে, মোহিতলাল মজুমদারের ‘আমি’ প্রবন্ধের সঙ্গে কাজী নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনার কোন সম্পর্ক নেই, এমনকি ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনার সময় ‘আমি’ প্রবন্ধের কোন ভাবও চুরি করা হয়নি। ‘বিদ্রোহী’ কবিতা নজরুলের একান্ত মনের এককভাবের দ্যোতনা।
নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনা সম্পূর্ণ মৌলিক। পরাধীন জাতিকে মুক্তির সাধ এনে দেয়ার প্রাণান্তকর আকাক্সক্ষা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখিত হয় কবিতাটি। এই কবিতাটিতে বীরত্বব্যঞ্জক ‘পুরাণ’ দ্বারা ‘আমি’কে উপমিত করার চমৎকার নজীর পরিলক্ষিত হয়। কাজী নজরুল নিজেই অসাধারণ প্রাণশক্তির আধার ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রোহাত্মক কবিতার জন্ম দিয়েছেন অতি অবলীলায়, যেটিকে স্রষ্টা প্রদত্ত দান বলে অভিহিত করা যায়। রবীন্দ্র প্রতিভার এমন প্রখর দ্বীপ্তির মধ্যাহ্ন প্রহরে বাংলা সাহিত্যে সতন্ত্র ধারা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে কেবল ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনার মাধ্যমে। নোবেল লোরিয়েট কবিকে জনপ্রিয়তার শিখর থেকে নামিয়ে দিতে পারেন বলেই হয়ত কাজী নজরুল লিখলেন-
‘আমি চির-বিদ্রোহী বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত মম শির!
এখানেই নজরুলের স্বাতন্ত্র্য। কারও ভাবসম্পদ-চুরি বা অনুকরণ করে নজরুল সাহিত্য সাধনা করেননি। তাঁর চিন্তার চমৎকার বিশেষত্ব দ্রোহাত্মক কবিতা ও গানে সুপ্রতিষ্ঠিত।
২. গণমানুষের চাহিদা পূরণ
নোবেল বিজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও বিদ্রোহী ছিল। সেটি যুগের চাহিদা পূরণ করার মতো নয়। কারণ তুষের আগুনের বিদ্রোহ যুদ্ধের ময়দানে প্রযোজ্য নয়। যুদ্ধে প্রয়োজন কাঠের আগুনের লেলিহান শিখা; দাবানলসম অনির্বাণ ও দুর্দমনীয় দ্রোহ। দার্শনিক দ্রোহ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যা সাধারণ জনতার ধরা ছোঁয়ার বাইরের। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের এসব প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন ছিল ‘বিদ্রোহী’ কবিতা। সময়ের প্রয়োজনে জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা আনায়নে এমন উচ্চারণের কোন বিকল্প ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভূমিকম্পের মতো ঝাঁকুনি দেয়ার সাধ্য ‘বিদ্রোহী’ কবিতা ছাড়া আর কোন কিছুর ছিল না। ভূমিকম্প, টর্পেডো, ভিম-ভাসমান-মাইন, প্রভৃতি উপমা কবি সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপোসহীন অরিন্দম কবি সেদিন গণমানুষের মনের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই এমন কবিতা সৃষ্টি হয়েছিল।
৩. মুক্ত মানুষ মুক্ত স্বদেশ
মানুষ নিজের দাসত্বমুক্ত না হলে অন্যকে মুক্ত করতে পারে না। মন-দাসত্ব মুক্ত হওয়া প্রথম প্রয়োজন। তিনি বার বার ‘আমি’ শব্দ ব্যবহার করে আমিত্ব প্রকাশ করতে চাননি। বরং ভারতীয় উপমহাদেশের দুর্বল-ভিরু মানুষকে বীরের জাতিতে পরিণত করার প্রত্যয়ে প্রতিটি ‘আমি’ ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছেন, এই সর্ব ‘আমি’ যদি স্বনিয়ন্ত্রিত জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, যদি সমস্ত কুসংস্কার পিছুটানকে পশ্চাতে ফেলে নিজের মুক্তি কামনা করেন, তা হলেই প্রত্যেকে যথাযথ বীর হবেন। এ জন্য তিনি ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রথম স্তবকেই মানুষকে বীর বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে লিখেছেন
বল বীর- বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি’ আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
৪. জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ
‘বিদ্রোহী’ কবিতার দ্রোহাত্মক বক্তব্য ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আপাত প্রযোজ্য প্রতীয়মান হলেও মূলত আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়নি। বাঙালী সমাজের মোড়লী অত্যাচার থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বেনিয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিবাদ কবিতাটিতে বিধৃত হয়েছে। অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে জয়লাভ করে ভুখা নাঙ্গা, অসহায়-প্রপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিতদের মুখে হাসি ফুটিয়ে কবি শান্ত হওয়ার আকুল প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শুধু বঙ্গভূমি বা ভারতীয় উপ-মহাদেশ নয়, বরং সামগ্র পৃথিবীর সকল স্বৈরাচার দুঃশাসকের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়কে সচেতনভাবে তুলে আনার জন্য কবি হিন্দু পুরাণ, মুসলিম পুরাণ ও গ্রীক পুরাণকে ব্যবহার করে বিদ্রোহের ভাষাতে নানা মাত্রা প্রয়োগ করেছেন। কবি পুরাণের ইতিহাসে যারা বিদ্রোহী হয়েছেন, নানা ক্ষেত্রে, বহুবিধ কর্ম বিন্যাসে ও সর্বব্যাপী অন্যায়ের বিস্তৃত প্রতিরোধে তাঁদের অনুপম দক্ষতায় কবিতার ক্যানভাসে তুলে ধরতে বাধাহীন চিত্ত ও অসঙ্কোচ ব্রত দেখিয়েছেন।
৫. ‘আমি’
কবি ব্যবহৃত ‘আমি’ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ অর্থে ‘আমি’ সঙ্কীর্ণ চেতনার বহির্প্রকাশ। কিন্তু নজরুলের ‘আমি’ প্রথমত সমগ্র ভারবাসীর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি, এরপর সমগ্র পৃথিবীর পরাধীন জাতির কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। কারণ তিনি লিখেছেন, ‘আমি উপাড়ি’ ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে’
৬. অসাম্প্রদায়িকতা
বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুলের মতো এমন নজিরবিহীন অসাম্প্রাদায়িক মানুষ আর নেই। তিনি সংস্কৃতির পুরোধা আবার নিজে সংস্কৃত। অনেকে অসাম্প্রদায়িকতার কথা লেখেন, বলেন। কিন্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন না। ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করেন না। অর্থাৎ যা বলেন তা বিশ্বাস করেন না এবং যা বিশ্বাস করেন তা বলেন না। জনতার করতালি পছন্দ করেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান করেন না। কাজী নজরুল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। অন্তরাত্মা দিয়েই শুরু করেছিলেন অসাম্প্রদায়িকতা লালন এবং ব্যক্তি জীবনে তা করে দেখিয়েছেন। সমাজ-রাষ্ট্র বিশ্বে সেটি বাস্তবায়নে অসংখ্য পঙ্্ক্তি রচনা করেছেন। ‘বিদ্রোহী’ কবিতাতেও তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতার উর্ধে থেকে সাম্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা সৃষ্টির অজর, অমর, অক্ষয় স্বপ্ন দেখেছেন। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার পরতে পরতে হিন্দু-মুসলিম-গ্রিক পুরাণের সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে মূলত মানুষেরই জয়গান গেয়েছেন। দল-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী সকল নিপীড়িত পরাধীন জাতীর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। স্বৈরাচার ও দোর্দ-প্রতাপ দুঃশাসকের করাল গ্রাসে নিপতিত অধীন বিশ্বকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন।
৭. যুদ্ধ নয়, শান্তি
‘বিদ্রোহী’ কবিতায় শেষ স্তবকের পূর্ব পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের বচন-বাচন, শব্দ প্রয়োগ, শব্দ ব্যবহারের ধরন-ধারণ, বিদ্রোহী পুরাণ ব্যবহারসহ বাক্যবিন্যাস পর্যালোচনা করলে মনে হবে তিনি চরম উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়মের নিত্যসঙ্গী, প্রচলিত বিধিবিধান এবং আইনকানুনের তিনি তোয়াক্কা করেন না। তিনি যুদ্ধ সংগ্রাম ও ধ্বংস চান। কিন্তু শেষ স্তবকে তাঁর মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।
মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রাম তাই, অনিয়ম, দুঃশাসন ও অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণের চরম বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা হরণকারী নিপীড়ক-নির্যাতক ও নিরীহ মানুষ হন্তাকারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর যুদ্ধ পৃথিবীর সকল পরাধীন জাতির সপক্ষে। সকল শোষিত-বঞ্চিত, ভূখা-নাঙ্গা ভাগ্যাহত জাতির সপক্ষে। তিনি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বে মোড়লী করার বিশ্বযুদ্ধ চাননি। তিনি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার বিশ্বযুদ্ধ চান, যার মাধ্যমে বিশ্বে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।
উপসংহার
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘বিদ্রোহী’ কবিতা মানব সমাজে স্বাধীনসত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনবদ্য সৃষ্টি। মানুষ নিজেই যখন কুসংস্কারমুক্ত হয় তখন সমাজ রাষ্ট্রকে কুসংস্কারমুক্ত করতে পারে। পরাধীন জাতীর ওপর ভিনদেশী তস্কর-নিষ্ঠুর ও জালিম শাসকের দুঃশাসনের মাত্রা যত ভয়ঙ্কর হয়; স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামও তত কঠোর- কঠিন, দোর্দ- প্রতাপী এবং অপ্রতিরোধ্য হতে হয়। তাই ব্রিটিশ দুঃশাসন থেকে মুক্তির জন্য বিদ্রোহী কবিতা এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম। এই কবিতাটি পৃথিবীর বঞ্চিত, শোষিত নিপীড়িত-নির্যাতিত, পরাধীন সকল জাতির মুক্তি সংগ্রামের অনবদ্য শক্তির তেজোদীপ্ত উৎস।
লেখক : বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত গীতিকার








