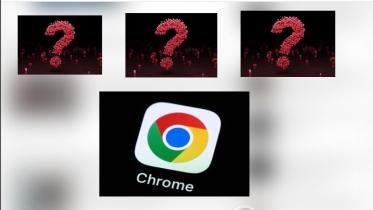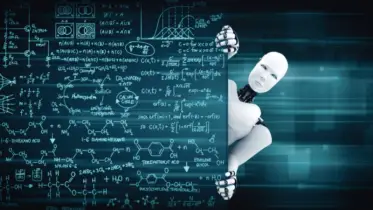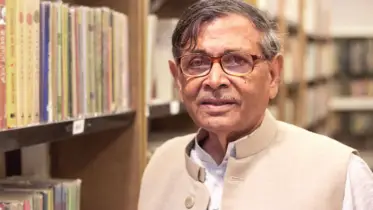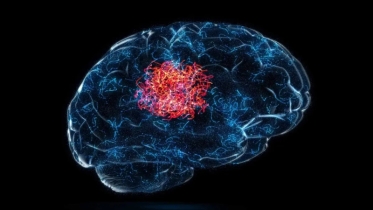বাঙালি জাতির একটি সংস্কৃতি, একটি উৎসব, একটি শেকড় সেটা হচ্ছে পহেলা বৈশাখ
বাঙালি জাতির একটি সংস্কৃতি, একটি উৎসব, একটি শেকড় সেটা হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। এটাই বর্তমান সময়ে প্রধান একটি দিন বাঙালি জাতির জন্য। একজন বাঙালির বাঙালিয়ানা উঠে আসে এই দিনটির মাধ্যমে। অনেকে নিজেকে একজন বাঙালি হিসেবে ভুলে গেলেও এই দিন যেন আবার মনে করিয়ে দেয়, ‘ওহে তুমি বাঙালি’।
বাংলা সনের ইতিহাস
খ্রিস্টাব্দ আর হিজরি সনের অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ। মূলত কৃষিকে কেন্দ্র করেই এর উৎপত্তি, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বাংলা সন কখন কিভাবে প্রবর্তিত হয়েছে বা কে এ সনের প্রবর্তক তা নিয়ে আছে নানান জনের নানা মত। বিশ্বের সবদেশের ইতিহাসের মতোই বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসও রচনা হয়েছে শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায়। ঐতিহাসিকদের লেখায় সিংহাসনের অধিকারীদের শৌর্য-ঐশ্বর্য আর বংশ-পরম্পরা উঠে এলেও ঠাঁই পায়নি সাধারণ মানুষের কথা। বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ যেহেতু প্রজাদের চাষাবাদের সুবিধায় প্রবর্তিত, তাই শাসকগোষ্ঠীর মুড়ি-মুড়কি খাওয়া ঐতিহাসিকদের রচনায় বাংলা সন উদ্ভবের কথা সেভাবে ঠাঁই পায়নি।
পরে পাল্টে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থায় ঐতিহাসিকরা গণমানুষের কথা ইতিহাসে তুলে ধরলেও বঙ্গাব্দ উৎপত্তির অকাট্য কোনো তথ্য-প্রমাণ খুঁজে পাননি। নানা সূত্র আর লোকমুখে প্রচলতি টুকরো ঘটনাকে এক সুতায় গেঁথে বাংলা সনের প্রবর্তক হিসেবে সিংহভাগ কৃতিত্ব মুঘল স¤্রাট আকবরের। পাশাপাশি বাংলা সনের পটভূমি তৈরি এবং এর বিকাশের পেছনে সুলতান হোসেন শাহ, রাজা শশাঙ্ক এবং তিব্বতি রাজা ¯্রংসনে অবদানের কথাও তুলে ধরেছেন গবেষক ও প-িতরা।
গবেষকদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বাংলা সন প্রবর্তনে মুঘল স¤্রাট আকবরের ভূমিকা উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে তারা স¤্রাট আকবরের স্বভাজন ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ সামনে রেখে বলছেন, গ্রন্থে বলা হয়েছে, স¤্রাট আকবর প্রজাদের চাষাবাদে চন্দ্রবছর হিজরি সন অনুসরণের অসুবিধার বিষয়ে অবগত হয়েছেন। তিনি হিজরি অব্দ ব্যবহারের বিরোধী। আকবর বহুদিন ধরে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে (দিন গণনার) সমস্যাকে সহজ করে দেওয়ার জন্য এক নতুন বছর ও মাস গণনাক্রম প্রবর্তন করতে আগ্রহী। এর নাম হলো ’ইলাহি সন’।
স¤্রাট আকবরের এই ‘ইলাহি অব্দ’ হলো সাধারণ কৃষকদের মাঝে চাষাবাদের সুবিধার্থে প্রচলিত দিন-মাস গণনার একটি সমন্বিত রূপ। ভারতবর্ষের সিংহাসনে স¤্রাট আকবর আরোহণ করেন ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন হিজরি সন ছিল ৯৬৩। বর্তমানে প্রচলতি বাংলা সনের হিসেবেও সেটি ছিল ৯৬৩ বঙ্গাব্দ। তার সিংহাসনে বসার বছরটি থেকেই চন্দ্রবর্ষ হিজরির পরিবর্তে সৌরবর্ষ ’ইলাহি সন’ গণনা শুরু হয়। যার পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত রূপই হলো বাংলা সন।
প-িতদের মতে, মুঘল আমলে রাজারা খাজনা আদায় করতেন চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী। চাঁদের উদয় অস্তের হিসাব করে গোনা হয় চান্দ্রবর্ষ। যেমন, আরবি হিজরি সন হলো চান্দ্রবর্ষ। আর সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণের ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয় সৌরবর্ষ। তখনকার দিনে কৃষকদের খাজনা চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী দিতে হতো। কিন্তু কৃষক তার জমির ফসল ঘরে তুলতে পারত একটি নিদিষ্ট সময় পর পর। চান্দ্রবর্ষ প্রতিবছর ১১ দিন করে এগিয়ে যেত যা কৃষকের খাজনা দেওয়া ও ফসল তোলার মধ্যে সমস্যা তৈরি করত। এতে কৃষকের খাজনা দেওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে যেত।
স¤্রাট আকবর তার শাসনামলের শুরু থেকেই সহজ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কার্যকর পদ্ধতিতে বছরের হিসাব রাখার কথা ভাবছিলেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার দায়িত্ব পড়ে সে সময়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোর্তিবিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর ওপর। তার প্রচেষ্টায় ১৫৮৪ সালের ১১ মার্চ ‘ইলাহী সন’ নামে নতুন এক সন চালু হয়। সে সময়ের কৃষকশ্রেণির কাছে এটি ‘ফসলি সন’ নামে পরিচিত হয়। পরে এটি ‘বঙ্গাব্দ’ নামেই পরিচিতি পায়।
কোনো কোনো প-িত বাংলা সন বা বঙ্গাব্দে প্রবর্তনের জন্য গৌড়ের স¤্রাট শশাঙ্ক, তিব্বতের রাজা গ্রংসনকে (তিনি ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে রাজা হন এবং মধ্যভারত ও পূর্ব ভারত জয় করে দুই দশক রাজত্ব করেন) এবং সুলতান হোসেন শাহকে মর্যাদা দিতে চান। একদল গবেষকের মতে, স¤্রাট শশাঙ্ক গৌড়বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিলেন ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল। ওই দিন থেকে বঙ্গাব্দের গণনা শুরু হয়েছিল। আরেকদল বলছেন, ‘৬০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে গ্রংসন নামে এক তিব্বতি রাজা মধ্য ও পূর্ব ভারত জয় করেন। তিনি তিব্বতের কৃষিকাজে প্রচলিত মৌসুম ভিত্তি দিন গণনা ভারতবর্ষে চালু করেন।
গ্রংসনের নামের শেষাংশ থেকে বাংলা ‘সন’ এসেছে। এই দুই মতের বিরোধিতা প-িতদের অপর একটি দল বলছেন, সুলতান হোসেন শাহের সময়ে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন চালু হয়। সুলতান হোসেন শাহ নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতেন। ‘শাহ-এ-বাঙালিয়ান’ বলে নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালিত্বের বিকাশেও শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও সুলতান হোসেন শাহের অবদান বিরাট। তার আমলেই প্রথম কৃষকদের ‘ফসলি সন’ শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য পায়।
শশাঙ্ক, গ্রংসন আর সুলতান হোসেন শাহকে বাংলা সন প্রবর্তনের সঙ্গে জড়ানোর পক্ষে কোনো প্রামাণ্য দলিল অবশ্য কেউই এখন পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের দাবি, লোকমুখে প্রচলতি নানা সূত্র ও অনেকটা অনুমানভিত্তিক। গ্রন্থসূত্র বিবেচনায় আবুল ফজলের ’আই্ন-ই-আকবরি’-তে উল্লেখ থাকায় মুঘল স¤্রাট আকবরকেই বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের মর্যাদা দিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনসহ সিংহভাগ গবেষক।
বাংলা সনের আধুনিকায়ন
বাংলা সন বা বঙ্গাব্দকে আজকের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব অবশ্য বাংলা একাডেমির। ১৯৬৬ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি কমিটি বাংলা সনের বিভিন্ন মাস ও ঋতুতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবনে কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাকে নির্ণয় করেন। যার মধ্যে ছিল বাংলা সনের ব্যাপ্তি গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির মতোই ৩৬৫ দিনের। যদিও সেখানে পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণের পরিপূর্ণ সময়কেই যথাযথভাবে নেওয়া হয়েছে। এই প্রদক্ষিণের মোট সময় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮
মিনিট এবং ৪৭ সেকেন্ড। এই ব্যবধান ঘোচাতে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির প্রতি চার বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি অতিরিক্ত দিন যোগ করা হয়। তবে বাংলা সনে অতিরিক্ত এই দিনটি রাখা হয়নি। এই সমস্যাগুলোকে দূর করতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কমিটি প্রস্তাবনায় বাংলা একাডেমি বাংলা সন আধুনিকায়ন ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। সিদ্ধান্ত হয়, বছরের প্রথম পাঁচ মাস অর্থাৎ বৈশাখ হতে ভাদ্র হবে ৩১ দিনের। পরের মাসগুলো অর্থাৎ আশ্বিন হতে চৈত্র হবে প্রতিটি ৩০ দিনের মাস।
প্রতি চতুর্থ বছরের ফাল্গুন মাসে অতিরিক্ত একটি দিন যোগ করে তা হবে ৩১ দিনের। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত হয়, বঙ্গাব্দের দিন গণনা শুরু হবে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই। ইংরেজি সন (খ্রিস্টাব্দে) দিন গণনা হয় রাত ১২টা থেকে। বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনের একটা বড় পার্থক্য হলো, ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করা হয় ঠিক রাত ১২টা থেকে আর বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।
পহেলা বৈশাখ উদযাপন যেভাবে শুরু
খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার সালে প্রাচীন ব্যাবিলনে নতুন বছর শুরু হতো নতুন চাঁদ দেখা সাপেক্ষে। পহেলা বৈশাখ বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাসের প্রথম দিন, তাই এটি বাংলা নববর্ষ। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে নববর্ষ উৎসব আমেজে পালন করা হয়।
মজার ব্যাপার হলো, আগে কৃষকদের মধ্যে ’ফসলি সন’ হিসেবে প্রচলিত আজকের বাংলা সন শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে। পহেলা অগ্রহায়ণ ছিল নববর্ষ। অগ্রাহয়ণে কৃষকরা মাঠের ফসল গোলায় তুলে অভাব-অনটন ভুলে একই সঙ্গে নববর্ষ ও নবান্নের উৎসবে মেতে ওঠতো। কৃষকদের সেই ফসলি সনকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন মুঘল স¤্রাট আকবর।
ঐতিহাসিকদের মতে, আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেককে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হতো। এর পরদিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। তখনকার সময় এই দিনের প্রধান ঘটনা ছিল একটি হালখাতা তৈরি করা। হালখাতা হলো একটি নতুন হিসাব বই। এটা বাংলা সনের প্রথম দিনে দোকানপাঠের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া।
পহেলা বৈশাখ গ্রামীণ সমাজে চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখী মেলার মাধ্যমে পালন করা হলেও একশ বছর আগে এই উৎসব ছিল নগরজীবনে অনুপস্থিত। কলকাতা ও ঢাকায় আধুনিক নববর্ষ উদযাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে। এরপর বিচ্ছিন্নভাবে পহেলা বৈশাখ পালন করা হলেও তা নগরজীবনে কিছুটা ব্যাপকতা পায় ষাটের দশকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি বিমাতসুলভ আচরণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে। তারই প্রতিবাদে ঢাকায় সংস্কৃতিকর্মীর সীমিত পরিসরে রমনা পার্কে পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু করে।
১৯৬৭ সালে ছায়ানট যুক্ত হয় এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে। পহেলা বৈশাখ উদযাপনের পরিধিও বেড়ে যায়। স্বাধীনতার পর তা আরও ব্যাপকতা পায়। নব্বই দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শেষে সেনাশাসনের অবসানের পর বাঙালি সংস্কৃতি উদযাপনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। এভাবেই পহেলা বৈশাখ আজকের সার্বজনীন রূপ লাভ করছে।
একদিনের সংস্কৃতি পরিহার করা জরুরি
নবর্বষ, এর মানে আমরা বুঝি নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া। এটা প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। ঠিক তেমনি বাঙালি জাতিরও পহেলা বৈশাখ নবর্বষ। এটাই আমাদের নতুন বছর। কিন্তু আমাদের কাছে আজ এটা কেমন যেন হয়ে গেছে। কারণ আমাদের কাছে পহেলা জানুয়ারি মানেই নতুন বছর! আমরা যে তাদের সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতিতে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এটাই আমাদের চরম ভুল। আমাদের বছর বাংলা, আমাদের সাল বাংলা কিন্তু আমরা চলি ইংরেজি সালে। অনেককেই যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আজ বাংলা সনের কত তারিখ।
সে দেখবেন আপনার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। তারখি তো দূরের কথা কত সন সেটাই বলতে পারবে না। কিন্তু সবাই আবার বর্ষবরণ করে। দেখতে একটু অন্যরকম লাগে। আমরা বাংলা সন অনুযায়ী চলি না, বলি না, করি না। অথচ আমরা এসা হে বৈশাখ এসো হে... করে গাইতে থাকি। তাহলে কি এটা আমাদের লোক দেখানো? কাউতে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, বাংলা নববর্ষ কখন? সে পহেলা বৈশাখ না বললেও ১৪ এপ্রিল ঠিকই বলবে। কারণ বাংলা মাস, বাংলা তারিখ এসব আমাদের কাছ থেকে এখন অনেকদূরে চলে গেছে। আমরা শুধু এখন লোক দেখানো একদিনের উৎসব করি।
প্রকৃত বাঙালি হয়ে উঠতে পারছি না। কিন্তু আমরা জানি না যে এই দিনটাই বাঙালির প্রাণ। আমরা যেভাবে এগুচ্ছি তাতে একদিন এই দিনটিও অর্থহীন হয়ে পড়বে। বাংলা র্চচা করি না ঠিকই কিন্তু ইংরেজি শেখার জন্য অনেক অনেক টাকা খরচ করে ফেলি। আমরা ইংরেজি শিখতে শিখতে এমন হয়ে পড়েছি বাংলায় আবার ইংরেজিও মেশাতে শুরু করেছি। আর যারা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশ্রণ করে কথা বলে, সমাজে তারাই আধুনিক। কিন্তু আমিতো আধুনিক হতে চাইনি। আমি একজন প্রকৃত বাঙালি হতে চেয়েছি। এ সমাজ বোধহয় সেটা আমাদের হতে দেবে না।
অথচ, আগেকার সময়ে সকলে বাংলা সনেই চলত, বাংলা সনেই কাজ করত। আজও আমার নানু বাড়িতে গেলে নানু জিজ্ঞেস করে, ‘নানাভাই আজকে বাংলা সনের কত তারিখ’? আমি নানুকে বালি, ‘নানু তুমি কি জান এটা বাংলা সনের কোন মান চলে’? নানু তখন চট করে বলে ‘আষাঢ় মাস আরকি’ আমি তখন অবাক! এখনো বাংলা মাস নিয়ে চলাফেরা করা মানুষ বাংলায় আছে এটা দেখে অনেকটা আনন্দিতও হলাম। নানু বলেন, এক সময় বাংলা সনের তারিখেই বিয়ে, অনুষ্ঠানসহ সব কিছু হতো। কিন্তু আজ আমরা দেখছি তার বিপরীত।
সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নোংরামি বন্ধ করতে হবে
নববর্ষের এই উৎসব নারী পুরুষ সকলের। উৎসবে যোগ দেওয়ার স্বাধীনতাও সবার সমান। কিন্তু দুঃখজনকভাবে নারী হয়রানি এবং নির্যাতনের বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে উদযাপনকালে, উৎসবস্থলে। এটি আমরা মেনে নেব না। এবারের নববর্ষের শুভক্ষণে মুছে যাক বিগত বছরের জরা এবং গ্লানি, যার মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন এবং আগুনের ঘটনাগুলো।
সকলের প্রতি আহ্বান, যার যার অবস্থান থেকে, বছরের প্রথম দিনটি থেকেই সকল প্রকার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি, আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ি। এছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনা থেকে কিভাবে প্রতিকার পেতে পারি সেটাও পহেলা বৈশাখ থেকে আমাদের সকলের ভাবতে হবে। শুধু আনন্দ নয়, দেশের কথাও ভাবার মাঝেও পাবেন পহেলা বৈশাখের আনন্দ।
পহেলা বৈশাখ আমাদের অহঙ্কার
পহেলা বৈশাখ হচ্ছে লোকজের সঙ্গে নাগরিক জীবনের একটি সেতুবন্ধন। ব্যস্ত নগর কিংবা গ্রামীণ জীবন যেটাই বলা হোক না কেন, এই নববর্ষই বাঙালি জাতিকে একত্রিত করে জাতীয়তা বোধে। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরাসহ দেশে বিদেশে বসবাসরত প্রতিটি বাঙালি এই দিন নিজ সংস্কৃতিতে নিজেকে খুঁজে পায়। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রতিটি বাঙালির কাছে শিকড়ের মিলন মেলায়। ধর্ম, বর্ণ সকল পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বাঙালি জাতি এই নববর্ষকে সাদরে আমন্ত্রণ জানায়।
গ্রামীণ মেলাগুলো পরিণত হয় উৎসবে। এই উৎসবের রংই একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়তে বাঙালি জাতিকে এগিয়ে নিয়েছে বারবার। নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য এদেশের মানুষ সব সময়ই আন্তরিক, অকৃত্রিম ও অগ্রগামী। দীর্ঘ প্রস্তুতির বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে অনেক আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সব পেশার মানুষ। বৈশাখী মেলা হালখাতা অনুষ্ঠান কিংবা নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয় এই নতুন বছরকে আমন্ত্রণ জানাতে। বাংলার পটশিল্পীরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। পটশিল্পে জায়গা করে নেয় আমাদের গ্রামীণ জীবনের নানা কথা।
লোকজ ব্যবহারিক তৈজসপত্রের বিভিন্ন অংকন শিল্প আমরা খুঁজে পাই এই পটচিত্রের মাধ্যমে। শিল্পী তার রঙ্গীন আল্পনায় স্বপ্ন দেখে আগামী দিনের। নিজ সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতির প্রজন্ম।
নগরকেন্দ্রিক ব্যস্ততাকে পিছে ফেলে সমস্তশ্রেণি পেশার মানুষ এই দিনটিকে সাদরে বরণ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বহু সাংস্কৃতিক সংগঠন মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রা সকল অপসংস্কৃতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিবাদ। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো ২০১৬ সালে এই মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।
বাঙালি সংস্কৃতির জন্য যা ছিল একটি বিশাল অর্জন। এছাড়া রমনার বটমূলসহ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় সংগীত, নৃত্যকলা কিংবা আবৃতি। এই শিল্পগুলোর প্রতিটিই স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের শিকড়কে। বরণ করে নেয় নিজ পরিচয়ের নববর্ষকে।
রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা
রাজধানীতে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের গানের মাধ্যমে নতুন বছরের সূর্যকে আহ্বান। ১৯৬৭ সাল থেকে পহেলা বৈশাখ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে গান গিয়ে নতুন বছরকে আহ্বান জানান। স্থানটির পরিচিতি বটমূল হলেও প্রকৃতপক্ষে যে গাছের নিচে মঞ্চ তৈরি হয় সেটি বট গাছ নয়, অশ্বত্থ গাছ।
ঢাকায় বৈশাখী উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ সকালে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। এই শোভাযাত্রায় গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। শোভাযাত্রায় সব শ্রেণি-পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার জন্য বানানো হয় রং-বেরঙের মুখোশ ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিলিপি। ১৯৮৯ সাল থেকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা পহেলা বৈশাখের উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ।
চট্টগ্রামে বর্ষবরণ এবং জব্বারের বলীখেলা
বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পহেলা বৈশাখের উৎসবের মূল কেন্দ্র আগে ডিসি হিলে থাকলেও এখন সিআরবি অন্যতম স্পট। এখানে সাহাবউদ্দিনের বলীখেলার মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়। এরপর বৈশাখের ১২ তারিখ শুরু হয় জব্বারের বলীখেলা। চট্টগ্রামের এই ঐতিহ্য এখনো বেঁচে আছে মানুষের আগ্রহের কারণে। এই বলীখেলাকে কেন্দ্র করে লালদীঘি ময়দানের আশপাশে প্রায় তিন কিলোমিটারজুড়ে বৈশাখী মেলার আয়োজন হয়। এটি বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকার সবচেয়ে বৃহৎ বৈশাখী মেলা। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর এই দেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়।
একসময় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলন। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ এবং একই সঙ্গে বাঙালি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা এবং শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের মনোবল বাড়ানোর প্রেরণা থেকেই চট্টগ্রামের বদরপতি এলাকার ব্যবসায়ী আবদুল জব্বার সওদাগর বলীখেলা বা কুস্তি প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। ১৯০৯ সালের ১২ বৈশাখ লালদীঘির মাঠে এই বলীখেলার সূচনা করেন তিনি। ব্যতিক্রমধর্মী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ব্রিটিশ সরকার আবদুল জব্বার মিয়াকে খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।
ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ছাড়াও বার্মার আরাকান অঞ্চল থেকেও নামি-দামি বলীরা এ খেলায় অংশ নিতেন। এছাড়াও এখানে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে পুরনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করার জন্য দুই দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুক্তমঞ্চে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকে নানা গ্রামীণ পণ্যের পশরা।
পরিশেষে বলতে চাই, একটি জাতি যখন তার নিজ সংস্কৃতিতে বলিষ্ঠ হয় তখন তাকে কোনো অপসংস্কৃতি, কু-সংস্কার গ্রাস করতে পারে না। তাই নিজ সংস্কৃতির সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা শিল্পগুলোর নিয়মিত চর্চার প্রয়োজন। যে কোনো জাতির কাছেই তার নিজ সংস্কৃতিই সেরা এবং আপন। বিশ্বায়নের এই যুগে নিজেদের সংস্কৃতির রক্ষায় এবং বিস্তারে আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির ছায়াতলে অবস্থান নিতে হবে। অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গেও আমরা পরিচিত হব, তবে তার আড়ালে যেন ঢেকে না যায় আমাদের স্বকীয়তা। কিন্তু বর্তমানে আমরা যেন সে পথেই হাঁটছি।
বাঙালি হিসেবে নিজ সংস্কৃতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থাকাও জরুরি। অন্যথায় পহেলা বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারি কিংবা বাঙালির যে কোনো উৎসব হবে অর্থহীন। বাঙালির প্রাণ পহেলা বৈশাখকে আরও অর্থবহ করতে হলে প্রয়োজন বাঙালির স্বকিয়তা ধরে রাখা। তবেই বাঙালির প্রাণ বাঁচবে।