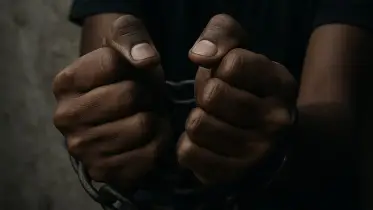ছোট বেলায় গ্রাম বাংলায় দেখেছি, পায়ে ব্যবহারের জন্য খড়ম ছাড়া তেমন কিছু ছিল না। চামড়ার জুতা বা স্যান্ডেল পরলেও তা ছিল হাতেগোনা। কেননা এটি ধনী ও সচ্ছল পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হয়তো অনেক প্রবীণ ব্যক্তি অবহিত আছেন যে একটি গ্রামে কারও এক জোড়া জুতা থাকলে, সেটা সারা গ্রামের বিবাহের ক্ষেত্রে বরের পায়ে শোভা পেত। সত্যি কথা বলতে কি, তখন গ্রামগঞ্জে অধিকাংশ লোক খালি পায়ে থাকত। কেবল ওজু ও ঘরে ঘুমানোর আগে পা ধুয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে ঘরে ঢুকত। অবশ্য বাড়িতে থাকার প্রাক্কালে খড়ম পরত। কিন্তু সবাই নয়। এদিকে দূর-দূরান্তে যেতে খড়ম ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। যদিও ব্যবহার কম হতো, তথাপিও শহর ব্যতিরেকে গ্রাম বাংলায় পায়ের জন্য ভরসা ছিল এক মাত্র খড়ম। যাহোক, তখন খড়ম দোর্দন্ত প্রতাপে আধিপত্য বজায় রাখলেও ষাটের দশকে পঞ্চ (ফোম) স্যান্ডেল অভিজাত্য নিয়ে খড়মের রাজ্যে ঢুকে। এখানে একটি কথা আছে, তা হলো পঞ্চ আসলেও সাধারণ জনগোষ্ঠির ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ছিল। কেননা এক জোড়া পঞ্চ স্যান্ডেলের দাম পাকা ১৮.০০ টাকা। আর সেই সময় সোনার ভড়ি ছিল মাত্র ২০০.০০ টাকার মতো। তাহালে বুঝুন, পঞ্চ স্যান্ডেল অহমিকা দেখাবে না কেন? এর এতটাই দেমাগ ছিল যে জুতা বাদ দিয়ে স্যুট পড়ে এই পঞ্চ স্যান্ডেল পায়ে দেওয়া অনেক বড় কর্মকর্তা ও ধনী-ব্যক্তিদের আমি দেখেছি। কালের পরিক্রমায় পঞ্চ স্যান্ডেলের দাম কমতে থাকে। মজার ব্যাপার হলো যে, এর মধ্যে রাবার ও প্লাস্টিকের স্যান্ডেল স্রোতের মতো আসতে থাকে এবং এতে পঞ্চ স্যান্ডেলের দাম দ্রুত কমে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালে আসে। এ সূত্র ধরে রাবার, প্লাস্টিক ও পঞ্চ খড়মের জায়গা দখল করে ফেলে। অবশ্য চামড়া স্যান্ডেল থাকলেও তুলনামূলক তার দাম বেশি। যাহোক, তখন খড়ম কোনঠাসা হয়ে পড়ে এবং অশ্রু সজল নয়নে ধীরে ধীরে চলে যাওয়ার পথ খুঁজতে থাকে। খড়মের চোখে জল দেখে, মাটির পাতিল ও কলসি বলে যে, তুমি কাঁদো কেন? আমরাও তো চলে যাচ্ছি এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিলের আগমনে। তাছাড়া ম্যালামাইনের কারণে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য কাঁসা ও পিতলের বাসন-কোসনের অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন।
এতক্ষন এ্যালিগোরী বা রূপকভাবে বললেও, আসলে এ সব কিছুর ব্যবহার কালচারের বহির্প্রকাশ বৈ কিছু নয়। আসলে চলমান সংস্কৃতি বা কালচার তার মতো করে চলে। কার কি ক্ষতি বা ভালো হলো, সেটা আমলে আনে না। এ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি বা কালচার নিয়ে কিছু কথা না বললে কমতি থেকে যাবে। বস্তুত সংস্কৃতি হলো সমাজের মানুষের জীবন ধারণের উপায়, যা তাদের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, ভাষা, শিল্পকলা, রীতিনীতি এবং নিত্যদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্রসহ জীবনযাত্রার পদ্ধতির মাধ্যমে বহির্প্রকাশ ঘটে। তাছাড়া সংস্কৃতি সময় ও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনশীল। তাই ব্যবহার্য জিনিসপত্রের পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এ সূত্র ধরে উল্লেখ্য, খড়মের স্থান যে রাবার, প্লাষ্টিক ও পঞ্চ দখল করে ফেলেছে, তাতে আশ্চার্য হওয়ার কিছু নেই। কেননা পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি সমাজের ধারক ও বাহক।
এবার আসুন প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূত্র ধরে সরাসরি খড়মের কথায় আসি। সাধারণত এক খণ্ড কাঠ পায়ের মাপে কেটে খড়ম তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে কাঠ হিসেবে কাঁঠাল, জাম, চালতা, হিজল, গর্জন ইত্যাদি উপযোগী। বস্তুত খড়ম দুই প্রকার, যেমন বর্তুলাকারে গুটি সম্বলিত খড়ম ও ফিতা লাগানো খড়ম। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, বর্তুল কাঠ দিয়ে প্রস্তুত। কিন্তু ফিতা পুরানো টায়ার কেটে; মোটা কাপড়, রাবার, চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। এক্ষেত্রে খড়মের সম্মুখভাগে বর্তুলাকারে কাঠের গুটি বসিয়ে দেওয়া হয়, যা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও পাশের আঙ্গুলিটি দিয়ে আঁকড়ে থাকে। এদিকে ফিতা ওয়ালা খড়মের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, একইভাবে খড়মের সম্মুখে মাপ মতো ফিতা কেটে দুই পাশের্^ টিনের টুকরার ওপর লোহার কাটা হাতুল দিয়ে পিটে লাগানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তুল সংবলিত খড়মের চেয়ে ফিতাওয়ালা খড়ম আরামদায়ক। কেননা বর্তুলের কারণে সংশ্লিষ্ট দুটি আঙ্গুল ব্যথা হয়ে থাকে। আরেকটি কথা, খড়ম পায়ে হাঁটা অতটা সহজ নয়। অধিকন্তু খড়ম পায়ে হাঁটার সময় চটাশ চটাশ শব্দ হয়, যা অনেকের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। তথাপিও খড়ম পায়ে দিয়ে কেউ আসলে এই শব্দ তার আগমনী বার্তা বললে ভুল হবে না।
পূর্বেই কিছুটা উল্লেখ করেছি যে, খড়ম একপ্রকার কাঠের পাদুকা। এই কাঠের পাদুকা বাংলায় ‘খড়ম’ নামে সুপরিচিত। আর এই খড়ম শব্দটি এসেছে হিন্দি ‘খড়ৌঙ’ থেকে। কিন্তু সংস্কৃতিতে পাদুকা নামেই পরিচিত। অবশ্য বিভিন্ন দেশে এই পাদুকা নানা নামে অভিহিত। যে ভাবেই বলি না কেন, সুদূর প্রাচীন কালে খড়মের উদ্ভব। এ সূত্র ধরে উল্লেখ্য যে, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞানী এরিক ট্রিঙ্কাউস তুষারযুগের মানুষদের নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, মানুষ জুতা পরতেন খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে। তবে পৃথিবীর প্রাচীনতম কাঠের জুতা বা খড়মের প্রথম সন্ধান মিলেছে যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন অঙ্গরাজ্যে, যা ছিল ৭ থেকে ৮ হাজার বছর আগের তৈরি। অবশ্য অনেকে বলে থাকেন যে, কাঠের টুকরা দিয়ে তৈরি প্রাচীনতম খড়মটি ছিল ১৩০০ শতকের, যা ব্যবহৃত হয়েছিল নেদারল্যান্ডে। তবে শুধু ডাচরাই নন, পশ্চিম থেকে পূর্ব বিশ্বের বহু উন্নত জাতির মধ্যেই খড়মের ব্যবহার দেখা গেছে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, খড়মের আদি-নিবাস নেদারল্যান্ড। আর কালক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশে^। এর স্বপক্ষে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৪ সালে যখন অক্সফোর্ড বিশ^বিদ্যালয়ে পড়ি। তখন সেক্সপিয়ারের বাড়িতে তাঁর ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে বর্তুল ওয়ালা খড়ম দেখেছিলাম। এদিকে, সনাতনী ধর্মে খড়মের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত। এক সময় দেবতার তুষ্টির জন্য পাদুকা পূজার প্রচলন ছিল। হিন্দুরা খড়মকে দেবতা ও শ্রদ্ধেয় সাধুসন্তদের পদচিহ্নের প্রতীকও মনে করতেন। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি জৈনধর্মেও ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী ও সাধুসন্তেরা খড়ম ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া হিন্দুদের মহাকাব্য রামায়ণে খড়মের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশে খড়মের ব্যবহার অনেক প্রাচীন। ১৩০৩ সালে বিখ্যাত সুফি দরবেশ ও পীর হজরত শাহজালাল (রহ:) সুদূর তুরস্ক থেকে সিলেটে এসেছিলেন খড়ম পায়ে দিয়ে। তার ব্যবহৃত খড়ম এখনো তাঁর সমাধিস্থল সংলগ্ন স্থাপনায় সুরক্ষিত আছে। সেই সময় থেকে বাংলার ভূস্বামী, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনের মধ্যে খড়মের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলায় পাদুকা বা জুতা বলতে তখন কাঠের তৈরি সেই খড়মকেই বোঝানো হতো, যা পূর্বেই কিছুটা উল্লেখ করেছি। অজু করে পুকুর ঘাট থেকে মসজিদে যেতে কিংবা রাতে শোবার আগে পুকুর থেকে পা ধুয়ে আসতে খড়ম ব্যবহার করা হতো। এদিকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যরা তখন খড়মকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেন। শত শত বছর ধরে বাংলার জমিদারদের কাছে পাদুকা হিসেবে এটি ছিল অদ্বিতীয়।
সাধারণত আশির দশক পর্যন্ত এই ঐতিহ্যবাহী খড়ম ব্যবহার হতে দেখা যেত। এদিকে ষাট-সত্তুর দশকে একজোড়া খড়মের দাম আট আনা (অর্থাৎ ৫০ পয়সা) থেকে বার আনা (অর্থাৎ ৭৫ পয়সা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য কাঠের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যমান অনুযায়ী দাম পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় কৃত্রিম সব পাদুকা আসার কারণে এখন শুধু স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এক সময় এই ঐতিহ্যবাহী খড়ম শিল্প সাহিত্যে বিশেষ অবস্থান নিয়ে ছিল। আর খড়মকে ঘিরে কম ছড়া, কবিতা ও গল্প প্রণীত হয়নি? তাছাড়া মিথ সাহিত্যেও খড়মের কথা উঠে এসেছে। পরিশেষে ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ঐতিহ্যবাহক খড়ম আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য সংস্কৃতি থেকে চির বিদায় নিতে বসেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে নতুন প্রজন্ম খড়ম বলে কিছু যে ছিল তা চেনেই না। তবে রংপুরের কিছু এলাকায় নাকি এই খড়ম পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।
লেখক : গবেষক ও অর্থনীতিবিদ
[email protected]
প্যানেল/মো.