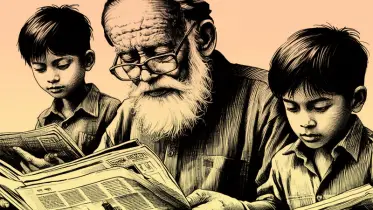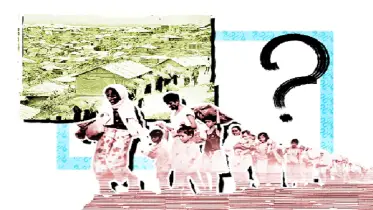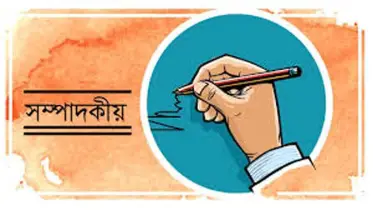অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা হ্রাসের ঘোষণা দিয়েছেন এবং নিজস্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে বাজেট পরিকল্পনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঘোষণাটি এমন এক প্রেক্ষাপটে এসেছে যখন ২০২২ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট মোকাবিলায় আইএমএফের ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তি ছাড়করণ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই ঋণের পরবর্তী কিস্তিগুলো ছাড় করা হয়নি। যার প্রধান কারণ ছিল কিছু শর্ত নিয়ে মতানৈক্য, বিশেষত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার উদারীকরণের বিষয়ে। অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ আইএমএফের পূর্ণাঙ্গভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার উন্মুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করছেন। আইএমএফ ক্রলিং পেগ ব্যবস্থার অধীনে থাকা ব্যান্ডের অপসারণের মতো শর্তও প্রস্তাব করেছিল। নারী-শিশু-শিক্ষা থেকে সমাজের সব বাজারের কেনাবেচার বস্তু বানিয়ে ফেলায় ঘোর বিশ্বাসী আইএমএফের এই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে সরকার অত্যন্ত ভালো কাজ করেছে। সরকারের কৌশলগত এই পদক্ষেপ সম্ভবত আইএমএফকে বোঝানোর একটি উপায় যে, বাংলাদেশের অন্য বিকল্পও রয়েছে এবং তারা কেবল ঋণের অবশিষ্ট অংশের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশ আইএমএফের কাছ থেকে কোনো অর্থ ছাড়াই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। তবে এই স্থিতিশীলতার মূল্যায়ন সতর্কতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। যদিও রিজার্ভ স্থিতিশীল মনে হচ্ছে, তবে এর অন্তর্নিহিত কারণ ও স্থায়িত্ব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এই অবস্থা ধরে রাখার জন্য।
বাংলাদেশের বর্তমান সরকার স্পষ্টভাবে বলেছে যে, আগের মতো আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং নিজস্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে বাজেট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আগ্রহী। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশ এমন কোনো ঋণের শর্ত মেনে নেবে না, যা দেশের অর্থনীতির জন্য উপযুক্ত নয়। সরকারের এই অবস্থান জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের ঋণদান মডেল এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। কারণ, আইএমএফের ঋণ প্রায়ই কঠোর কাঠামোগত সংস্কারের শর্তের সঙ্গে আসে, যা ভর্তুকি হ্রাস, কর ব্যবস্থার সংস্কার এবং সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধন অন্তর্ভুক্ত করে। সমালোচকরা মনে করেন যে, এই শর্তগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কঠিন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তৈরি করে। এছাড়া এই সংস্থাগুলোর চাপিয়ে দেওয়া বাজারভিত্তিক সংস্কারনীতি দারিদ্র্য বিমোচনের পরিবর্তে বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তোলে এবং স্থানীয় আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। রাষ্ট্রীয় নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়নে আন্তর্জাতিক আমলাদের হস্তক্ষেপ ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রে আবদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত। গবেষণায় দেখা গেছে, আইএমএফ ঋণের কাঠামোগত সংস্কার দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে।
বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ব্যতীত অন্যান্য বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক যেমনÑ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি) এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (আইডিবি) কাছ থেকে প্রকল্প সহায়তা আশা করতে পারে। এডিবি বাংলাদেশের আইএমএফের সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে, যা বর্ধিত সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত দেয়। সরকার এডিবির কাছ থেকে বাজেট সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যান্য বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের ওপর নির্ভরতা কমাতে সহায়ক হতে পারে। বিভিন্ন দেশ থেকে দ্বিপক্ষীয় সাহায্যও বাংলাদেশের জন্য অর্থায়নের একটি সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প অর্থায়ন উৎস। বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে আরও বেশি এফডিআই আকৃষ্ট করার বিষয়ে আলোচনা করেছে। বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে এফডিআই প্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সম্প্রতি রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যদিও বাংলাদেশে কার্যক্রম এখনো সীমিত, তবে উদ্যোক্তাদের জন্য শরিয়াহসম্মত বিকল্প অর্থায়নও উল্লেখযোগ্য একটি উৎস হতে পারে। এ ছাড়া ঋণভিত্তিক ও পুরস্কারভিত্তিক মডেলও হতে পারে কার্যকর উৎস। বিকল্প ঋণদান যেমনÑ পিয়ার-টু-পিয়ার লেন্ডিং এবং অন্যান্য অপ্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতিতেও বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বও (পিপিপি) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হচ্ছে, রাজস্ব সংগ্রহের কাঠামো পরিবর্তন। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত কম। কার্যকর ও ন্যায্য কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত গরিবমুখী করপ্রথা সংস্কার করে ধনীমুখী করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন কর ব্যবস্থার সরলীকরণ, ইলেকট্রনিক ফাইলিং, পেমেন্ট বাস্তবায়ন, কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ঘুষ-দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স। কর ছাড়ও যৌক্তিকীকরণও জরুরি। বাংলাদেশে অতীতে কর ব্যবস্থার সংস্কার করা হলেও কর-জিডিপি অনুপাতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটানো যায়নি। দুর্বল কর প্রশাসন, কম পরিপালন এবং নীতিগত দুর্বলতা রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। রাজস্ব সংগ্রহের উন্নতির জন্য কর ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন এবং বিভিন্ন কর বিভাগের সমন্বয় জরুরি। কালো টাকা মোকাবিলা ও আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সরকারের প্রচেষ্টা ও চ্যালেঞ্জ মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, কালো টাকা সাদা করার বিভিন্ন সুযোগ দেওয়া হলেও এর সাড়া ছিল কম এবং কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই ধরনের পদক্ষেপ দুর্নীতিকে উৎসাহিত এবং সৎ করদাতাদের নিরুৎসাহিত করে। সম্প্রতি সরকার কিছু ক্ষেত্রে কালো টাকা সাদা করার সুবিধা বাতিল করেছে। কালো টাকা কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য শক্তিশালী আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থা ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের নীতিপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ঋণগ্রহণকারী কোনো দরিদ্র দেশ ধনী হওয়ার কাছাকাছি যেতে পেরেছে এমন কোনো নজির নেই। বরং এসব সংস্থার ওপর নির্ভরশীল প্রতিটি দেশে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য কেবলই বাড়তে দেখা গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এসব সংস্থার চাপিয়ে দেওয়া কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (এসএপি), শুল্ক অপসারণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলোর বেসরকারিকরণ ও শ্রম সুরক্ষা হ্রাস করার ফলে চাকরিচ্যুতি, মজুরি স্থবিরতা, শ্রমিকদের বিশেষ করে নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠী আরও দুর্বল হয়েছে। তাদের সহায়তার নামে আরও ঋণগ্রহণে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত ঋণের বোঝা আরও বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে। উচ্চ ঋণগ্রস্ত দেশগুলো সামাজিক পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগের চেয়ে ঋণ পরিশোধকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হয়েছে, যা বৈষম্যকে আরও বাড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে অনেক নিম্ন আয়ের দেশকে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের ঋণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে এসওপি বাস্তবায়ন করতে হয়েছিল। এর ফলে সামাজিক ব্যয় হ্রাস, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলোর বেসরকারিকরণ ও বিকৃত শিল্পধারা সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ আদমজী জুট মিলসহ দেশের অধিকাংশ পাটকল ও চিনি মিল বন্ধ করা হয়েছিল। এর পরিণতিতে বাংলাদেশ এখন চিনি আমদানির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পাটের বাজার ভারতের দখলে। অক্সফামের প্রতিবেদন বলছে, বিশ্বে আগের চেয়ে বেশি শত কোটিপতি রয়েছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির সম্পদের মাত্র ১ শতাংশ সাড়ে ১০ কোটি জনসংখ্যার ইথিওপিয়ার সমগ্র স্বাস্থ্য বাজেটের সমতুল্য। এর ফলে ইথিওপিয়ায় আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের ঋণের জাল বিস্তার সহজ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকই স্বীকার করেছে, ২০১৩ সাল থেকে দারিদ্র্য হ্রাসের হার অর্ধেক হয়ে গেছে এবং অধিকাংশ উন্নয়শীল দেশে চরম দারিদ্র্য আসলে বাড়ছে। হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ দারিদ্র্য বৃদ্ধির জন্য চীনকে দায়ী করে বলা হয়েছে, গত ২৫ বছরে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাসের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ চীনের কারণে হয়েছে। কারণ, দেশটি ব্যাংক ও তহবিলের প্রচলিত নীতি সুপারিশগুলো অনুসরণ করেনি।
পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য রাখলেও নির্দিষ্ট প্রকল্প অর্থায়ন বা কারিগরি সহায়তার জন্য আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক ধাক্কার সময় ঝুঁকির কারণ হতে পারে, যা প্রশমনে কার্যকর নীতি চূড়ান্ত করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসের জন্য নিজস্ব শক্তিশালী পূর্বাভাস সক্ষমতা তৈরি করা উচিত। সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন না করলেও আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে একটি বাস্তবসম্মত ও সুনির্ধারিত সম্পৃক্ততা বজায় রাখা প্রয়োজন সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও নির্দিষ্ট প্রকল্প অর্থায়নের সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য। একই সঙ্গে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার স্পষ্টভাবে তুলে ধরে সম্মানজনক অংশীদারিত্বের সন্ধান করতে হবে।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্যানেল