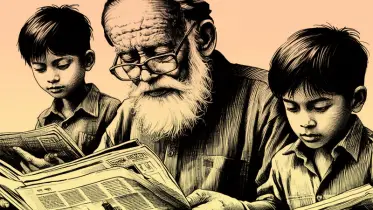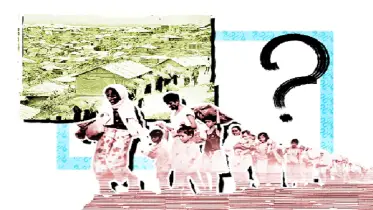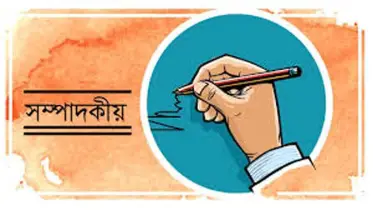বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই। রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভোগ, মানব মহিমাবোধ এবং প্রকৃতি ও মানবের মিলনে অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভূতি। কবির কাছে প্রকৃতি জড় নয়, প্রাণময়ী। তাঁর কর্মকুশলতা, চিন্তা-চেতনা ও সৃষ্টিশীলতা এই সংস্কৃতিকে দিয়েছে নানা রূপময়তা, রঙ, গন্ধ ও বৈচিত্র্যমুখিতা। সংস্কৃতির এত বড় সংগঠক প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান আধুনিককালেও বাঙালি সমাজে জন্মগ্রহণ করেনি। তিনি আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান রূপকার। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। গতকাল ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী।
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্র চিত্রকলা জগতের অভিনব সৃষ্টি, অনন্যসাধারণ। তাঁর চিত্রকলা একান্তরূপে তাঁর নিজস্ব, তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। এ চিত্রকলার হুবহু অনুকরণ কারও পক্ষেই যেমন সম্ভব নয়, তেমনি মনের মতো করে সমুচিত ব্যাখ্যা দেওয়াও অসম্ভব। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ কবিতার কাটাকুটি করতে গিয়ে ছবি আঁকায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৪ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তাঁর ছবি আঁকার সময়কাল। অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের মতো লোক, যারা ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রশিল্পের দিকপাল, তাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য তাকে ছবির প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যেমন সহজাত, তেমনই চিত্রশিল্পও তার সহজাত। বলতে গেলে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে স্কেচবুকে তার আঁকাআঁকির শুরু জীবনীকারদের তথ্যে তা পাওয়া যায়। ১৮৯৩ সালে শাহজাদপুর থেকে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন, ‘ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি- অন্যান্য বিদ্যার মতো তাকে তো সহজে পাবার জো নেই- তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তার প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। রবিঠাকুর পেয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও। ১৯৩০ সালে প্যারিস শহরের পিগ্যাল আর্ট গ্যালারিতে তার প্রথম শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পরে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে এ প্রদর্শনী চলে। বিশেষ করে বার্মিংহাম, লন্ডন, বার্লিন, মিউনিখ, কোপেনহেগেন, জেনেভা, মস্কো, বোস্টন, নিউইয়র্ক এবং সবশেষে ১৯৩১ সালের মে মাসে ফিলাডেলফিয়ায় শেষ হয় এ প্রদর্শনী।
অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ
নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা বরাবরই ঠাকুর বাড়িতে লক্ষ্য করা যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য সাধনার পর্যায়কে অস্বীকার করার সুযোগ স্বল্পই আছে। নাট্যপ্রয়োগের জন্যও সমকালে এ বাড়ি বিশেষ হয়ে উঠেছিল। বাড়ির মঞ্চেই প্রথম অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৭৭ সালে অভিনয় করেন ‘এমন কর্ম আর করব না’ প্রহসনে, এখানে তার চরিত্রের নাম ছিল অলীকবাবু। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৮৮১ সালে নিজের লেখা নাটকে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকের নাম ‘বাল্মিকী প্রতিভা’। তাঁর বয়স তখন ২০। এই নাটকে একাধারে সুরযোজনা ও নির্দেশনার কাজ করেন তিনি। ‘বাল্মিকী প্রতিভা’ নাটকের দর্শকসারিতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। ১৮৮২ সালের ২ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় ‘কালমৃগয়া’। এরপর আর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি। এ নাটকে তিনি অভিনয় করেছিলেন অন্ধমুণির চরিত্রে। ১৮৮৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ‘রাজা ও রানী’ নাটকে বিক্রমদেব চরিত্রে অভিনয় করেন। এই নাটকে তাঁর অংশগ্রহণ ও নাটকের বিবরণ দেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেন, ‘দেবদত্ত সেজেছিলেন মেজো জ্যাঠামশায়, সুমিত্রা মেজ জ্যাঠাইমা, রাজা রবিকাকা, ত্রিবেদী অক্ষয় মজুমদার, কুমার প্রমথ চৌধুরী, ইলা প্রিয়ম্বদা, সেনাপতি নিতুদা, যেমনি লম্বা চওড়া ছিলেন স্টেজে ঢুকলে মনে হতো যেন মাথায় ঠেকে যাবে।’
রবীন্দ্রনাথের ৬২ বছর বয়সে এম্পায়ার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল ‘বিসর্জন’। ১৯২৩ সালে মঞ্চস্থ এই নাটকে রাজা সেজেছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথ এবং জয়সিংহের ভূমিকায় কবি নিজেই অভিনয় করেছেন। ১৯১৬ সালে অভিনীত ‘ফাল্গুনী’ নাটকে তিনি বাউলের চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরুর বাউলমূর্তি এঁকেছিলেন। ৫৫ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ নাচ, গান ও অভিনয়ের ত্রিবেনী সঙ্গমে দর্শকের ওপর ব্যাপক প্রভাব রেখেছেন। ১৯১৭ সালে মঞ্চস্থ হয় ‘ডাকঘর’। একই বছর লিখিত এই নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয় শান্তিনিকেতনে। কলকাতার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর ‘অরূপরতন’ মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯০৯ সালে শান্তিনিকেতনে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ অভিনীত হয়। পরের বছর আরও দুবার মঞ্চস্থ হয় নাটকটি। এই তিনবারের মধ্যে দুবার রবীন্দ্রনাথ নাটকটিতে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই চরিত্রে অভিনয়ের সময় তিনি গান ও নাচের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন, যাতে বাউল ভাবটি প্রকাশিত হয়। ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতনে মঞ্চস্থ হয় ‘রাজা’। এখানে তিনি অভিনয় করেন ঠাকুরদার ভূমিকায়।
বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ
বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নোবেলজয়ী এই কবির জীবনের আরেকটি অপরিচিত দিক হলো, জীবদ্দশায় তিনি পণ্যের বিজ্ঞাপনের অত্যন্ত জনপ্রিয় তারকা ছিলেন। আজকালকার দিনে বিজ্ঞাপন জগতে সিনেমার নায়ক-নায়িকা আর ক্রিকেটারদের জনপ্রিয়তা যেমন আকাশছোঁয়া, ঠিক তেমনি। আর রবীন্দ্রনাথ যেসব পণ্যের বিজ্ঞাপন করতেন তার কাটতিও বেড়ে যেত হু হু করে। কেমন ছিল তাঁর বিজ্ঞাপনের ধরন? একটি মজার নমুনা দিয়ে শুরু করা যাক। লিপটন চায়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ-বিরচিত বিজ্ঞাপন : চা-স্পৃহ চঞ্চল, চাতকদল চল কাতলি-জল তল, কলকল হে... বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, রবীন্দ্রনাথ একজন অতি-উৎসাহী চা-প্রেমী। ফলে সেই সময়ের চা-খোর শৌখিন মানুষদের মধ্যেও তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। ১৮৮৯ থেকে মৃত্যুর বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ছোট-বড়, পরিচিত-অপরিচিত বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ অংশ নিয়েছেন। ঘি থেকে ত্বকের ক্রিম, মিষ্টি থেকে হারমোনিয়াম কোনোকিছুই বাদ নেই এর মধ্যে। তবে মডেলরা যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করে মনমাতানো হাসির ঝিলিক দিয়ে বিজ্ঞাপন করেন, ঠাকুরমশাই নিশ্চয়ই ওভাবে বিজ্ঞাপন করেননি। বিজ্ঞাপনে থাকত তার সেই বিখ্যাত গোঁফ-দাড়িওয়ালা ছবি আর স্বাক্ষরসহ ওই পণ্য সম্পর্কে কিছু কথা। তবে বিজ্ঞাপনের জন্য লিখে দেওয়া বাণীতে তিনি যে স্রেফ পণ্যের গুণগান গেয়েছেন তা কিন্তু নয়। ওইসব বাণীর মধ্যে ছিল রস, বুদ্ধিমত্তা, ছন্দ, শ্রুতিমধুরতা, দেশপ্রেম আর থাকত একটা দৃশ্য বা সমাজের কোনো একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত। নেহাত শখে যে এ সব বিজ্ঞাপনে সম্মতি দিতেন, তা নয়। জানা যায়, মূলত বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহই ছিল তাঁর বিজ্ঞাপন জগতে আসার কারণ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে ব্রিটিশের দেওয়া নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন। সেই ঘটনার সূত্রেও এক পানীয় কোম্পানি নিজেদের বিজ্ঞাপনে লিখেছিল, ‘টেগোর হ্যাজ গিভ্ন আপ হিজ নাইটহুড বাট ক্যান ইউ অ্যাফোর্ড টু গিভ আপ ড্রিংকিং আওয়ার ফ্রুট?’ এতেই বোঝা যায় তাঁর বিজ্ঞাপনযোগ্যতা কেমন ছিল।
গায়ক রবীন্দ্রনাথ
জীবন স্মৃতির প্রথম পান্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘আমাদের পরিবারে গানচর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা গড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। ‘তাঁর স্মৃতিচর্যায় ধরা পড়েছে : ‘মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল। কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না।’ রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি এলে বারান্দায় শীতলপাটি বিছিয়ে সংগীত ও সাহিত্যের আসর বসত। শান্তিময়ী দত্ত লিখেছেন, ‘এমনই একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ গাইলেন ‘আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।’ তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, গাওয়ার সময় সর্বদাই আশপাশের গায়ক-গায়িকাদের নিজের সঙ্গে গাইতে বলতেন ও গানটি শিখে নিতে বলতেন। ঐ গানটি সেদিন রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সুরে গাইলেন যে, শান্তা-সীতা অবাক হয়ে নিঃশব্দে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ করে কবি বললেন, ‘কি রে, তোরা চুপ করে রইলি কেন? আমার সঙ্গে গাইতে পারলি না?’ সীতাদেবী বললেন, ‘কি করে গাইব? আপনি যে সম্পূর্ণ নতুন সুরে গাইলেন। এ সুর তো আমাদের জানা নেই!’ কবি হেসে বললেন, ‘তাই নাকি? তোরা কি সুর শিখেছিস শোনা দেখি।’ তারা অন্য সুরে গানটি গেয়ে শোনানোর পর তিনি বললেন, ‘তা হবে। আমারই হয়তো ভুল হয়েছে।’ কলকাতার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া শেষ গান শোনার অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায় শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ‘যাত্রাপথের আনন্দগান’-এ– স্টেজে দাঁড়িয়ে ‘আমি রূপে তোমায় ভোলাব না’ গানটি নিজে গাইলেন। তখন আমি গানের দল থেকে বেরিয়ে গান শোনবার লোভে কাউকে না বলে অডিটরিয়ামে চলে গিয়েছিলাম। গানটি যথারীতি গেয়ে গুরুদেব স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে লক্ষ্য করলেন যে, গানের দলে আমি বসে নেই। আমিও তাড়াতাড়ি অডিটরিয়াম থেকে ফিরে আসছিলাম এবং আসতে গিয়ে সামনে পড়ে গিয়েছি। পড়ে যাওয়াতেই তিনি এক ধমক লাগালেন। বললেন, ‘গানের দলে যে তোমাকে দেখতে পেলাম না! তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কোথা থেকে আসছ?’ তার উত্তরে তেমনি সুর চড়িয়ে আমিও বললাম, ‘আমি ঠিক জায়গায় ছিলাম।’ তখন চাপা গলায় বললেন, ‘শোনা গিয়েছিল তো?’” অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ যে কত মধুর ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, ‘গলা ছিল তাঁর আশ্চর্য। রবীন্দ্রনাথ বন্ধু হিসেবে আমাদের বাসায় প্রায় প্রত্যহই আসতেন এবং প্রায় প্রত্যহই তাঁর স্বরচিত গান শুনতুম।’
লেখক : ব্যাংক কর্মকর্তা ও সংস্কৃতিকর্মী
প্যানেল