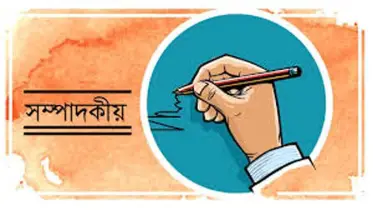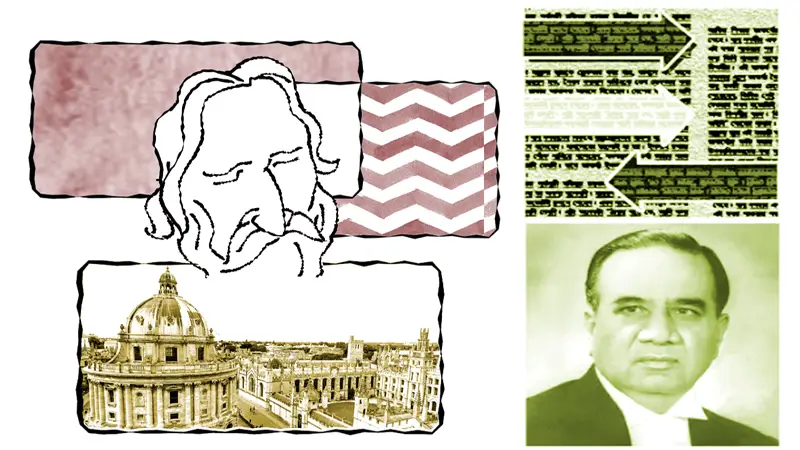
রবীন্দ্রবিরোধিতার দুটো দিক। সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক
রবীন্দ্রবিরোধিতার দুটো দিক। সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক। রবীন্দ্রনাথ নিজে রাজনীতিতে নেমেছিলেন একবারই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে রাজনীতি হয়েছে বার বার। নোবেল পাওয়ার দু’বছর পর উনিশ শ’ পনেরো সালে রাজা পঞ্চম জর্জ নিজের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে ‘নাইটহুড’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এ উপাধি দেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকাই স্বাভাবিক ছিল। নাইট খেতাব গ্রহণ করায় অনেকের মধ্যে অস্বস্তি থাকলেও প্রায় সদ্য অর্জিত নোবেল প্রাইজ প্রচণ্ড উদ্দীপ্ত করেছিল ভারতীয় তরুণদের। সে সময়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের ছাত্র হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর এক লেখায় এর আঁচ পাওয়া যায়।
উনিশ শ’ তেরো সালে ইউরোপ ভ্রমণের অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ইংল্যান্ডে কাটিয়েছিলেন। সে সময় অক্সফোর্ডে ভারতীয় ছাত্রদের ক্লাব ‘অক্সফোর্ড মজলিস’-এর অন্যতম সদস্য আইন বিভাগের ছাত্র হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। অক্সফোর্ডে তিনি দু’দিন ছিলেন।
উনিশ শ’ একচল্লিশ সালে কবির মৃত্যুর পর মুসলিম লীগ নেতা এবং অবিভক্ত বাংলার প্রজাপার্টি- মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তিরিশ বছর আগে অক্সফোর্ডে কবির সঙ্গে কাটানো সেই দু’দিনের স্মৃতিচারণ করেন, যা দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে রবীন্দ্র স্মরণে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়েছিল। ‘অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ’ নামে লেখাটি অনুবাদ করেছেন হেমায়েত উদ্দীন আহম্মেদ।
‘১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন, আমি তখন অক্সফোর্ডের ছাত্র। সে সময়ে আমরা, ভারতীয়রা সংখ্যায় খুব বেশি ছিলাম না। কিন্তু আমাদের সবাই মিলে ছিলাম একদল উচ্ছ্বল উদ্দাম তরুণ-গভীর দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত। এই দেশপ্রেমের অনেকটাই ছিল আবেগতাড়িত।
আবেগের আতিশয্যই ক্রমে আমাদের আকর্ষণ করে চরমপন্থি জাতীয়তাবাদের (বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ) দিকে। কোনো মধ্যমপন্থি নরম নীতিতে আমরা ছিলাম অধৈর্য। সে সময়ে অক্সফোর্ডে আধুনিক ভারতীয়দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। শেষ পর্যন্ত কোনো দিকেই না গিয়ে সমসাময়িক অনেক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মতো নিজেদের আমরা সমাজবাদী বলতে শুরু“করলাম।
অবশ্য, আমার কাছে এই সমাজবাদ মনে হতো এক অস্পষ্ট ঢিলেঢালা, ঐতিহ্যভিত্তিক, ইন্দ্রিয়াতীত পরম দেশপ্রেমের প্রতিভাস মাত্র। অক্সফোর্ডে তখন ভারতীয় ছাত্রদের একটি ক্লাব ছিল। কয়েক বছর আগে, হর্ষ দয়াল নামের একজন ভারতীয় এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেন। নাম ছিল ‘অক্সফোর্ড ইন্ডিয়ান ক্লাব’। ক্লাবটির কোনো আঁটসাঁট সাংগঠনিক রূপ ছিল না। ক্লাবের একমাত্র কাজ ছিল প্রতি সপ্তাহান্তে রবিবার বিকালে কেক-পেস্ট্রিসহ চা-চক্রে আড্ডা দেওয়া। ১৯১২ সালে আমরা এই ক্লাবটি দখল করে নিই এবং এর নতুন নামকরণ করি ‘অক্সফোর্ড মজলিস’।
এই মজলিসে আমরা প্রথম নাম বিতর্ক বিষয়ে চোখা চোখা বক্তব্যসহ আলোচনা শুরু করলাম। এই বিতর্ক-আলোচনায় তুখোড় ইংরেজ ও ভারতীয় ছাত্ররা এসে একে একে অংশ নিতে শুরু করে। ফলে, সকলের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সপক্ষে এক অভূতপূর্ব ঐক্যবোধ ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। আমরা নির্বাচন ও অন্যান্য মতদ্বৈততার ক্ষেত্রে দলগতভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করার ও ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দেওয়ার অভ্যাসও গড়ে তুলি।
অক্সফোর্ড মজলিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-রাজনীতিতে এক শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে অচিরেই পরিচিতি লাভ করে। ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের সময় মেধাবী ও সুবক্তা ইংরেজ ছাত্ররাও আমাদের মজলিসের সভায় বক্তৃতা করতে চাইতেন- আমাদের সমর্থন লাভের আশায়, কখনো কখনো তাতে তাদের পূর্বেকার কঠিন ও গোঁড়া মতবাদ একটু পরিবর্তিত ও নরম করে হলেও। ক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে সত্যি সত্যি আমরা একটা বড় শক্তি হয়ে উঠি।
এতে অক্সফোর্ডে অধ্যয়নরত আমাদের সকলের মনে একটা গর্বের ভাব জেগে ওঠে। প্রায়ই নৈশভোজ শেষে ক্যাম্পাসের অলিগলি আমাদের গঠিত পদচারণায় মুখর হয়ে উঠত। মাঝে মধ্যে ইংরেজ ছাত্রদের প্রতি অসম্মানজনক কটূক্তি করতেও আমাদের দ্বিধা হতো না। অবশ্য ব্রিটিশবিরোধী কথাবার্তার ও স্লোগানের পাল্টা জবাব দিতে তারাও কম যেত না। বলতÑকালো ছেলেরা, কালো দেশে ফিরে যাও।
এমনি সময়, আমাদের কাছে খবর এলো, এবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন আমাদের (ভারতীয়দেরই) একজন। এতে আমাদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন সকালে খবরের কাগজে খবরটি বের হলো, সেদিন আমার ল্যান্ডলেডি ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসার পর তাঁর চোখে কি এক বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি দেখেছিলাম।
আমি অবশ্য ভান করে বললাম, ‘এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? এমন যে হবে, তা তো জানাই ছিল।’ আসলে, মল্লিক দার কাছে এ খবর আমি আগেই পেয়েছিলাম। এরই মধ্যে তিনি লন্ডন গিয়ে কবির সঙ্গে দেখাও করে এসেছেন।
তবে বাইরে আমি যাই দেখাই, বলতে বাধা নেই, কয়েক শতাব্দীর অধোগতি ও ভাগ্যবিড়ম্ব^নার পর দেশের জন্য এই অভূতপূর্ব সম্মান আমাদের সকলের মাঝে এক নতুন প্রয়াসের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নিজেদের ওপর আবার আমরা আস্থা ফিরে পেলাম। একদিন আমাদের পরিচয় ছিল ম্যাক্সমুলার অনূদিত বৈদিক জপমন্ত্রের রচয়িতাদের ভ্রষ্ট, বিড়ম্বিত বংশধর হিসেবে, অথবা ঈশ্বরভক্ত, অদৃষ্টে বিশ্বাসী এক অলস জনগোষ্ঠী হিসেবে বা বড়জোর গঙ্গাতীরের বিপ্লবী সন্ত্রাসী হিসেবে। এতদিন পর আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে অধিষ্ঠিত হলাম এবং আমাদের লুপ্ত গৌরবের আসন ফিরে পেলাম।
ভারতের অতীত গৌরবগাথা নিয়ে গর্ব করলেও শৈশব ও কৈশোরে আমার শিক্ষার ধারা এমনি ছিল যে, বাংলায় পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার সুযোগ মোটেই হয়নি। বলতে এখন লজ্জা হয়, পড়া তো দূরের কথা, ভাল মার্জিত বাংলায় কথা বলতেও হিমশিম খেতে হতো। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সব কবিতা ও গানের কথা আমি শুনেছি। বাংলার শহরে ও গ্রামে গ্রামে কবির গান খুব জনপ্রিয় তাও জানতাম। তবে বিশ্ব সাহিত্যের তুলনায় তার অবস্থান নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল।
এখন ইংরেজি ভাষান্তরে কবির সেই সব অনবদ্য সৃষ্টি আমি বুঝতে পারছি। এর ভাব ও ছন্দের অভিনবত্বে ও সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। আরও অভিভূত হচ্ছি রদেনস্টাইন, স্টার্জ ও ইয়েটসের মতো কবি-সাহিত্যিক যাঁদের নাম বহুদিন থেকে আমার মনে গাঁথা ছিল, কবির প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধাবোধ দেখে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের আন্তরিক সখ্য দেখে।’
সাহিত্যে রবীন্দ্র বিদ্রোহের কথা তো সবার জানা। তবে বেশিরভাগ বিদ্রোহ ছিল যতটা না রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে ঘিরে যে আদিখ্যেতার বলয় তৈরি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। কল্লোল যুগের রবীন্দ্রবিরোধীরা মুখে বিরোধিতা করলেও অন্তর তাদের ছিল রবীন্দ্রময়ই। তার পরের জেনারেশনের বিরোধিতা ছিল অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ। তারা তাঁর লেখার দুর্বল দিকগুলো নির্মোহভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তাদের মধ্যে যে আবেগের আতিশয্য ছিল না তাও নয়।
কল্লোল যুগের বিদ্রোহীরা অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁর কাব্যে কৃষক মজুরের কথা নেই। রুশ কথাসাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের সাহিত্যে বিপ্লব ও প্রতিরোধ বিরোধিতা, খ্রিস্টধর্মের প্রচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে থাকার পরও রুশ কৃষকের সত্যিকারের চেহারা যেভাবে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথে তা অনুপস্থিত। টলস্টয়ের মতো রবীন্দ্রনাথও ভূ-স্বামী পরিবার থেকে এসেছেন।
দুজনই অভিজাত পরিবার থেকে এলেও টলস্টয়ের আভিজাত্য ছিল স্বাধীন রাশিয়ার স্বাধীন সমাজ থেকে পাওয়া। আর রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্য ঔপনিবেশিক শাসনের কৃত্রিম সমাজ থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্নতা সেখানে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান তৈরি করেছে। শিলাইদহের কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করলেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই কৃষককে তার জীবনের সমগ্রতা নিয়ে ধরা সম্ভব হয় না। টলস্টয়ের বেলায় আভিজাত্য কোনো সংকট তৈরি করেনি।
কাউন্ট টলস্টয়ের জীবন প্রায় আগাগোড়া কৃষক সংলগ্ন। টলস্টয় পড়লে রুশ কৃষকের নাড়ি নক্ষত্র জানা যায়। অথবা এভাবে বলা যায়, রুশ কৃষককে পেতে হলে যেতে হবে টলস্টয়ের কাছে। হয়ত সে জন্যই তাঁর সাহিত্য কর্মকে লেনিন বলেছেন ‘রুশ বিপ্লবের দর্পণ।’
একদল ‘প্রগতিবাদী’ রবীন্দ্রনাথের জমিদার পরিচয়কে কটাক্ষ করে প্রতিক্রিয়াশীল বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টাও করেছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের কিছু হয়নি, তাদের দৈন্যই প্রকাশ পেয়েছে।
কোনও ক্যাটাগরির নির্দিষ্ট চৌহদ্দিতে শিল্প সাহিত্যকে বিচার করা যায় না বলেই হয়ত রাজতন্ত্রী ‘বালজাক’ ছিলেন কার্লমার্কসের প্রিয় কবি। সমসাময়িক সমাজতন্ত্রী কবিদের চেয়ে তাঁর বেশি মনোযোগ ছিল ইসকিলাস, শেক্সপিয়ার, দান্তে, গ্যেটে, হাইনরিখ হাইনের দিকে। কমিউনিস্ট কবি মায়কোভস্কির চেয়ে অকমিউনিস্ট কবি আলেক্সান্দার পুশকিনের প্রতি লেনিনের পক্ষপাতিত্ব বেশি ছিল।
রবীন্দ্রনাথকেও ক্যাটাগরির শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করে প্রত্যেকে নিজের মতো করে পড়লেই খুঁজে পাওয়া যায় বাঙালির নিজের রবীন্দ্রনাথকে।