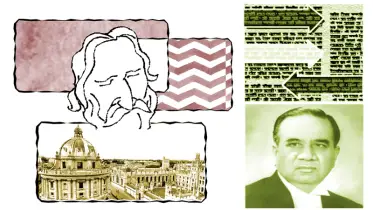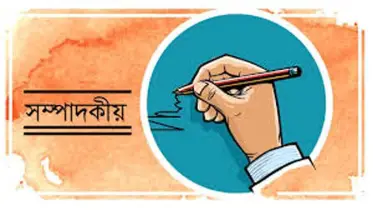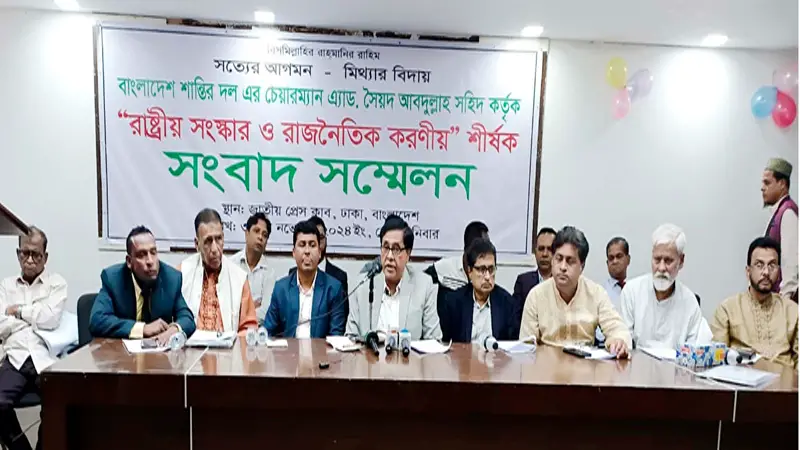
রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাক্সিক্ষত রূপ লাভ করেনি
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে এলেও এখনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাক্সিক্ষত রূপ লাভ করেনি। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হলেও তা কখনই সুসংহত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত দুর্বলতা, নেতৃত্বের সংকট, নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সব মিলিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এক গভীর সংকটে পড়েছে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে আদর্শের জায়গা বরাবরই দুর্বল থেকেছে। রাজনৈতিক দলগুলো নামমাত্র কিছু নীতিকথা প্রচার করলেও বাস্তবিক অর্থে আদর্শিক চর্চা অনেকাংশেই অনুপস্থিত। অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মকা- ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। যার ফলে জাতীয় স্বার্থ প্রায় প্রাধান্য পায় না। দলগুলোর ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এতটাই প্রকট যে, প্রায় সব দলই একক নেতৃত্বনির্ভর হয়ে উঠেছে।
এ অবস্থায় বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না। ফলে নেতৃত্বের জড়তা ও স্থবিরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে। দলের ভেতরে নেতৃত্ব, নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না হলে জনগণের আস্থা অর্জন সম্ভব নয়। আদর্শভিত্তিক রাজনীতির মূল শর্তই হলো দলভিত্তিক গণতন্ত্রের চর্চা। যেখানে মতবিনিময়, সমালোচনার সুযোগ ও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থাকবে। দুঃখজনকভাবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।
নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলেও বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্নবিদ্ধ। অতীতের নির্বাচনে নানা অনিয়ম, ভোট জালিয়াতি, প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ভূমিকা ইত্যাদি কারণে জনগণের মধ্যে নির্বাচনের প্রতি আস্থা প্রায় হারিয়ে গেছে। নির্বাচনের আগে নানা প্রতিশ্রুতি থাকলেও সেগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান নির্বাচন কমিশন বা সাংবিধানিক কাঠামোতেও কিছু মৌলিক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।
কমিশনের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনা মোতায়েন-এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশে রাজনীতির আরেকটি বড় সমস্যা হলো ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা। প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং শত্রু হিসেবে দেখা হয়। যার ফলে গঠনমূলক আলোচনা কিংবা সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় না।
রাজপথে রাজনৈতিক সহিংসতা, পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ, হরতাল- এসব দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। রাজনীতিতে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল মত-পথের মধ্যে ঐক্য স্থাপন জরুরি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংলাপ এবং সহাবস্থান নিশ্চিত না হলে রাজনৈতিক সংস্কার সফল হবে না। জাতীয় ঐক্যের ধারণা যদি বাস্তব রূপ না পায়, তবে সংবিধান বা নীতিমালার সংস্কারও অকার্যকর হয়ে পড়বে।
বাংলাদেশ একটি ধর্মপ্রাণ রাষ্ট্র হলেও সংবিধান অনুযায়ী এটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাজনৈতিক বাস্তবতায় দেখা যায়, প্রায় সব রাজনৈতিক দলই কোনো না কোনোভাবে ধর্মকে ব্যবহার করেছেÑ হোক তা নির্বাচনী প্রচারণায়, জনমত গঠন কিংবা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তি দুর্বল হয়েছে এবং গণতন্ত্রের বিকাশে তৈরি হয়েছে প্রতিবন্ধকতা।
বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর গঠন ও কার্যক্রম অনেক সময় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে খাপ খায় না। আবার শুধু ইসলামপন্থি দলগুলো নয়, মূলধারার দলগুলোও বারবার ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ প্রবণতা বন্ধ না হলে রাজনীতি কখনই আদর্শিক ও প্রগতিশীল ধারায় ফিরতে পারবে না।
রাজনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। বর্তমান বাস্তবতায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের দুরবস্থা, ব্যাপক দুর্নীতি এবং ধনী-গরিবের ব্যাপক বৈষম্য জনগণের মধ্যে চরম হতাশা সৃষ্টি করেছে। এই হতাশা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।
যদি সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো সত্যিকার অর্থে জনগণের আস্থা ফিরে পেতে চায়, তাহলে সুশাসন, জবাবদিহি এবং কার্যকর প্রশাসনের বিকল্প নেই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়াস ব্যর্থ হবে।
রাজনৈতিক সংস্কার কোনো একক কর্মসূচি নয়, এটি একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় দলগুলোর আদর্শিক রূপান্তর, ভেতরে গণতন্ত্র চর্চা, নেতৃত্ব বিকাশ, জনগণের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের উচিত হবে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া। একই সঙ্গে, নাগরিক সমাজ, শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম এবং মিডিয়ারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
তাদের সচেতনতা ও চাপ রাজনৈতিক সংস্কারের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিনের এক সংকটে নিমজ্জিত হলেও, এই সংকট অনতিক্রম্য নয়। সমস্যা যেহেতু বহুস্তরীয়, সমাধানও হওয়া উচিত বহুমাত্রিক।
নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার, রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা, নেতৃত্বের বিকাশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা - সবকিছুর মিলিত প্রয়াসেই সম্ভব একটি টেকসই ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা। তবে এ পথ দীর্ঘ, কণ্টকাকীর্ণ ও ধৈর্যের পরীক্ষা। তবু এই পথেই রয়েছে ভবিষ্যতের আশার আলো।