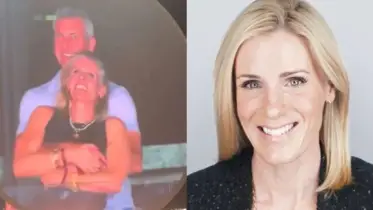রাজশাহী : গোদাগাড়ি উপজেলার প্রত্যান্ত অঞ্চল পানিহার গ্রামে ৮০ বছর আগে এই মাটির ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয় লাইব্রেরি। এটি এখনো বিদ্যমান -জনকণ্ঠ
গল্পটি অনেক পুরানো। আজ থেকে ৮০ বছর আগের গল্পটি একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার। কেনো শহরের গল্প নয়। সবদিক দিয়ে অনুন্নত একটি নিভৃত গ্রামের গল্প। গ্রামটির নাম পানিহার। এ গ্রামের অবস্থান রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায়।
রাজশাহী শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে গোদাগাড়ী উপজেলা সদরের ডাইংপাড়া মোড়। এখান থেকে আরও ১২ কিলোমিটার দূরের গ্রাম আইহাই। বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রায় প্রত্যন্ত এ এলাকা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। আইহাই গ্রামের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু সড়ক পেরিয়ে পৌঁছানো যায় পানিহার গ্রামে। এখন উপজেলা সদর ছাড়াও বিভিন্ন পথ বেয়ে ওই গ্রামে যাওয়া যায়। গত তিন দশকের ব্যবধানে ওই গ্রামের পাশে গড়ে উঠেছে বাজার, দোকান-পাট।
এ গ্রামেই ৮০ বছর আগে ১৯৫৪ সালে মাটির ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি লাইব্রেরি। যখন জেলা শহর রাজশাহী তো দূরের কথা, উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল দুর্গম। রাস্তাঘাট ছিল না। বিদ্যুতের আলো সেতো কল্পনারও অতীত ছিল। অথচ সেই গ্রামে প্রতিষ্ঠা বরা হয় বই সমৃদ্ধ এক লাইব্রেরি। যার নাম ‘পানিহার পাবলিক লাইব্রেরি’।
ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৫ সালেই অনুন্নত প্রান্তিক গ্রামে নিজের ভিটে বাড়িতে লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এনায়েত উল্লাহ মাস্টার নামের একজন শিক্ষানুরাগী। তবে সে সময় তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন কিংবদন্তি আদিবাসী নেতা সাগরাম মাঝি। সাগরাম মাঝি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। পানিহার লাইব্রেরীর পত্তন হয়েছিল মাটির ঘরে। অনেক পরে যদিও পাশেই পাকা ঘর তৈরি হয়। কিন্তু ৮০ বছরের পুরানো সেই মাটির ঘরটি এখনো ব্যবহার হচ্ছে।
সোমবার সকালে সরেজমিন ওই গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, মাটির প্রতিষ্ঠাকালীন ঘরের পাশেই পাকা একতলা ভবন। তিন কক্ষের বারান্দা ওয়ালা এ ভবনে লেখা ‘পানিহার পাবলিক লাইব্রেরি’। প্রতিষ্ঠাকাল দেওয়া আছে ১৯৪৫ আর মঞ্জুরির সাল দেওয়া আছে ১৯৫৪। সামনে দিয়ে সরু পাকা রাস্তা চলে গেছে গ্রামের মাটির বাড়িঘর ভেদ করে। সবুজ ছায়াঢাকা মায়াবি ও স্নিগ্ধ একটি গ্রাম।
লাইব্রেরিটি পরিদর্শনে গিয়ে তালাবদ্ধ পাওয়া যায়। তবে লাইব্রেরির দেওয়ালে লেখা ‘প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নম্বর’। সেটি লাইব্রেরিয়ান মোয়াজ্জেম হোসেনের। ওই নম্বরে কল দিয়ে পরিচয় দিতেই তিনি জানালেন, তার জমিতে ধান রোপণ চলছে। তিনি মাঠে রয়েছেন। আসতে মিনিট বিশেক লাগবে।
কথা অনুযায়ী ২০ মিনিটের মধ্যে মোয়াজ্জেম হোসেন আসতে না পারলেও লাইব্রেরির চাবি নিয়ে যথাসময়ে হাজির আব্দুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি। তিনি এসেই জানালেন, তিনি লাইব্রেরিয়ান মোয়াজ্জেম এর চাচাত ভাই। লাইব্রেরিয়ান মোয়াজ্জেম হোসেনের অনুপস্থিতিতে তিনিই লাইব্রেরি চালু রাখেন। তিনি লাইব্রেরি খুলে দিলেন। শুরুতেই তিনি বললেন, এখন আর তেমন পাঠক আসে না। পাঠকের এখন বড় অভাব। তবুও প্রতিদিন খোলা হয় লাইব্রেরি। মোবাইল আর ইন্টানেটের যুগে বই পড়ার পাঠকের অভাব এখন তবে অনেকে আসেন। পছন্দের বই নিয়ে বাড়িতে গিয়ে পড়েন। সে সব বই জমা দিয়ে আবার নিয়ে যান। এখন এভাবেই কার্যক্রম চলছে এ লাইব্রেরির।
লাইব্রেরি ভেতরে প্রবেশ করতেই নাকে বিঁধলো পুরানো বইয়ের ঘ্রাণ। টেবিল আলমারির থাকে থাকে সাজানো পুরানো বইয়ের ভাণ্ডার। দেওয়ালে লাগানো দেশ বিদেশের মনীষীদের ছবি। আছে রাজনৈতিক নেতাদের ছবিও। এককোনে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা এনায়েত উল্লাহর ছবি। আছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিখ্যাত লেখক, সাহিত্যিকদের বাঁধাই করা ছবি।
আবদুল্লাহ জানালেন, এই লাইব্রেরির সংগ্রহে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার বই। এমন এমন সব দুর্লভ বই ও পত্রিকার সংকলন রয়েছে যা দেশের জাতীয় লাইব্রেরিতে পর্যন্ত নেই বলে দাবি তার। লাইব্রেরির দুটি নতুন বুক সেলফ চোখে পড়লেও বাকি সব আসবাবপত্র যেমন বুক সেলফ সব কাঠের ও প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের। পুরানো বুক শেলফগুলো ও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল।
এনায়েত উল্লাহ মাস্টার লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করলেও শেলফগুলো সে সময় মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, সাঁওতাল, মুন্ডা আদিবাসসহ সব বর্ণ ধর্মের মানুষ নিজ পয়সায় কিনে দিয়েছিলেন। এই লাইব্রেরিটি অসাম্প্রদায়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।
এই লাইব্রেরিতে যারা কাজ করেন, তাঁরা শুরু থেকেই কোনো বেতন পান না। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মনের আনন্দে লাইব্রেরি সামলে রেখেছেন তারা। বিশেষ করে লাইব্ররিয়ান মোয়াজ্জেম হোসেন আন্তরিকতার সঙ্গে আগলে রেখেছেন ঐতিহ্যের এ লাইব্রেরিটি।
প্রাচীন এ লাইব্রেরিতে গেলে যে কারও মন-প্রাণ দুটোই ভরে যাবে, যদি সে বইপ্রেমী হন। ৮০ বছর আগে প্রান্তিক এই গ্রামে এমন একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি জ্ঞানপিপাসার সাক্ষ্য বহন করে আসছে আজও। যেন মাটির ঘরে পুরো জ্ঞানের ভাণ্ডার। জ্ঞান বিকশিত করার ঘরও বলা যায় এ লাইব্রেরিকে।
অনুসন্ধানে জানা যায়, ঐতিহ্যের পানিহার পাবলিক লাইব্রেরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গত শতকের চল্লিশের দশকের মধ্যভাগে। ঠিক ব্রিটিশ শাসনামলের শেষবেলায়। সে সময় অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা প্রত্যন্ত গ্রাম পানিহারসহ আশপাশের অনেক এলাকার মানুষের কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছিল এই লাইব্রেরিটি। তখন বই পাঠে ছিল আগ্রহ। জ্ঞানপিপাসু মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুড়ে আসতেন মাটির ঘরের এই জ্ঞান ভাণ্ডারে। বই পড়তে এসে গ্রামেও থেকে যেতেন। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বলেত ছিল না কিছুই। ছিল শুধু মাইলের পর মাইল হেঁটে চলা পথ।
এ সময় জ্ঞানের আলো ছড়ানো আলোকবর্তিকা হয়ে থাকা এ এ লাইব্রেরিটি তথ্যপ্রযুক্তি আর মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটের যুগে এসে খেই হারাতে বসেছে। বইয়ের প্রতি অনাদর-অবহেলার কারণে আলো ছড়ানো লাইব্রেরিটি দীপ্তি এখন নিভতে বসেছে। পাঠক সংকট, সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে এখানকার সংগ্রহে থাকা হাজারো গ্রন্থ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এনায়েত উল্লাহ মাস্টার ছিলেন এক সমাজহিতৈষী। তিনিই বাড়ির পাশে ২ শতক জমির ওপর ৮০ বছর আগে গড়ে তোলেন এই লাইব্রেরীটি। বর্তমানে আধুনিকতার কোনো ছোঁয়া ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে এটি। তবু কখনো কখনো দুর্লভ বইয়ের টানে অনেক কবি-সাহিত্যিক ও গবেষকরা ছুটে আসেন এখানে।

সরেজমিন দেখা যায়, লাইব্রেরিটির এখন বেহাল অবস্থা। দেখা যায়, টেবিলের ওপর রাখা একটি পুরানো পত্রিকার ফাইল ও কিছু বই উইপোকায় খাচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকালীন আলমারিগুলো ঘুণে খাওয়া। ভেতরে রাখা বইগুলোর অবস্থাও করুণ।
স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা জানান, লাইব্রেরিটির প্রতিষ্ঠাতা এনায়েত উল্লাহর বাবা ছিলেন একজন কৃষক। কৃষক হলেও শিক্ষানুরাগী এ মানুষটি ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর হাইস্কুলে। ওই স্কুল থেকে বাংলা ১৩১৮ সনে এনায়েত উল্লাহ এন্ট্রান্স পাশ করেন। ওই সময়েই স্কুলের লাইব্রেরির সদস্য হন। গ্রামে ফিরে নিজের মতো করে একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন।
এলাকায় ফিরেই এনায়েত উল্লাহ প্রথমে আইহাই গ্রামে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মাসিক ১৫ টাকা বেতনে নিয়োগ করেন শিক্ষক। বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে থাকেন। সে সময় তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য বই আনতেন কলকাতা থেকে।
ওই সময় পাঠ্যবইয়ের বাইরে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থেকে অল্প অল্প করে বাইরের বইও সংগ্রহ করতে শুরু করেন। বইয়ের মোটামুটি একটা সংগ্রহ দাঁড়ালে ১৯৪৫ সালে মাটির ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন জ্ঞানের ভান্ডার লাইব্রেরিটি।
সেই সময় লাইব্রেরির জন্য আরও বই সংগ্রহের জন্য এনায়েত উল্লাহ গ্রামের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। একই সময়ে এ এলাকা থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন তার সহপাঠী সাগরাম মাঝি। লাইব্রেরিটিকে সাজিয়ে তুলতে তিনিও সঙ্গী হন এনায়েত উল্লাহর। লাইব্রেরিয়ান মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, লাইব্রেরিতে বিভিন্ন সাময়িকী, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সিনেমা, অনুবাদ, ধর্ম-বিজ্ঞান, কবিতার বই, গোয়েন্দা উপন্যাস এবং উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এখন প্রায় ১০ হাজার বই আছে। ২০টি আলমারিতে রাখা আছে এগুলো। পাঠকদের জন্য আছে একাধিক টেবিল ও পর্যাপ্ত চেয়ার। গ্রন্থাগারটি ঘুরে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসিমউদ্দীন ও আবুল মনসুর আহমদ থেকে শুরু করে হুমায়ূন আহমেদ-সবার বই আছে। রয়েছে কলকাতার রজনীকান্ত দাস সম্পাদিত শনিবারের চিঠি, মাসিক মোহাম্মদী, মাহে নও, জয়তী, নতুন দিন, দৈনিক বাংলাসহ অনেক সাময়িকী। আগে এখানে নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা রাখা হলেও এখন অর্থ সংকটে কোনো সংবাদ পত্র রাখা সম্ভব হয় না।
ইতিহাস ঘেটে জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পল্লীকবি জসিমউদ্দীন, কবি বন্দে আলী মিয়া ও উত্তরবাংলার চারণকবি আব্দুল মান্নানসহ আরও অনেক গুণীব্যক্তি এই লাইব্রেরি ঘুরে গেছেন।
এখন একটি পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে চলে পানিহার পাবলিক লাইব্রেরি। বর্তমান এটির সভাপতি আবদুল মতিন। তিনি স্থানীয় হাইস্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক। তার স্কুলে গিয়ে পাওয়া যায় তাকে। তিনি জানান, পানিহার লাইব্রেরি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৮ সালে মঞ্জুরি পায়। সে সময় এর পরিবর্তিত নাম হয় ‘পানিহার পাবলিক লাইব্রেরি’। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হতো এটি। বছরে অনুদান আসতো ৫০০ টাকা। ১৯৮০ সালে লাইব্রেরিটিকে জেলা প্রশাসকের অধীনে আনা হয়। ২০০০ সালে জেলা প্রশাসক গ্রন্থাগারটিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অধীনে হস্তান্তরের পর আনুদান আসা বন্ধ হয়ে যায়।
আবদুল মতিন বলেন, লাইব্রেরির জন্য আগে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনিয়মিতভাবে কিছু অর্থ পাওয়া যেত। তবে ২০১৭ সালের পর থেকে আবেদন করেও কোনো অনুদান পাওয়া যায়নি। আর নব্বইয়ের দশকে মাটির ঘরের পাশে পাকা ঘরটি করে দেয় উপজেলা পরিষদ।
আবদুল মতিন বলেন, এখন আর আগের মত পাঠক আসে না এখানে। লাইব্রেরিটি বাঁচিয়ে রাখার মতো মানুষও কমে আসছে।
এ লাইব্রেরিটি একাধিকবার পরিদর্শন করেছেন রাজশাহী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ মুহা. হবিবুর রহমান। তিনি বলেন, এ লাইব্রেরিটি নিশ্চয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। মানুষকে আলোকিত করার উৎস। তিনি বলেন, এখানে বইয়ের যে সংগ্রহ তা অন্য কোনো লাইব্রেরিতে হয়ত নাই। তিনি বলেন, এত পুরানো বই আর পাওয়া যাবে না। সেজন্য আর্কাইভ করা উচিত। স্ক্যান করেও বইগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব।
জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরণে মশিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন পাঠাগার
একটি পাঠাগার ঘিরে একটি গ্রাম যে শিক্ষা-দীক্ষায় বদলে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত রেখেছে মশিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন পাঠাগার নামের একটি প্রতিষ্ঠান। গ্রামের ছায়ায় বেড়ে ওঠা একদল শিক্ষিত তরুণের উদ্যমী কার্যক্রমের ফল এ পাঠাগার। সমাজ সংস্কারে একধাপ এগিয়ে আসা এ গ্রামের নাম মশিদপুর। এ গ্রামটির অবস্থান উত্তরের নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায়।
একদল যুবকের গড়ে তোলা একটি সমিতির মাধ্যমে পুরো গ্রামছাড়াও আশেপাশের গ্রামে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে চলেছে এ পাঠাগার। যা গ্রামে শিক্ষার আলো বিচ্ছুরণের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নিভৃত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত এ পাঠাগারের কার্যক্রম এখন সাড়া ফেলেছে আশেপাশের গ্রামে। পাঠাগারের মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষায় অবদানের জন্য গত সোমবার (১৪ জুলাই’২৫) গুনিজন সংবর্ধনা পেয়েছেন এ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা আবদুর রাজ্জাক। আবদুর রাজ্জাক একজন শিক্ষানুরাগী, নজরুল গবেষক ও সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক। রাজশাহী শহরের একটি সনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরির পাশাপাশি সুযোগ পেলেও ছাটে যান গ্রামে। শিক্ষার বিচ্ছুরণ ফোটাতে নানামুখি কার্যক্রম চালিয়ে যান বছরব্যাপী।
আবদুর রাজ্জাক জানান, তাদের গড়ে তোলা মসিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন পাঠাগারে ৭৫০ এর অধিক বই রয়েছে। সপ্তাহের ৫ দিন বিকেল বেলা খোলা হয় এ পাঠাগার। এ পাঠাগারে নিয়মিত ১৮ থেকে ২৫ জন শিক্ষাথী আসে বই পড়তে। শুধু শিক্ষার্থীরা নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষও অবসর পেলেই ছুটে আসেন বই পড়তে।
আবদুর রাজ্জাক জানান, বইপড়া, পত্রিকা পড়া ছাড়াও সকল জাতীয় দিবসসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন করা হয় গুরুত্ব বিবেচনায়। বইপাঠ প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা হয়। সচেতনতা তৈরিতে পাঠকসমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ করা হয়।
জেলার মান্দা উপজেলার নিভৃত ছায়াঢাকা গ্রাম মশিদপুর। অন্যান্য গ্রামের মতো এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। ক্ষেত-খামার নিয়েই তাদের বছরব্যাপী ব্যস্ততা। গ্রামের মেঠো পথ অনেকটায় আঁকাবাকা হলেও ওই গ্রামের প্রতিটি মানুষ সহজ-সরল। প্যাচ বুঝে না। তবে শিক্ষার ব্যাপারে অনেক সচেতন।
বইয়ের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর অনন্য এক আয়োজন করা হয়। এ গ্রাম থেকে উচ্চ শিক্ষায় বেরিয়ে আসা একদল যুবকের অনুপ্রেরণায় প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে বইমেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে বই মেলার পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তার, স্কুল থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ছাড়াও মুলত শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ বই মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে দেশের শিক্ষাবিদরাও অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান গ্রামের মানুষকে। প্রথমে সমিতি পরে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ গ্রামকে জাগ্রত করে তোলা হয়েছে।
২০১০ সাল থেকে এভাবেই গ্রামের মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রস্ফুটিত করে তুলতে প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ‘মশিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি’র পর মশিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ব্যানারে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে ইমাজউদ্দিন মেমোরিয়াল বৃত্তি। প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে তুলে দেওয়া হয় শিক্ষাবৃত্তি। শুধু শিক্ষাবৃত্তিই নয়, দিনভর খাওয়া দাওয়া আর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দেওয়া হয় চিকিৎসা সেবাও। এতকিছুর সব আয়োজন করা হয় মুলক পাঠাগার ঘিরে।
রাজশাহীর তানোর ও নওগাঁর মান্দা আর নিয়ামতপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী তিন উপজেলার সন্ধিস্থল মান্দার চৌবাড়িয়া। সেখান থেকে আরও কিছুদূর ভেতরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত একটি গ্রাম মশিদপুর। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা আর শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর এ গ্রামে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় বইমেলা। সঙ্গে নানা আয়োজন।
প্রতি বছরের একদিন বইয়ের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এলেই আয়োজন করা হয় এ গ্রামে। বই পড়া, বই কেনা ও শিক্ষার প্রতি প্রজন্মকে আগ্রহী করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এ মেলার আয়োজন করা হয়।
নিভৃত পল্লীর কৃষি অধ্যুষিত এ গ্রামে শিক্ষা বিস্তারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক। তিনি জানান, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলার তিন উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম মশিদপুর ছিল অবহেলিত। এখানে অশিক্ষার হার ছিল অনেক বেশী। স্কুল থাকলেও নানা কারণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা ছিল অনেক বেশি। এ কারণে এ গ্রামে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনিই মূলত গড়ে তোলেন ‘মশিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি’। এ সমিতির ব্যানারেই শিক্ষার প্রসারে নানা কার্যক্রম চলে বছরজুড়েই। পরে ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ‘মশিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন পাঠাগার।
তিনি বলেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে বইয়ের নীবিড় সম্পর্ক স্থাপন, মেধাবীদের শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে নিয়ে আসা, স্কুলে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ আর গ্রামের শিশুদের স্কুলমুখী করার লক্ষ্য নিয়ে মশিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি বইমেলাসহ নানা আয়োজন করে আসছে। প্রথমদিকে তেমন সাড়া না পেলেও এখন এলাকায় দারুণভাবে সাড়া ফেলেছে।
মামুন-অর-রশিদ, রাজশাহী
পুস্তকালয় থেকে
সাধারণ গ্রস্থাগার
বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগারটিও রাজশাহীতে রয়েছে। এটির নাম রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারের আদি নাম ছিল রাজশাহী সাধারণ পুস্তকালয়। ১৯৭৫ সালের গঠনতন্ত্র সংশোধনীর মাধ্যমে নামকরণ হয় রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার। হাজারো দুষ্প্রাপ্য বই সমৃদ্ধ এ গ্রন্থাগারটি আধুনিতার নামে ভেঙে ফেলা হয়েছে। ২০১৮ সালে গ্রন্থাগারের আদি ভবন ভেঙে মেগা বাজেটে গ্রস্থাগার কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হলেও তা গত সাত বছরেও আলোর মুখ দেখেনি।
রাজশাহীর এ গ্রন্থাগারটি ছিল ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের। দিঘাপাতিয়ার জমিদার রাজা প্রমদা নাথ রায়ের দান করা জমিতে কাশিমপুরের জমিদার রায় বাহাদুর কেদার নাথ প্রসন্ন লাহিড়ী কর্তৃক ১৮৮৪ সালে আনুষ্ঠানেকভাবে যাত্রা শুরু করলেও প্রকৃত সূচনাকাল ছিল আরো আগের। রাজশাহী নগরীর মিয়াপাড়ায় অবস্থিত বলে এটিকে ‘মিয়াপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার’ বলেই চেনেন অনেকে। এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রানী ভবানীর বংশধর রাজা আনন্দনাথ।
ইতিহাস ঘেটে জানা যায়, ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও এর আগে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম উইলসন হান্টার প্রণীত স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট বইতে এই লাইব্রেরির কথা বলা হয়েছে। হান্টারের দেয়া তথ্য মতে ১৮৭১-৭২ সালে এই লাইব্রেরিতে বই ছিল মাত্র ৩ হাজার ২৪৭টি এবং সাময়িকী ছিল ছয়টি। এ সময় পাঠক ছিল নয়জন। এর মধ্যে ছয়জন ছিল ইংরেজ। রাজা আনন্দ রায়ের পরে তাঁর ছেলে রাজা চন্দ্র রায় বছরে ২০ পাউন্ড বা ২০০ টাকা অনুদান দিতেন। এ গ্রন্থাগারটি আধুনিক লাইব্রেরি কমপ্লেক্সে রূপ দিতে প্রাচীন ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। এটির জন্য রাজশাহী সিটি করপোরেশন বড় বাজেট বরাদ্দ করে। তবে এটি নির্মাণের শুরুতেই পাইলিংয়ের শেষ হয়ে যায় বরাদ্দ অর্থ। ফলে আটকে যায় এটির নির্মাণ কাজ।
অর্থ সংকটের কারণে এটির আংশিক নির্মাণের পর রাজশাহী সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে ভবন নির্মাণের কিছু অংশ সম্পন্ন করে জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও নতুন করে কার্যক্রম চালু হয়নি। তাই এখন অনেকে ভুলতে বসেছে এ গ্রন্থাগারের নাম। রাজশাহীর সচেতন মহল মনে করেন, এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম দ্রুত চালু করা জরুরি।

জানা গেছে, রাজশাহী সিটি করপোরেশন ৩ কোটি ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রন্থাগারটির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন শুরু করে। এই প্রকল্পের অর্থায়ন করে ভারত সরকার। ‘সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’-এর আওতায় নগরীর মিয়াপাড়ায় এই গ্রন্থাগার নির্মাণ করা হয়। যদিও শুরুতে এখানে আধুনিক গ্রন্থাগারসহ একটি ৩০০ আসনের অডিটোরিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল, তা অর্থের অভাবে বাস্তবায়ন হয়নি।
নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু থেকেই জটিলতা ছিল। ২০১৬ সালে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের পর ২০১৮ সালে পুরানো ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। দায়সারাভাবে কাজ করে সম্প্রতি এটির চাবি জেলা প্রশাসনে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে কার্যক্রম কিছুই শুরু হয়নি। এখনো পর্যন্ত রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন ভবনে রাখা বইগুলো স্থানান্তর করা হয়নি। লাইব্রেরির জন্য বরাদ্দ ভবনে কেবল পাঠাগার অংশ নির্মাণ সম্পন্ন হলেও, অডিটোরিয়ামসহ অন্যান্য অবকাঠামো বাদ পড়ে গেছে। এতে একদিকে যেমন আয়ের উৎস তৈরি হয়নি, অন্যদিকে পাঠকদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাও নিশ্চিত হয়নি।
বুধবার সকালে সেখানে গিয়ে পাওয়া গেলো মো. শাহীন আলম নামের এক ব্যক্তি। তিনি এটির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে। তার ভাষ্য তিনি ৩৬০০ টাকা করে মাসিক বেতন পেতেন। তবে গত ১৫ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। তিনি মূলত এ গ্রন্থাগার এখন দেখভাল করছেন।
তিনি বলেন, এখনো চালু হয়নি এটি। বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয় নি। তাই রাত হলেই এখাকার জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে। জানালার থাই গ্লাস পর্যন্ত চুরি হয়ে গেছে কার্যক্রম চালুর আগেই। সম্প্রতি এ গ্রন্থাগার চালুর জন্য একটি এডহক কমিটি গঠন করে দিয়েছেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক। এডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দয়িত্ব পালন করছেন রাজশাহী পুলিশ লাইনন্স শহীদ মামুন মাহমুদ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ গোলাম মওলা। তিনি বলেন, এ গ্রন্থাগারটি রাজশাহীবাসীর কাছে অপরিসীম। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি ছিল উত্তরাঞ্চলের বিদ্যাচর্চা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু।
তিনি বলেন, কিছুদিন হলো তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিমধ্যে মিটিংও করেছেন। তিনি বলেন, ভবন নির্মাণ অসমাপ্ত রয়েছে। তারপরেও যেটুকু পাওয়া গেছে সেখানেই কার্যক্রম শুরু করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সরেজমিন গিয়ে এ ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গ্রন্থাগারে কোনো বই-পুস্তক পাওয়া যায় নি। কয়েকটি পুরনো টেবিল ও ভাঙ্গাচোর চেয়ার দেখা যায়।
প্যানেল/মো.