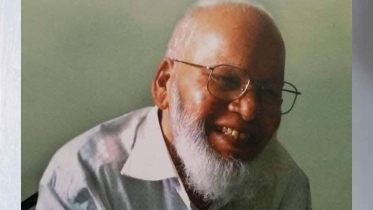রাজীব সরকার
নজরুলের প্রবন্ধসাহিত্য

মাত্র বাইশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে বাংলা সাহিত্যকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন নজরুল। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, সঙ্গীতের বর্ণিল জগতে বহুমাত্রিকতার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর জীবনদর্শনের প্রধান প্রবণতা ছিল উচ্ছ্বাস। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনকে রাঙিয়ে তুলেছিলেন তিনি। উচ্ছ্বাসে অনেক সময় আবেগ পরিমিতবোধকে ছাড়িয়ে যায়, যুক্তি হয়ে পড়ে গৌণ। চিরউচ্ছ্বসিত সাহিত্যিক নজরুলের ভিন্নমাত্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তায়। পরিমিত আবেগ ও পেশিবহুল যুক্তির সমন¦য়ে গভীর মননশীল এক ব্যক্তির দেখা মেলে সেখানে।
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ একটি প্রতিক্রিয়াজনিত রচনা। মার্কিন সংবাদপত্র ‘ঘবি ণড়ৎশ ঐবৎধষফ’ এ জনৈক লেখক তুর্কদের সম্বন্ধে যে বিবরণ দেন এর উপর ভিত্তি করে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে তুর্কী রমণীগণ সুন্দরী নন। এর প্রতিবাদস্বরূপ ‘সওগাত’ পত্রিকায় ‘তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি উপরোক্ত মন্তব্যের অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং তুর্কী রমণীর অনিন্দ্যরূপ সম্পর্কে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন। পরের বছর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৭ সংখ্যায় নজরুলের এই তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়- ‘জীবনবিজ্ঞান’, ‘জননীদের প্রতি’ ও ‘পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব’। এগুলো ‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি ইংরেজী প্রবন্ধের ভাবানুবাদ-মৌলিক রচনা নয়।
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধের শিরোনাম ‘উদ্বোধন’। এটি ‘বকুল’ পত্রিকার আষাঢ় ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটিই পরে ‘জাগরণী’ নামে তাঁর ‘যুগবাণী’ প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি শুরু হয় পল্লী প্রান্তরে মেঠো গানের সহজ সুরে জেগে ওঠার জন্য বকুলকে আহ্বান জানিয়ে। সমাপ্তি ঘটে শাশ^ত বাঙালীকে জেগে ওঠার ডাক দিয়ে-
‘জাগো বকুল, জাগো! তুমি যেখানে ছোট, সেই পল্লীতেই আছে আমাদের সত্যিকার বাঙলা-বাঙালীর আসল প্রাণ। আমাদের এ শাশ^ত বাঙালীর সুষুপ্ত, ঘুমে ভরা অলস প্রাণ জাগিয়ে তোল তোমার জাগরণের সোনার কাঠি দিয়ে।.....জাগো, বকুল জাগো! যৌবনের জয়টিকা নিয়ে!!!’
প্রথম বিশ^যুদ্ধ পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিকামী, শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রবল কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল নজরুলের রচনা। সাম্যবাদী নজরুলের চেতনায় ছাপ রেখে যায় সমকালীন আন্তর্জাতিক ঘটনা। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে নবজাগরণ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকা-, ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ^রে বোমা কারখানার খবর, ১৯২৯ সালে ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, ১৯৩০ সালে সূর্যসেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা নজরুলের বিদ্রোহীসত্তাকে তীব্রভাবে আলোড়িত করে। পাশাপাশি দেশের দারিদ্র্য, জাতিভেদ, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা ও নারীর অধিকারহীনতা তাকে বিক্ষুব্ধ করে। এরই প্রতিবাদে রচিত হয় নজরুলের বারুদগন্ধী প্রবন্ধসমূহ। এসব প্রবন্ধে তৎকালীন উত্তাল সময়ের জাজ্জ্বল্যমান চিত্র ফুটে ওঠেছে।
প্রাবন্ধিক নজরুলের বিকাশে তাঁর সাংবাদিকসত্তা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। সাংবাদিক জীবনে নজরুল ‘নবযুগ’, ‘ধূমকেতু’, ‘গণবাণী’ ও ‘লাঙল’ পত্রিকায় যেসব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এগুলোই পরিমার্জিত হয়ে পরবর্তীকালে তাঁর চারটি প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়। এগুলো হচ্ছে- যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৬) এবং দুর্দিনেরযাত্রী (১৯২৬)। নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ ‘যুগবাণী’ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় এর গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ বৈশিষ্ট্যের জন্য। বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ ‘নবযুগ’ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নবযুগের সূচনা ঘটেছিল এর উজ্জ্বল স্মারক। বিশের দশকে ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য মুক্তিকামী দেশের সংগ্রামী উম্মাদনার এক বিশ^স্ত দলিল এই প্রবন্ধটি। উল্লেখ্য, এর সামান্য কয়েক বছর আগেই রুশ দেশে ঘটে গেছে বিশে^র প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যার রক্তিম বিপ্লবী চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে বিশ^ব্যাপী মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী মন। নজরুলের ভাষায়-
‘আজ রক্ত প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নবপ্রভাতী ধরিয়াছে ‘পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।’ এ সুর নবযুগের। সর্বনাশা বাঁশীর সুর রুশিয়া শুনিয়াছে আয়ারল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরও অনেক শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান,- জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃৃৃৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।’
‘নবযুগ’ প্রবন্ধে রুশ বিপ্লব, আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতার সংগ্রাম, সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলামুক্ত নতুন তুরস্ক এবং পরাধীন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে একসূত্রে নজরুল গেঁথেছেন। এভাবে সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবনের শুরু থেকেই নজরুল স্বদেশী ও আন্তর্জাতিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এসব ভিন্ন দেশের সংগ্রামের প্রকৃতি এক রকম ছিল না, কিন্তু মানুষের মুক্তি যেখানে লক্ষ্য, সেখানে নজরুল কোন বিভেদ দেখেননি, বিরোধ দেখেননি কাস্তে, হাতুড়ি আর অর্ধচন্দ্র প্রতীকের মধ্যে।
স্বদেশী উদ্দীপনামূলক অন্যান্য রাজনৈতিক প্রবন্ধের কয়েকটি হলÑ‘আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল’, ‘তুবড়ী বাঁশীর ডাক’, ‘মোরা সবাই রাজা’ প্রভৃতি। এগুলোর প্রতিটিতে অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত তথা পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্যে এগিয়ে আসার জন্য যৌবনদীপ্ত তরুণদের প্রতি আবেগে টই-টুম্বর শব্দালঙ্কারঝংকৃত ভাষায় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। নবযুগ পত্রিকায় কয়লা শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে ‘ধর্মঘট’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখলেন-
‘এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়। কেননা ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগাদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে, এ দেশেও মহত্ত্বর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং, শ্রমজীবীদলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডেমোক্র্যাসির জাগরণও এদেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।’
‘নবযুগ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ছুঁৎমার্গ’ প্রবন্ধে নজরুল জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রধান কারণরূপে নির্দেশ করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখলেন-
‘আমাদের গভীর বিশ^স যে হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়াছুইয়ের জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোন ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোন ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম কখনও এত সংকীর্ণ অনুদার হইতে পারে না।’
এই শ্রেণীর অন্যান্য প্রবন্ধেও এমন তেজস্বী ভাষা ও আবেগময় অভিব্যক্তি দৃশ্যমান। অন্যান্য প্রবন্ধগুলো হলো ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে’, ‘তিলকের মৃত্যুতে শোক’, ‘গেছে দেশ দুঃখ নাই/আবার তোরা মানুষ হ’ প্রভৃতি।পরাধীন ভারতের ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিপ্রতীপে জাতীয় শিক্ষা প্রদানের একটি কার্যক্রম ও আন্দোলন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রশ্রয়ে আগেই শুরু হয়েছিল। সে সম্বন্ধে তিনি দেশবাসীকে সজাগ করে ‘জাতীয় শিক্ষা’ প্রবন্ধে লিখলেন-
‘জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাদাতা কর্তাদের সম্বন্ধে আমরা আজ পর্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা খারাপ বলিতে আমাদেরই বক্ষে বাজিতেছে। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিয়া ভ-ামি দিয়া কখনও মঙ্গল উৎসবের কল্যাণ প্রদীপ জ্বলিবে না- পবিত্রতার নামে এমন জুয়াচুরিকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের ভবিষ্যত একদম ফর্সা।’
অনুরূপভাবে ‘জাতীয় বিশ^বিদ্যালয়’ শীর্ষক রচনায় তিনি জাতীয় বিদ্যালয়গুলোর স্ট্যান্ডার্ড ও পাঠক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এবং জাতীয় বিদ্যালয়গুলোর নেতিবাচক সমালোচনা না করে তিনি ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললেনÑ
‘আমরা চাই আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হোক যাহা আমাদের জীবন শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ মন দুইকেই পুষ্ট করে তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।... এই দুই শক্তিকে প্রাণ শক্তি আর কর্ম শক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ^বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।’
সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে নজরুলের জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ‘বর্তমান বিশ^সাহিত্য’ ও ‘জনসাহিত্য’ প্রবন্ধে। শিল্পের জন্য শিল্প বা কলাকৈবল্যবাদের ঘোরবিরোধী ছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে তিরিশের সাহিত্যান্দোলনের মূল সুর ছিল কর্লাকেবল্যবাদ। ‘বর্তমান বিশ^সাহিত্য’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- ‘বর্তমান বিশ^সাহিত্যের দিকে একটি ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলীর ঝশুষধৎশ - এর মত, মিল্টনের ইরৎফং ড়ভ চধৎধফরংব- এর মতো এই ধূলি মলিন পৃথিবীর উর্ধে উঠে স্বর্গের সাধনা করে, তার চরণ কখনও ধরার মাটি স্পর্শ করে না; কেবলি উর্ধে- আরও উর্ধে উঠে স্বপন লোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।...
আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে-অন্ধকার নিশিতে, ভয়ের রাতে বিহ্বলশিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে- তরুলতা যেমন করে সহ¯্র শিকড় দিয়ে ধরণী মাতাকে ধরে থাকে তেমনি ঘরে। এইখানে সে মাটির দুলাল।’
এ প্রবন্ধে সহজ সুন্দর চিত্রকল্প ও উপমার সাহায্যে বিশ^সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজী, ফারসী, রুশীয়, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ও নরওয়েজিয়ান সাহিত্যের প্রতি নজরুলের আগ্রহ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে অনায়াসে উপস্থাপন করেছেন তিনি।
‘জনসাহিত্য’ প্রবন্ধটির সুর বিশিষ্ট ও বাস্তবমুখী; তাই একালেও প্রাসঙ্গিক। জনগণের সাহিত্যের প্রকৃতি কী রকম হওয়া বাঞ্জনীয়, সে ব্যাপারেই যেন বহুবিচিত্র -অভিজ্ঞতায় -সমৃদ্ধ কবির একান্ত উপলব্ধি এ রচনাটি। রবীন্দ্রনাথ কবি সাহিত্যিক-শিল্পীদের ‘সৌখিন মজদুরী’-কে নিন্দা করেছিলেন। এ প্রবন্ধে নজরুলও তাই করেছেন-
‘জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের একটি মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এর সমাধানও জনসাহিত্যের একটা দিক।... যাঁদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সেখান থেকেই তাঁদের সাহিত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই।....
জনগণের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। তারা আত্মীয়ের গালি সহ্য করতে পারে, কিন্তু অনাত্মীয়ের মধুর বুলিকে গ্রাহ্য করে না।......
আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজ-নীতি সবই টবের গাছ। মাটির সঙ্গে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জন-সাহিত্যের জন্য জনগণের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কি করে চলে?’
নজরুলের শাণিত প্রবন্ধ ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে ধর্মীয় কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। মানবতাবাদী নজরুল সমগ্র সাহিত্যকর্মেই ধর্মের নামে হানাহানি, জাতের নামে বজ্জাতিকে ঘৃণা করেছেন। ‘আমার পথ’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন-
‘ধূমকেতু’ কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোন হিংসার দুশমনীর ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ^াস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনও অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।’
ব্যঙ্গ বিদ্রƒপের কশাঘাতেও নজরুলের প্রবন্ধ অসামান্যতা অর্জন করেছে। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় ‘কামাল’ নামে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি আচারস্বর্বস্ব ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেন-
‘দাড়ি রেখে গোস্ত খেয়ে নামাজ রোজা করে যে খেলাফত উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না তা সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল, তা না হলে সে এতদিন আমাদের বাংলার কাছা খোলা মোল্লাদের মতন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কাছা না খুলে কাবার দিকে মুখ করে হর্দম উঠবোস শুরু করে দিত। ...ও সব ধর্মের ভ-ামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না, ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার, দাড়িও নয়, নামাজ রোজাও নয়।....।’
এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে ‘বাঙালীর ব্যবসাদারী’, ‘রোজ কেয়ামতের দিন’, ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’- এই রচনাগুলো অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় উন্মাদনাকে তীব্র শ্লেষে ক্ষতবিক্ষত করেছেন নজরুল ‘মন্দির মসজিদ’ প্রবন্ধে। তৎকালীন ভারতবর্ষে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের রক্তপিপাসু দ্বন্দ্বের প্রতি নজরুলের ক্ষোভ ঝরে পড়েছে-
‘মারো শালা যবনদের! মারো শালা কাফেরদের! আবার হিন্দু মুসলমান কা- বাঁধিয়া গিয়াছে । প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ আল্লাহ এবং মা কালীর ‘প্রেস্টিজ’ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম- তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে- ‘বাবা গো, মাগো!’
ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ডামাডোলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কয়েক বছর যেতে না যেতেই বাঙালী মুসলমানের মোহভঙ্গ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এই জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। ষাটের দশকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত উত্থান ঘটে এবং এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। ‘জয় বাংলা’ মন্ত্রে মুখরিত হয়েছিল মুক্তিপিয়াসী বাঙালী। এই মন্ত্রের উদগাতা নজরুল। বাংলা ও বাঙালীত্বের জয় কামনা করে ‘বাঙালীর বাংলা’ প্রবন্ধে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন-
‘বাংলা বাঙালীর হোক! বাঙালীর জয় হোক! বাঙালীর জয় হোক।’
যুক্তি, চিন্তা আর বিচারের সমন্বয়ে সার্থক প্রবন্ধ গড়ে ওঠে। নজরুলের প্রবন্ধে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে গেছে মাত্রাতিরিক্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস। প্রতিবাদী ও আক্রমণাত্মক ভাষা, উপমা ও অলঙ্কারের কারণে তার বক্তব্য একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে অশান্ত, উত্তেজনাময় ও গতিশীল। এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। তবে ‘আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচানো’র জন্য এই ভাষা কার্যকর হয়েছে। এখানেই নজরুলের প্রবন্ধের সার্থকতা।