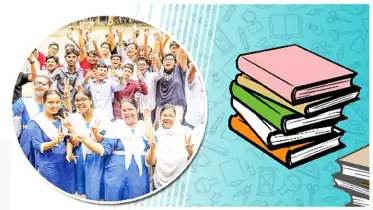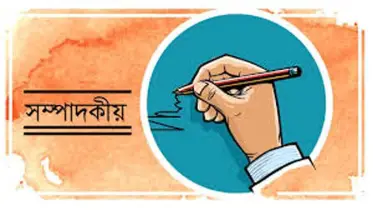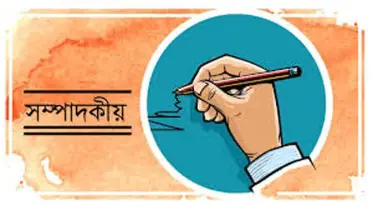আম বাংলাদেশের প্রধান ফল হলেও কাঁঠাল জাতীয় ফল হিসেবে বিবেচিত। প্রতি বছর আমের মৌসুমকে ঘিরে আমচাষি ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে সরকারকে নানা নীতি-পরিকল্পনা নিতে দেখা যায়, আর ভোক্তাদের জন্য সেসব নীতি বেশ জোরেশোরে প্রচার করা হয় গণমাধ্যমে যার মধ্যে আছে আমের উৎপাদন বাড়ানো, যত্নসহকারে বাগানের পরিচর্যা, গাছে সময়মতো স্প্রে করা, হার্ভেস্টিং, ফল সংরক্ষণ, ভেজালমুক্তভাবে বাজারজাতকরণ, বিদেশে রপ্তানিকরণ ইত্যাদি। আমচাষ লাভজনক হওয়ায় অনেক কৃষক শস্যদানা আবাদ বাদ দিয়ে ফসলি জমিতে মৌসুমি ও বারোমাসি আম চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, যা অর্থনীতির জন্য সুখবর।
বাংলার প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে আধুনিক কৃষিনির্ভর অর্থনীতি পর্যন্ত, আম এক অদ্ভুত ধারাবাহিকতায় আমাদের জীবন, সংস্কৃতি ও কৃষিতে গেঁথে আছে। শুধু স্বাদের জন্য নয়, আম আমাদের কাছে রীতিমতো এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিশ্ব ইতিহাস ঘেঁটেও আমের অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালে যখন আলেকজান্ডার সিন্ধু উপত্যকায় পা রাখেন, তখনই তিনি প্রথম দেখেন আমের বাগান। ষষ্ঠ শতকে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণে আসেন, তিনিও আমের স্বাদে মুগ্ধ হয়ে দেশে ফেরার আগে আম পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের শাহবাগের দাঁড়ভাঙা এলাকায় এক লাখ আমগাছ রোপণের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন সুবিশাল আমবাগান যার ধারাবাহিকতা এখনো টিকে আছে।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে দেশের বিভিন্ন জেলায় ২ লাখ ২৫ হাজার ৩৪ হেক্টর জমিতে আমবাগান রয়েছে। এ বছর ২৭ লাখ ৩৫ হাজার টন আম উৎপাদনের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে আম উৎপাদনের পরিমাণ ২৮ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মোট উৎপাদনের মধ্যে রাজশাহী বিভাগের চার জেলা রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোরে প্রায় ১৩ লাখ ৫৫ হাজার টন আম উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন কৃষিসংশ্লিষ্টরা। এবার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৫ জুন থেকে আম্রপালি ও ফজলি, ৫ জুলাই থেকে বারি আম-৪, ১০ জুলাই থেকে আশ্বিনা, ১৫ জুলাই থেকে গৌড়মতী সংগ্রহ করা যাবে। এ ছাড়া কাটিমন ও বারি আম-১১ সারা বছরই পাকা সাপেক্ষ পাড়া যাবে। কিন্তু অতিরিক্ত গরমে এবার একসঙ্গে সব জাতের আম পেকে গেছে। ঈদের ছুটিতে বাজারে আমের সরবরাহ হলেও পর্যাপ্ত ক্রেতা ছিল না। এতে বাজারে চাহিদা কমে দরপতন হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানান, ঢাকা ও অন্য বড় শহরে চাহিদা কম থাকায় অনেক পাইকারই আমের চাষের এলাকায় যাননি। এদিকে নওগাঁর সাপাহারের আম হাটে প্রতি মণ হিমসাগর ১৪০০-১৬০০ টাকা, ল্যাংড়া ১২০০-১৫০০, নাকফজলি ১৩০০-১৮০০, ব্যানানা ম্যাঙ্গো ৩৫০০-৪২০০, হাঁড়িভাঙা ১৫০০-২৫০০ এবং আম্রপালি ১৮০০-৩৫০০ টাকা মণ বিক্রি হয়।
নওগাঁর সাপাহারের ওড়নপুর গ্রামের আমচাষি মাহমুদুর রহমান বলেন, এ বছর আমের দাম খুবই কম। গত বছর এই বাগানের আম প্রতি মণ বিক্রি করেছি ৪২০০-৪৫০০ টাকা। এবার বিক্রি করছি ২০০০-২৫০০ টাকা। যে দামে আম বিক্রি করলাম, তাতে খরচও উঠবে না। সাপাহার হাটে আম বিক্রি করতে আসা পত্নীতলার আমচাষি অজি উল্যাহ জানান, তিনি ১০ বিঘা জমি বর্গা নিয়ে আম্রপালির বাগান করেছেন। দাম গত বছরের তুলনায় অর্ধেক। এটা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজি। নওগাঁর বদলগাছি এলাকার চাষি নুরুল ইসলাম বলেন, এ এলাকার বিখ্যাত ফজলি আমের মণ যাচ্ছে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা পাইকারি, যা গত বছরের চেয়ে প্রায় ৬০০ টাকা কম। তিনি বলেন, এবার ঈদের কারণে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। লম্বা ছুটিতে শহরের মানুষ গ্রামে থেকেছে। ফলে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর এলাকায় আম পাঠানো যায়নি, চাহিদাও ছিল না। তখন আম পেকেছে, নষ্ট হওয়ার ভয়ে কম দামে বিক্রি করেছি। এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট বাজারে মৌসুমের শেষদিকে হিমসাগরের দাম কিছুটা বেড়েছে। মণপ্রতি ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে এই জিআই পণ্য। চাষিরা বলছেন, সরবরাহ কমে যাওয়ায় শেষদিকে দাম বাড়লেও তা লোকসান পুষিয়ে নেওয়ার মতো নয়। এ ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবে উপেক্ষিত। নওগাঁর সাপাহার, রাজশাহীর বানেশ্বর বা চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট- সব বাজারেই কেজি দরে আম কেনাবেচার সিদ্ধান্ত থাকলেও ব্যবসায়ীরা তা মানছেন না। আমচাষিদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কেজি দরে আম কেনাবেচার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৫ জুন রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ে কেজি দরে আম কেনাবেচা নিয়ে উপজেলা প্রশাসন, ব্যবসায়ী, আড়তদার ও চাষিদের মাঝে আলোচনা হয়। কেজি দরে আম বিক্রির সিদ্ধান্ত হলেও প্রশাসনের নিয়ম মানা হচ্ছে না। ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন চাষিরা। তাদের অভিযোগ, এখনো ৫০-৫২ কেজিকে মণ ধরা হচ্ছে। এতে কম দামে বেশি আম যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের ঝুলিতে।
বিশ্বে আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম হলেও রপ্তানিতে সেই ধার নেই। চলতি মৌসুমে চীনসহ ৩৮টি দেশে ৫ হাজার টন আম রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এখন পর্যন্ত রপ্তানি হয়েছে মাত্র ৭৮০ টন। রপ্তানি হোঁচট খাচ্ছে নানা জটিলতায়। এই বিপুল উৎপাদনের পরও রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই পিছিয়ে। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে আমের চাহিদা বাড়ছেই। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৯ সালের মধ্যে বৈশ্বিক আম বাজারের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। দুঃখজনকভাবে, এত বড় বাজারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ প্রায় নগণ্য। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছিল ৭৮৮ টন আম। কিন্তু পরের বছরই সেই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় মাত্র ২৮৮ টনে, যা ক্রমান্বয়ে আরও কমে প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছায়। এই পতনের মূল কারণ শুধু বৈদেশিক নীতি বা প্রতিযোগিতা নয়- বরং আমাদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, মান নিয়ন্ত্রণে গাফিলতি এবং একশ্রেণির অসৎ ব্যবসায়ীর অনিয়ম। ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা চেইনশপ ওয়ালমার্টে বাংলাদেশি আমের প্রবেশ ঘটে। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। ওই সময় এফএও, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও সাতক্ষীরার হিমসাগর, ল্যাংড়া ও আম্রপালি জাতের আম বাছাই করা হয় রপ্তানির জন্য। কৃষকেরা ব্যাগিং পদ্ধতি গ্রহণ করেন, মান নিয়ন্ত্রণে সরাসরি যুক্ত হন এবং এক আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ শুরু হয়। কিন্তু এ আশার বেলুন হঠাৎ করেই চুপসে যায়। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান দ্বীপ ইন্টারন্যাশনাল কয়েক টন আম পাঠানোর পরই রপ্তানিতে ব্যাঘাত ঘটে। সরকারের একটি কোয়ারেন্টাইন বিভাগ হঠাৎ করে এই প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, অন্য দেশে রপ্তানি করা এক চালানে ফলের মধ্যে ফ্রন্ট ফ্লাই থাকার অভিযোগে। এতে করে ওয়ালমার্টের সঙ্গে করা বড় চুক্তিটি বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। রপ্তানির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা জানান- প্রধান সমস্যা ছিল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেশনের অভাব। আন্তর্জাতিক হোলসেল বাজারে প্রবেশ করতে হলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিবহন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে মান নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট মানদণ্ড মানতে হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানির জন্য ইইউ কমপ্লায়েন্স থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এই বিষয়টি অবহেলিত ছিল। কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে এসেছে আম প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে।
নাটোর অঞ্চলের টক জাতের আম, যা একসময় দাম না পেয়ে নষ্ট হতো, তা দিয়েই এখন জ্যাম, জুস, চাটনি ইত্যাদি পণ্য তৈরি হচ্ছে। এখানে প্রাণ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা প্রথমবারের মতো শিল্পপর্যায়ে আম প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু করেন। আজ সেই পথ ধরে দেশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছে ছোট-বড় প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা। সরকার আশা করছে, ২০২৫ সালেই অন্তত ৪ হাজার টন আম রপ্তানি সম্ভব হবে। আমাদের আম যদি বিদেশি বাজার জয় করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের কৃষিও পৌঁছাবে এক নতুন উচ্চতায়।
সারাদেশের আম উৎপাদনকারী এলাকা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে চাষের আওতায় জমি/চাষির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আবহাওয়া ও বাজার ব্যবস্থা সহায়ক থাকে তা হলে আর সমস্যা কি? এ ব্যাপারে সরকারী নীতি সহায়তা, প্রসেসিং শিল্প, উৎপাদনে প্রণোদনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, আম সংরক্ষণ ইত্যাদি সহায়ক হলে আমের অর্থনীতির চাঙ্গা ভাব আরও জোরালো হবে এবং আম ফল হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে একটি স্থান করে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়।
লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ
প্যানেল/মো.