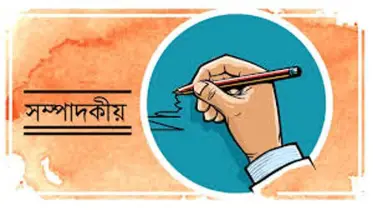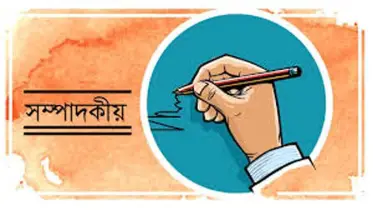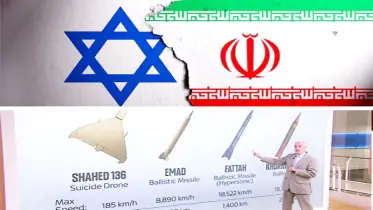বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষার গতিপ্রকৃতি ও মান নিয়ে নানা খবর গণমাধ্যমে প্রচার হচ্ছে, যা কোনো প্রকার আশার আলো বহন করছে না। যেটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দুশ্চিন্তর কারণ। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার হয়েছে বিস্তর। কিন্তু মান নিয়ে একটি বিতর্ক সব সময়ই বিচরণ করছে। যার সমাধান সহজে হবে বলে মনে হয় না। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যেমন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। যেগুলোর সংখ্যা এখন সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১৬৬টি। যার মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৫টি। এই সকল উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে ইউজিসি। এর মধ্যে ২৫টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিদায়ী গত সরকারের শাসনামলে। অথচ স্বাধীনতার পর পর দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ছয়টি। এর মধ্যে বুয়েট ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল টেকনিক্যাল হিসেবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ। গবেষণা মূলত জ্ঞানের মজুত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সাধিত সৃজনশীল ও পদ্ধতিগত একটি কাজ। এর মধ্যমে যে কোনো বিষয় বোঝার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ, সংঘটন ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এতে পক্ষপাত ও ত্রুটির উৎস নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবিক কোনো সমস্যার সমাধান করা, যা একটি ধারাবাহিক কার্য প্রক্রিয়া বা নির্দিষ্ট কিছু ধাপ অনুসরণের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে। একটি গবেষণা প্রকল্প অতীতে সম্পন্ন কোনো কাজের সম্প্রসারণও হতে পারে। এমনকি প্রয়োজনবোধে গবেষণায় কোনো যন্ত্রপাতি, পদ্ধতি বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈধতা যাচাই করার জন্য আগের প্রকল্পের উপাদান বা সমগ্র প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ পর্যন্ত থেকে যায়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে হতে হয় গবেষণাবান্ধব।
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নীতিনির্ধারক ভাইস চ্যান্সেলর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নিজের মতো নিয়োগ বোর্ড গঠন, সিন্ডিকেট তৈরি ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন। প্রশ্ন হলো, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কারা ভাইস চ্যান্সেলর হচ্ছেন। ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকর হয়েছে এরকম ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিনেটের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বাকি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের প্রক্রিয়া কী এই প্রশ্ন অনেক পুরনো, যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে।
গত ৭ অক্টোবর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠক শেষে শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন শিক্ষার্থীদের পড়ানোর পরিবর্তে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য হতে বেশি আগ্রহী। তিনি বলেছেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো ৩০০, ৪০০ বা ৫০০ শিক্ষক আছেন; কিন্তু তারা সবাই কেন উপাচার্য হতে চান আমি বুঝি না। তিনি আরও বলেছেন, আমি সব সময় একজন ভালো শিক্ষক হতে চেয়েছি, উপাচার্য হতে চাইনি। প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ উপর্যুক্ত মন্তব্যের পাশাপাশি আরও দু-একটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। কথাগুলো নিঃসন্দেহে জনগুরুত্বপূর্ণ। তবে উল্লিখিত মন্তব্যের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ কখনোই কাম্য স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষকের সংখ্যাও। পরিমাণগত এ বৃদ্ধি শিক্ষার মানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষার যে স্তরেই থাকেন না কেন, তার জ্ঞানার্জন শিক্ষার স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এর ফলে যে জনশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে তার পক্ষে জাতীয় উন্নয়নে কাক্সিক্ষত ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় না।
আওয়ামী লীগের গত নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ হিসেবে মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রতি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে সরকারের শেষ সময়ে ঘোষণা দেওয়া এমন ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। কেননা, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো কোনো কার্যক্রমই শুরু হয়নি। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫টিই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের গত দেড় দশকে। নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নারায়ণগঞ্জে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নাটোরে ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কক্সবাজার বিশ্ববিদ্যালয়, নড়াইলে এসএম সুলতান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরগুনা, ভোলা ও জয়পুরহাটে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। এগুলোর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন গত বছর সংসদে পাস হয়েছে। আর ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া একই বছর সংসদে চূড়ান্ত হয়। বাকি ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষেও ইউজিসি ইতিবাচক মতামত দিয়েছিল। শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না করেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে যেখানে-সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় উচ্চশিক্ষায় উল্টো বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। অবনমন ঘটেছে শিক্ষার মানে। এমন পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত হবে নতুন ১০ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা।
আমরা বারবার বলেছি, ‘কোয়ালিটি এডুকেশন’ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য যে বিনিয়োগ দরকার সেটা কি আমরা করছি? জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে ফেলছি। আদৌ কি সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হতে পেরেছে? অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র চার-পাঁচজন শিক্ষক মিলে অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রি দিয়ে দিচ্ছেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ভবন, শিক্ষকদের বসার জায়গা ও ল্যাবরেটরি নেই। শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এগুলোর কি সংস্কার দরকার নেই? র্যাংকিংয়ে দেখা যায় যে, চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বিশ্ব র্যাকিংয়ে প্রথম স্থানে, সেখানে বিশ্বের ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো অবস্থান নেই। অথচ ভারত ও পাকিস্থান সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছে। সম্প্রতি টাইমস হায়ার এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিংয়ের ২০২৫ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শীর্ষ পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয় ৮০১-১০০০-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এগুলো হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র্যাংকিং বেশ কয়েকটি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। র্যাংকিংয়ের কিছু সাধারণ মানদণ্ড থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন র্যাংকিং এজেন্সি তাদের নিজস্ব মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এক র্যাংকিং এজেন্সি থেকে অন্য র্যাংকিং এজেন্সির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কর্মকাণ্ডই সব র্যাংকিং এজেন্সির জন্য প্রধান ও সাধারণ সূচক। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন জায়গাগুলো কীভাবে উন্নত করা যায় সেটি নিয়ে আলোচনা করা দরকার।
বিভিন্ন সংস্থার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষমতা সূচকগুলোর মূল্যায়নের মানদণ্ড থেকে এটি খুব স্পষ্ট যে, সব সংস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গবেষণা। গবেষণায় রয়েছে প্রকাশনা, শিক্ষকের সাইটেশন, প্রকাশনার প্রভাব, গবেষণা তহবিল বা আয়, নোবেল বিজয়ী এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। বিশ্ব র্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মক্ষমতা উন্নত করতে প্রধান অগ্রাধিকার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রচার। সর্বোত্তমমানের গবেষণা ফল তৈরির শক্ত ট্র্যাক রেকর্ডধারী দক্ষ গবেষকরাই উচ্চমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। নতুন গবেষক তৈরি করে গবেষণার খ্যাতি, সাইটেশন, সহযোগিতা, প্রভাব এবং প্রশিক্ষণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন। বর্তমানে দেশে সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক হলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ৬৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ই আইকিউএসি প্রতিষ্ঠা করেছে। বলা চলে, বেশিরভাগ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বারবার তাগাদা দেওয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আশানুরূপ সাড়া মিলছে না। এটা উচ্চশিক্ষায় মান যথাযথ গুরুত্ব না পাওয়ারই প্রতিফলন। দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে দক্ষ ও গুণগতমানের মানবসম্পদ জোগাতে হলে শিক্ষার মানে জোর দেওয়ার বিকল্প নেই। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের আরও উদ্যোগী ভূমিকা কাম্য।
সত্য যে, বিগত দুই দশকে দেশে উচ্চশিক্ষায় সংখ্যা ও অবকাঠামোগত উল্লম্ফন ঘটেছে বিস্তর। তবে মান ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। নিয়মিত বিরতিতে তারই প্রকাশ ঘটছে বৈশ্বিক র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হতাশাজনক অবস্থানে। বিশ্বখ্যাত যুক্তরাজ্যভিত্তিক কিউএস জরিপ নয়; সাংহাই, স্কপাস ও টাইমসের মতো অন্য স্বীকৃত বৈশ্বিক র্যাংকিংয়েও বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে। এর পেছনে গবেষণায় প্রাধিকার না পাওয়া, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ঘাটতি, শিক্ষায় অপ্রতুল বিনিয়োগ, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি বিস্তারের মতো কিছু অন্তর্নিহিত ফ্যাক্টর তো আছেই। তার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সব প্রতিষ্ঠানে আইকিউএসি না থাকাও নিশ্চয়ই একটি বড় কারণ। কেননা, আইকিউএসির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু নিয়ম-নীতি অনুসরণের পাশাপাশি শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও প্রাক্তনদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে তা নিরীক্ষা করা হয় এবং চূড়ান্তভাবে মানোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যার ভিত্তিতে মান নিয়ন্ত্রণের কাজটি করা হয়। কাজেই উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি কার্যকর আইকিউএসির গুরুত্ব কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। বারবার নির্দেশনা দেওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হচ্ছে না তা খতিয়ে দেখতে হবে ইউজিসিকে। প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। বৈশ্বিক র্যাংকিংগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, ভারতসহ আমাদের অদূরবর্তী দেশগুলোর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় উপর্যুপরিভাবে ভালো করছে। উল্লিখিত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী ধরনের পাঠক্রম অনুসরণ করছে এবং মান নিয়ন্ত্রণে কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলেছে তা বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। সেখানকার আইকিউএসিগুলো কীভাবে কাজ করছে সে অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো যেতে পারে।
লেখক : অধ্যাপক (অর্থনীতি), সাবেক ডিন (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ) ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা