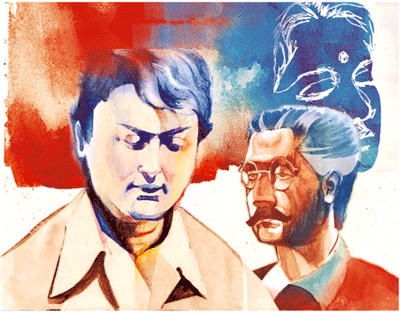
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর সাহিত্যিক জীবনে ১১৯টি ছোটগল্প লিখেছেন, তার মধ্যে প্রায় ২৩টি ছোটগল্পে যৌতুক বা পণ প্রথার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। কোনটিতে প্রবলভাবে আবার কোনটিতে আকারে ইঙ্গিতে। বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্প ও গল্পকার দুটোরই কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। আর প্রথম সার্থক ছোটগল্প দেনা-পাওনা’র বিষয়বস্তুও যৌতুক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্যক্তিজীবনের তিক্ততা ও সামাজিক প্রথার যাঁতাকলে বিষিয়ে উঠেছিলেন বলেই হয়তো যৌতুকের বিষয়টি তাঁর গল্পে এত প্রবলভাবে এসেছে। রবন্দ্রীনাথের যৌতুক নিয়ে লেখা প্রায় সব গল্পেই যৌতুকের বলি হতে হয়েছে নারীদের আর নিঃস্ব হতে হয়েছে তাদের পিতাদের। গল্পগুলো জুড়েই রয়েছে যৌতুকের নির্মমতার শিকার নারীদের আত্মচিৎকার আর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বুকফাটা আর্তনাদ। এদিক থেকে অপরিচিতা (১৯১৪) গল্প রবন্দ্রীনাথ ঠাকুরের বিশেষ সংযোজন। যৌতুক নিয়ে লেখা হলেও গল্পটি মূলত যৌতুকের বিরুদ্ধে নারী-পুরষের সম্মিলিত প্রতিবাদ আর পিতৃত্বের জয়গাঁথা।
সমাজ বিবর্তিত হয়, অন্ধকার আলোর মুখ দেখে, অত্যাচারিত মাথা তুলে, প্রথাও একসময় অনিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। পরিবর্তন আসে সময়, সমাজ ও মানুষের মননে। রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন গল্পে যৌতুকের নির্মমতা নানানভাবে প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করেননি। দিনের পর দিন নির্যাতিত হয়েছে নারীরা, নিঃস্ব^ হয়েছে পিতারা কিন্তু কেউই ঘুরে দাঁড়ায়নি। অশিক্ষিত গ্রাম্য পিতা যেমন এ যন্ত্রণায় ভুগেছেন তেমনি শিক্ষিত পিতা তার শিক্ষিত কন্যা নিয়েও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে পারেননি বরং নির্যাতন সয়ে গেছেন। প্রসঙ্গক্রমে দেনা-পাওনা গল্পের নিরুপমা ও তার পিতা রামসুন্দর মিত্র এবং হৈমন্তী গল্পের হৈমন্তী ও তার পিতা গৌরীশঙ্কর বাবুর কথা বলা যায়। নিরুপমা ও রামসুন্দর মিত্র সমাজের নিচুস্তরের অশিক্ষিত মানুষ হয়ে যা মেনে নিয়েছেন, হৈমন্তী ও গৌরীশঙ্কর বাবু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হয়েও তাই করেছেন। শিক্ষা তাদের মধ্যে প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো সাহস সঞ্চার করতে পারেনি। ফলে নিরুপমা ও হৈমন্তীকে তিলে তিলে নিঃশেষ হতে হয়েছে। গৌরীশঙ্কর ও রামসুন্দরকে কন্যার মৃত্যু মেনে নিতে হয়েছে। প্রতিবাদের কোন ভাষা তাদের তো ছিলই না বরং ধার-দেনা করে কিংবা বসতভিটা বিক্রি করেও তারা মেয়েদের মুক্তি দিতে পারেননি। পেরেছেন কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন।
রবীন্দ্রনাথ অপরিচিতা গল্পের মধ্য দিয়েই সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন, প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দুঃসাহস দেখালেন। যুগ যুগ ধরে সমাজে গেঁড়ে বসা প্রথার মুখে কুলপ এঁটে দিলেন। কন্যা ও কন্যার পিতার যৌতুকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধই অপরিচিতা গল্পের বিশিষ্টতা।
শম্ভুনাথ সেন পেশায় একজন ডাক্তার। তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ সুপুরুষ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
‘বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এ পারে বা ও পারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।’
হ্যাঁ শম্ভুনাথ সেন সুপুরুষই বটে। আর এ সুপুরুষতার মধ্যে রয়েছে শম্ভুনাথ সেনের ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা, দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং প্রতিবাদী চেতনা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে কন্যাদয়গ্রস্ত পিতার এমন হুংকার প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে একরকম যুদ্ধ ঘোষণা যার সহচরী মেয়ে কল্যাণী। যেখানে মেয়ের লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার চেয়ে বিয়ের আসর থেকে বরকে ফিরিয়ে দেওয়াই বেশি লজ্জার, অপমানের।
‘সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড় সৎপাত্রের কপালে এত বড় কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল?’
শম্ভুনাথ সেন মেয়ে কল্যাণীর বয়স বাড়া নিয়ে কখনো চিন্তিত ছিলেন না বরং চিন্তিত ছিলেন একজন সুপাত্র নিয়ে, শিক্ষার পাশাপাশি যার থাকবে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা, ন্যায় অন্যায় বুঝার ক্ষমতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সৎসাহস ও শক্তি। অনুপমকে শম্ভুনাথ সেন তাই ভেবেছিলেন। এজন্য কল্যাণীকে পাত্রস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না, তার জন্য চাই পারিবারিক পরিচর্যা যা অনুপমের মধ্যে ছিলো না। অনুপমের অর্জন শুধু উচ্চশিক্ষার সনদ আর মায়ের আদেশ মেনে নেওয়ার ক্ষমতা। যার জন্য নিজেকে সে সৎপাত্র দাবি করে, যে কিনা তামাক পর্যন্ত খায় না।
‘কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালো মানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।’
সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অনুপম সৎপাত্র’ই বটে কিন্তু সমাজের এ সৎপাত্র’ই কল্যাণী ও শম্ভুনাথ সেনের কাছে ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ বলে আখ্যায়িত হয়েছে। যে কিনা পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়।
পারিবারিক হীনম্মন্যতার মধ্যে বেড়ে ওঠা অনুপম কখনো নিজের স্বাধীন মতটুকু প্রকাশ করতে পারেনি। মা আর মামার চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে। নিজের বিয়ে সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস তার ছিলো না। কল্যাণীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ার পর কল্যাণীকে দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্তে¡ও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি কিংবা একখানা ফটোগ্রাফের আবদারও সে করতে পারেনি। বন্ধু হরিশ আর পিসতুতো ভাই বিনুদার মুখের বর্ণনা শুনেই তাকে শান্ত থাকতে হয়েছে।
বিয়ের আসরে অনুপমের যৌতুক লোভী মামার অদ্ভুত আবদারে শম্ভুনাথ সেন অবাক হয়েছিলেন। বিষয়টি আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি অনুপমকে ডেকে পাঠান এবং তার সাথে কথা বলেন। কিন্তু মামার মুখের ওপর অনুপমের কথা বলতে না পারা শম্ভুনাথকে রীতিমতো হতবাকই করেনি, কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। তখনই হয়তো তিনি এই মেরুদÐহীন প্রাণীটির হাতে কন্যা সমার্পণ না করার চ‚ড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এরপর যা করেন তার সবটুকুই সৌজন্যতা মাত্র।
মেয়ের শরীর থেকে গহনা খুলে সেগুলোকে পরীক্ষা করিয়ে শম্ভুনাথ সেন দেখিয়ে দিয়েছেন সোনার মধ্যে যেমন কোনো খাদ নেই তেমনি খাদহীন তার মনমানসিকতা। খাঁটি সোনার মতোই তার ব্যক্তিত্ব। পক্ষান্তরে, কল্যাণীকে আশীর্বাদ করার সময় অনুপমের মামার দেয়া এয়ারিং জোড়াও তিনি পরীক্ষা করিয়েছেন এবং সেটার নড়বড়ে অবস্থার মতো অনুপম ও তার মামার হীন মানসিকতাকে তিনি সুকৌশলে চিহ্নিত করেছেন। তাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।
‘গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্রার হাতে দিয়া বলিলেন, এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।’
স্যাক্রা কহিল, ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।
শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, ‘এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।’
মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।
মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল।’
লজ্জায় মামার মুখ লাল হলেও এ লজ্জা মামার একার নয়, এ লজ্জা পুরো সমাজের, পুরুষাশাসিত সমাজ ব্যবস্থার। শম্ভুনাথ সেনের এ প্রত্যাখ্যান পুরো সমাজের মুখকেই লাল করে দিয়েছে।
শম্ভুনাথ সেন নির্বিকারভাবে বরযাত্রীদের ভোজনকার্য শেষ করানোর পর তাদের বাড়ি চলে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবে বরপক্ষ আশ্চর্য হলেও শম্ভুনাথকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা যায়নি। তিনি ছিলেন স্বাভাবিক। অনুপমের মামার কাছে যা ঠাট্টা বলে মনে হয়েছিলো।
‘মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।’
শম্ভুনাথ কহিলেন, ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।’
মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।
শম্ভুনাথ কহিলেন, আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।’
শম্ভুনাথের এ ঠাট্টার সম্পর্ককে স্থায়ী করতে না চাওয়াটাই ছিলো সবচেয়ে বড় ঠাট্টা। তবে সে ঠাট্টা শুধু অনুপমের মামার সঙ্গে নয়, এ ঠাট্টা তিনি করেছেন প্রচলিত সমাজের সঙ্গে। যে ঠাট্টা পুরো সমাজকে ধমকে দেয়, ধমকে দেয় সমাজের প্রচলিত ধ্যান, ধারণা ও বিশ্বাসকে। যে ঠাট্টায় কন্যার পরিবার নয়, বরের পরিবারকে সমাজ হেও প্রতিপন্ন করে। সমাজ ব্যবস্থাকে করে ব্যঙ্গ, কুলপ এঁটে দেয় সমাজের মুখে, সমাজপতিদের মৃখে। যার প্রকৃত উদাহরণ অনুপমের মামা, যে কিনা পরবর্তীতে অনুপমের বিয়ে নিয়ে আর একটি কথাও বলার সাহস পায়নি। কর্তৃত্বের ভার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।
শম্ভুনাথ সেনের একমাত্র মেয়ে কল্যাণী। তার সমস্ত আয়োজন মেয়েকে ঘিরেই। কল্যাণীই তার সমস্ত সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকার। সুতরাং যৌতুক হিসেবে তিনি যা দিতে রাজি হয়েছেন তা কল্যাণীরই প্রাপ্য। কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন অনুপমের বিষয়ে তার আপত্তি ছিল। রামসুন্দর মিত্র ও গৌরীশঙ্কর বাবুর মধ্যে সুপাত্র’র প্রতি যে দুর্বলতা ছিলো তা শম্ভুনাথ সেনের মধ্যে দেখা যায়নি। তাই তিনি মেয়ে লগ্নভ্রষ্ট্র হবে জেনেও একটুও বিচলিত হননি। কারণ মেয়ে নির্যাতিত হয়ে মারা যাওয়ার চেয়ে লগ্নভ্রষ্ট হয়ে পিতার আশ্রয়ে থাকাকে তিনি শ্রেয় মনে করেছেন। আর লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার ধারণাও যে সমাজের প্রচলিত সংস্কার, যার তোয়াক্কা কল্যাণী ও শম্ভুনাথ কেউই করেননি। এখানেই শম্ভুনাথ অন্যদের চেয়ে আলাদা, এখানেই শম্ভুনাথ চরিত্রের বিশিষ্টতা। মেয়ে কল্যাণীকেও তিনি সেভাবেই গড়ে তুলেছেন। যে শিক্ষা অনুপমের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেনি সে শিক্ষা শম্ভুনাথ কল্যাণীকে দিতে পেরেছেন। তিনি নিজেকে কখনো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ভাবেননি। কল্যাণীকে তিনি লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিচারে মেয়ে হিসেবে না দেখেছেন সন্তান হিসেবে। যার জন্য লগ্নভ্রষ্ট হয়েও কল্যাণী বিচলিত হয়নি বরং নিজেকে আরো শক্তিশালীরূপে তৈরি করেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে। সমাজের প্রচলিত প্রথা থেকে নারীকে মুক্তির জন্য মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছে। দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছে। আর তার এ চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়মনোভাবের পেছনে যে মহৎ শক্তিটি কাজ করেছে তার নাম শম্ভুনাথ সেন। কল্যাণীর পিতা। পিতা হিসেবে এখানেই শম্ভুনাথ সেনের সার্থকতা। অপরিচিতা গল্প তাই পিতৃত্বের জয়াখ্যান।








