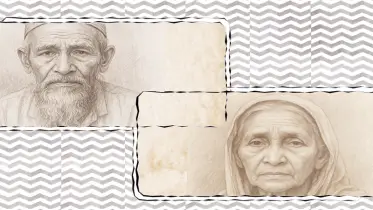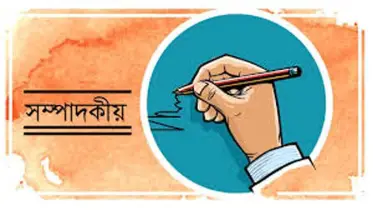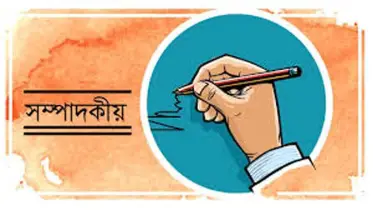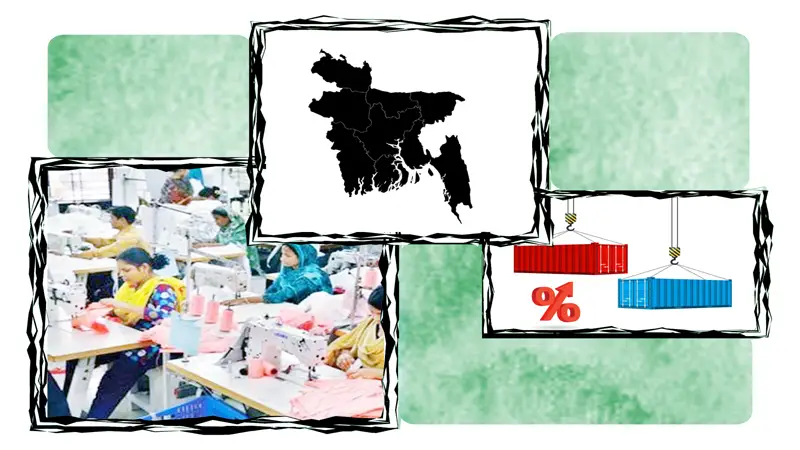
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক ২০২৫ সালের মাঝামাঝিতে এসে অভূতপূর্ব এক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু, কিন্তু বাংলাদেশের মিত্র- এমন রাষ্ট্রের সঙ্গেও বহুমাত্রিক সম্পর্ক রক্ষায় আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ একাধিক পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ শুধু একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তির বাধা নয়, বরং বৈশ্বিক বাণিজ্য ন্যায়বিচার, ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য এবং বহুপক্ষীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্যই একটি উদ্বেগজনক ইঙ্গিত। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির যুক্তি দিয়ে এই শুল্ক আরোপ করা হলেও ট্রাম্প প্রশাসনের ভূরাজনৈতিক অভিসন্ধিই এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতির খ্যাতনামা বিশ্লেষক জোসেফ স্টিগলিটজ, লরা টাইসন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল। তাঁদের মতে, ‘বাণিজ্য ভারসাম্য’ শব্দটি দিয়ে একটি বৃহৎ কৌশলগত উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখা হয়েছে, যেটি হলো চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস করা এবং চীন-নির্ভর আমদানি-রপ্তানিকারক দেশগুলোর ওপর কৌশলগত চাপ প্রয়োগ।
বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই চাপ বহুমাত্রিক। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানি ছিল ১৬.৬৩ বিলিয়ন ডলার, যা মোট আমদানির ২৬.৪ শতাংশ। এর মধ্যে ৮০ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের কাঁচামাল- ওভেন কাপড়, রাসায়নিক দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক উপকরণ। যুক্তরাষ্ট্র এখন এসব পণ্যে ৪০ শতাংশ ‘স্থানীয় মূল্য সংযোজন’-এর কঠোর শর্ত দিয়ে বাংলাদেশের উৎপাদন শৃঙ্খলেই আঘাত হানছে। রুলস অব অরিজিনের এই প্রস্তাব একদিকে চীননির্ভর সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর সরাসরি চাপ সৃষ্টি, অন্যদিকে বিশ^বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বহুপক্ষীয়তার মূলনীতির পরিপন্থি আচরণকেও সামনে নিয়ে আসছে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে ৩.৩৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। এই প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ওয়ালমার্ট, লেভিস, ও এইচঅ্যান্ডএমের মতো কোম্পানিগুলো অর্ডার স্থগিত বা সীমিত করছে, মূলত শুল্কসংক্রান্ত অনিশ্চয়তার কারণে। বিশেষ করে ওয়ালমার্টের কিছু সরবরাহকারী ইতোমধ্যে আগাম কার্যাদেশ বাতিল করেছে নয়তো স্থগিত রেখেছে। এমনকি লেভিস তাদের ২০২৫ সালের প্রয়োজনীয় পোশাকের ৬০ শতাংশ আগেভাগেই মজুত করে রেখেছে, ভবিষ্যতের ঝুঁকি এড়াতে।
এদিকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এখনো অনেক দিক থেকেই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, ৫ ডলারে কেনা একটি টি-শার্ট যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয় ৩০-৩৫ ডলারে। ফলে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার ব্যবধান বহাল থাকে। ট্রাম্প প্রশাসনের পূর্ববর্তী ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর যে শুল্ক ভাগাভাগির মডেল গড়ে উঠেছিল, তা এখন আরও দৃঢ় হচ্ছে। প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক ও খুচরা বিক্রেতা- তিন পক্ষেই বোঝা ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। তবু এতে ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলোর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ৩৮.৪৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা বৈশ্বিক বাজারের ৬.৯ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। অথচ ভারতের অবস্থান পঞ্চম, যদিও তাদের তুলা ও শ্রমশক্তি বেশি। এর কারণ হলো- উৎপাদন সক্ষমতার ঘাটতি, গঠনগত সমস্যা ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের অভাব। বাংলাদেশের এই সাফল্য সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক কাঠামো ও ভূরাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের চাপ দেশের জন্য বহুমুখী চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। ওয়াশিংটন যেমন বাংলাদেশের চীননির্ভরতা কমাতে চায়, তেমনই নিজের কৌশলগত মিত্রদের জন্য একতরফাভাবে বাণিজ্য সুবিধা নির্ধারণ করছে, যা বিশ^ বাণিজ্য সংস্থার ‘মোস্ট ফেভার্ড নেশনস’ নীতিকে স্পষ্টভাবেই লঙ্ঘন করে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে, বাংলাদেশ যেন চীন থেকে আমদানি কমিয়ে মার্কিন পণ্য যেমন তুলা, গম, এলএনজি ও সামরিক সরঞ্জাম বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার এই শর্ত সরাসরি মেনে না নিলেও কৌশলগত সমঝোতার পথে হাঁটার চেষ্টা করছে। মার্কিন বাজারে রপ্তানি ঘাটতি কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ভারসাম্য আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং গম ও এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে তাদের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার জন্য সরঞ্জাম কেনার আহ্বান জানিয়েছে। অর্থাৎ সরাসরি না বললেও, শুল্ক ছাড়ের বিনিময়ে একটি ভূরাজনৈতিক অক্ষ গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। আবার চীন বিভিন্ন দেশকে সতর্ক করে বলেছে, যেসব দেশ ট্রাম্পের শুল্ককে কেন্দ্র করে চীনের সঙ্গে বিদ্যমান বাণিজ্যসহ অন্য সম্পর্কে পরিবর্তন আনবে, চীন তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। এই পরিস্থিতি শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক কৌশলেরও পরীক্ষা। কারণ বাংলাদেশ চাইলে রাতারাতি চীনা পণ্যের বিকল্প উৎস খুঁজে পাবে না। আবার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাও কৌশলগতভাবে অসম্ভব। ফলে ট্রাম্প প্রশাসনের ‘আমাদের পাশে না, মানেই বিপক্ষে’ ধরনের মনোভাব বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য কার্যত ‘জিও-ইকোনমিক ব্ল্যাকমেইলিং’-এ পরিণত হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকেও নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদদের একাংশ সতর্ক করে বলছেন, এই শুল্কনীতি দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য ক্ষতিকর হবে। কারণ উৎপাদন খরচ বাড়বে, আমদানি কমবে এবং বিকল্প উৎস খুঁজে পেতে সময় ও ব্যয়- দুটোই বাড়বে। একই সঙ্গে পতনশীল ‘মার্কিন সভ্যতা (আসলে অসভ্যতা)’ আরও গতি পাবে। এমন এক যুগসন্ধিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে যা করণীয়, তা হচ্ছে-
১. বাংলাদেশের উচিত এলডিসি মর্যাদার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নিয়মের আওতায় মার্কিন শুল্ক কমানোর জন্য জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো। এর জন্য লবিস্ট নিয়োগ, আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমর্থন আদায় এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির শর্তে নমনীয়তা প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন পণ্য যেমন গম, তুলা, এলএনজি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে মার্কিন ভূরাজনৈতিক শর্ত যেমন নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা বা অন্য দেশের সঙ্গে শুল্কমুক্ত সুবিধা না দেওয়া) গ্রহণ না করে ডব্লিউটিওর এমএফএন নীতির প্রতি অবস্থান বজায় রাখা জরুরি।
২. বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮১ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে এবং যুক্তরাষ্ট্র তার অন্যতম বড় বাজার। ট্রাম্পের শুল্কনীতি এ খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস করছে, বিশেষ করে ভিয়েতনামের তুলনায়। এ ছাড়া ওয়ালমার্টের মতো মার্কিন খুচরা বিক্রেতারা অর্ডার স্থগিত করছে, যা রপ্তানি আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের উচিত রপ্তানি বাজার বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমানো। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং উদীয়মান বাজার যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। ইউরোপে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জিএসপি সুবিধা পায়, যা আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ছাড়া পোশাক ছাড়াও অন্য খাত যেমন চামড়া, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব।
৩. বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, বিশেষ করে ওভেন খাত, চীন থেকে আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর ৭০ শতাংশেরও বেশি নির্ভরশীল। ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর ‘রুলস অব অরিজিন’ (৪০ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজন) এই নির্ভরতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংকট ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা উৎপাদন ব্যাহত করছে। এজন্য কাঁচামালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে স্থানীয় টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। নিটওয়্যার খাতে স্থানীয় সুতা উৎপাদনের সাফল্যের মতো ওভেন খাতেও স্থানীয় কাপড় উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এর জন্য সরকারি প্রণোদনা, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর জরুরি। পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়ন করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, উন্নত বন্দর ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বিত লজিস্টিকস নিশ্চিত করতে হবে, যা উৎপাদন খরচ কমাবে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াবে। এ ছাড়া শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, যা উচ্চ শুল্কের প্রভাব মোকাবিলায় সহায়ক হবে।
৪. যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের চীনের ওপর বাণিজ্যিক নির্ভরতা কমাতে চাপ দিচ্ছে, যা বাংলাদেশকে ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলেছে। এ ছাড়া ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সমস্যা ও প্রতিযোগী দেশগুলোর (যেমন ভিয়েতনাম) শুল্ক সুবিধা বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করছে। এ অবস্থায় আঞ্চলিক জোট গঠনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের উচিত তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে মার্কিন শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে যৌথ কৌশল তৈরি করা। আসিয়ান বা সার্কের মতো আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মে এই বিষয়ে আলোচনা জোরদার করা যেতে পারে। চীনের পাশাপাশি ভারত, তুরস্ক বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি বাড়ানো যেতে পারে, যাতে চীনের ওপর নির্ভরতা কমে এবং মার্কিন ‘রুলস অব অরিজিন’ শর্ত পূরণ সহজ হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এমএফএন নীতির আওতায় মার্কিন শুল্ক নীতির বৈষম্যমূলক প্রকৃতি নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে। এটি আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে সহায়ক হবে।
৫. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে শুল্কের বোঝা সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পক্ষ (প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, খুচরা বিক্রেতা) ভাগ করে নিচ্ছে। তবে ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলো এই চাপ বহন করতে অক্ষম। এ অবস্থায় সরকারের উচিত হবে রপ্তানিকারকদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা, ঋণ সুবিধা ও কর হ্রাসের মাধ্যমে শুল্কের প্রভাব মোকাবিলায় সহায়তা করা। তবে মনে রাখতে হবে, অতীতের মতো বড় ও সক্ষম প্রতিষ্ঠানগুলো প্রণোদনার অর্থ আত্মসাৎ করতে না পারে। এ ছাড়া শিল্পের ডিজিটালাইজেশন ও স্বয়ংক্রিয়করণে বিনিয়োগ বাড়িয়ে উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করবে।
মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ এখন এক নীরব অথচ গভীর বাণিজ্যযুদ্ধের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে। এই যুদ্ধে অস্ত্র নয়, প্রয়োজন হবে শাণিত কূটনীতি, স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঁচামাল ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সংহতি এবং অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার সুষম বিকাশ। শুধু দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নয়, বহুপাক্ষিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই হতে হবে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যে এটিও বুঝতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আজকের সর্বোন্নত দেশগুলো ১০০-১৫০ বছর আগে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ আয়কারী বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প উচ্ছিষ্ট আর আবর্জনা মনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আর এই শিল্পকেই যদি আমরা ‘সোনা’ মনে করি, তাহলে অতি চালাক ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প তো ছেলেখেলাই করবেন।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্যানেল/মো.