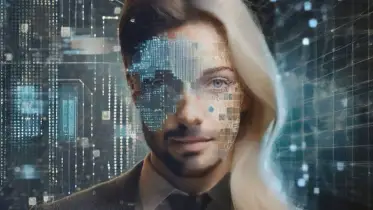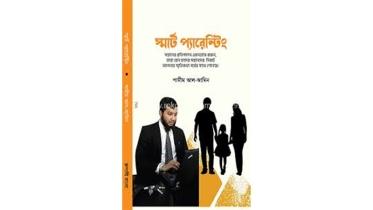ছবি: জনকণ্ঠ
বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো সংস্কার আগে নাকি নির্বাচন আগে। প্রশ্নটি কোটি টাকার হলেও উত্তরটি আমার মতে খুবই সস্তা। উত্তরটি হল নির্বাচন।
এত সরল উত্তরে কেউ কেউ মন খারাপ করে ফেলতে পারেন। তবে এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, যেগুলো আন্তরিকভাবে বিবেচনায় নিলে আমার উত্তরটিকে শতভাগ সঠিক বলেই মেনে নেওয়া সম্ভব হবে।
১. একটি দেশের ধারাবাহিক উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল প্রশাসন-পুলিশ প্রশাসন ও সিভিল প্রশাসন। আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই দুই প্রশাসনই ভয়ংকর রকম নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এর অন্যতম প্রমাণ বিভিন্ন জায়গার 'মব' চর্চা। অধিকাংশ জায়গায় 'মব' আটকাতে প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেশবাসী দেখেছেন। গুগল বলছে, বাংলাদেশে পুলিশ ও জনগণের অনুপাত ১:৭৫৫-১:১২০০। জাতিসংঘের সুপারিশ ১:৩০০। যেখানে ভারতে ১:৭০০, আমেরিকায় ১:৩৬৫, যুক্তরাজ্যে ১:১৭৩, জার্মানিতে ১:৩৩২। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে এই হার ১:১৩৬–১:৫৭৯।
এখান থেকে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর শক্তির সক্ষমতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যৌক্তিকভাবে এই বিপুল পরিমাণ মানুষকে শৃঙ্খলায় রাখতে যে পরিমাণ শক্তি পুলিশের প্রয়োজন তা আনুপাতিক হারে একেবারেই তলানিতে। তাহলে শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসনের উপরে নির্ভর করে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আশা করা বা শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে কার্যকরভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে নিবৃত করা অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের জন্য কঠিনই নয় বরং অসম্ভব।
এর পরেই আরেকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। এই পুলিশ প্রশাসনের বড় একটা অংশের বিরুদ্ধে পতিত সরকারের হয়ে বিভিন্ন প্রকার আইনবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত। পুলিশের অভিযুক্ত বড় কর্মকর্তাগুলো আইনের আওতায় আসলেও বা পালিয়ে যাওয়ার কারণে পুলিশ বাহিনীতে না থাকলেও নিম্ন পর্যায়ের সদস্যরা এখনো পুলিশ বাহিনীতে বহাল। এদের এই সংখ্যাটাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এরা কৌশলে যে 'পুলিশিং' করছে না, এটা দিবালোকের মত সত্য। ফলে পুলিশ-জনগণের ওই অনুপাতটির তফাৎ আরও বড় হয়ে গেল।
এর পরে আসি সিভিল প্রশাসনের কথায়। সিভিল প্রশাসনের এই মুহূর্তে যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের প্রায় সবই গত সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তাদের অনেক বড় একটা অংশ কোনো না কোনোভাবে অতীত সরকারের বিভিন্ন অপকর্মের সাক্ষী এবং সঙ্গী। কিছু জায়গায় আমরা পরিবর্তন করেই ধরে নিচ্ছি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এটি আসলে সম্ভব নয়। পরিবর্তনটাও সম্ভব নয়। সিভিল প্রশাসনের চরিত্রের আমূল পরিবর্তনও প্রায় অসম্ভব। কারণ এটি তো একটি বাতি বা পাখা চালানোর সুইচের মত নয় যে টিপে দিলাম চলল, টিপে দিলাম বন্ধ হয়ে গেল!
কথা আসতে পারে, পুলিশের সাথে তো আমাদের গর্বের সশস্ত্র বাহিনী মাঠে রয়েছেন। তারা মাঠে রয়েছেন ঠিকই, তবে তাদেরকে পুলিশের বিকল্প ভাবার বোকামিটা বোধহয় করা ঠিক হবে না। বিচারিক ক্ষমতা নিয়েই রয়েছেন আমাদের সশস্ত্র বাহিনী, তবে এই কাজ তাদের না। তাদেরকে দিয়ে এমন একটি কাজ করানো হচ্ছে যা তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।
২. বাংলাদেশে এই মুহূর্তে রাজনীতিতে কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখছে এমন সবচেয়ে বড় দলটি হল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এরপরেই রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম এবং তার সাথে এনসিপি বা অন্যান্য ছোটখাটো রাজনৈতিক দল। তবে আমরা সবাই সচেতনভাবে হোক বা অসচেতনভাবে হোক—কেন যেন ভুলে যাই যে, যে দলটি ৫ আগস্ট ২০২৪-এর আগ পর্যন্ত প্রায় ১৬ বছর এই দেশ শাসন করেছে, তাদের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ পালিয়ে গেলেও বা আইনের আওতায় আসলেও মধ্যম সারির বা নিচের সারির নেতারা এবং তাদের সমর্থকরা (যার সংখ্যা কয়েক কোটি হতে পারে) এখনো এই দেশে রয়েছে, যাদের অনেকেই নিষ্ক্রিয় থাকলেও অনেকেই ক্রিয়াশীল।
আমরা যদি সারা দেশে রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিশৃঙ্খলা তৈরির দায় এককভাবে শুধু ওই দলটির দেশে অবস্থানকারী নেতাকর্মীর উপরেই দেই, তাহলেও ওই বিপুলসংখ্যক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে একমাত্র প্রশাসনের সহায়তায় নিয়ন্ত্রণ করা বা অপরাধ থেকে বিরত রাখাটা প্রায় অসম্ভব। আর অন্য দলের নেতাকর্মীরা যদি সেই খাতায় নাম লেখায়, তাহলে তো কথাই নেই!
৩. বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ও প্রশাসন ব্যবস্থায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে জনগণ। জনগণের সম্পূর্ণ অংশ না হলেও সরকারি দলের কর্মী-সমর্থকরা প্রশাসনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পূর্বশর্ত হলো সামাজিক শৃঙ্খলা। শুনতে যেমনই লাগুক, বর্তমানের এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আর যাই হোক 'কর্মী-সমর্থক' ওই অংশটি নেই যেটি সামাজিকভাবে প্রশাসনের সমর্থক হিসেবে দলীয় বা রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য আদায়ে সক্রিয়ভাবে দেশের আনাচে-কানাচে কাজ করবে!
৪. সংস্কার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অপরপক্ষে নির্বাচন একটি একক এবং এককালীন প্রক্রিয়া। একটি দেশের যেকোনো ধরনের আইন প্রণয়ন বা আমরা যাকে সংস্কার বলছি—সেটিতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেন এবং ধরে নেওয়া যায় জনগণই পরোক্ষভাবে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু যখন ভোট দিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া 'আবেগের প্রতিনিধিরা' আইন প্রণয়ন বা সংস্কারের প্রক্রিয়া চালান, তখন এটি কখনো কখনো হিতে বিপরীত হতে পারে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন রাজনীতিবিদদেরই দায়িত্ব, সামাজিকভাবে এ দায়িত্ব কারো পালন ঝুঁকিপূর্ণ। এতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা যায়। কখনো কখনো এতে জনগণের ইচ্ছার বাস্তবায়ন দেখা যায় না।
৫. দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া যত দেরি হবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ততই নাজুক হতে পারে। প্রশ্ন আসতে পারে—সংস্কার ছাড়া নির্বাচন কি কার্যকর হবে কিনা? কার্যকর ও স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল ব্যাপার—
প্রত্যেকটি ভোটারের ভীতিহীন স্বতঃস্ফূর্ত ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া, সততার সাথে প্রয়োগকৃত ভোটগুলো গণনা করা ও নির্বাচিত প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা। এই মুহূর্তেই নির্বাচনের দায়িত্ব এককভাবে সেনাবাহিনীর হাতে হস্তান্তর করলেই দ্রুততম সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব। তবে সংস্কারের নামে কাল বিলম্ব করলে তা যে কোনো কাজে আসবে না—এটা মোটামুটি নিশ্চিত। এর কারণ আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—সামাজিক অসক্ষমতা।
সুতরাং দ্রুততম সময় নির্বাচন দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে অধিকতর সংস্কারের পথ উন্মোচন করা এখন সময়ের দাবি।
লেখক:
এস এম নাহিদ হাসান
শিক্ষক, সাংবাদিক ও কবি
ফরিদপুর, পাবনা
মুমু ২