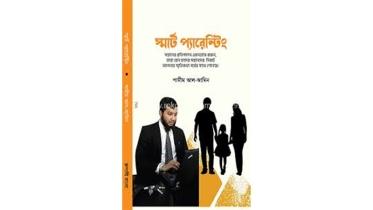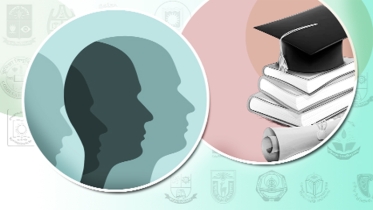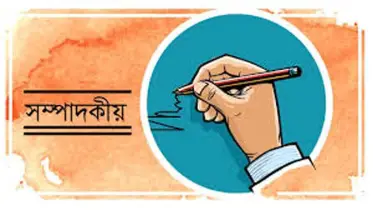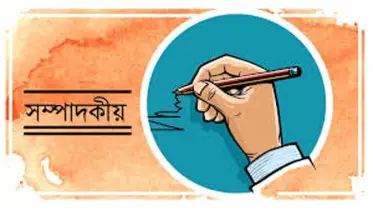বর্তমান রাজনীতিতে ‘ট্যাগিং’ একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা
বর্তমান রাজনীতিতে ‘ট্যাগিং’ একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা হিসেবে হাজির হয়েছে। তা শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠী, এমনকি ব্যক্তিরাও এখন একে অপরকে ভুল তথ্য ও গুজব ছড়িয়ে বদনাম করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ‘ট্যাগিং রাজনীতি’ বলতে মূলত বোঝায়, কোনো ব্যক্তি বা দলকে মিথ্যা লেবেল দিয়ে তাদের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া ও সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা।
২০১৩ সালে রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিভাজনকে কিছু সহজ পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়। যেমন শাহবাগি বনাম ইসলামপন্থি, ভারতপন্থি বনাম পাকিস্তানপন্থি, রাজাকার বনাম ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। এই বিভাজন শুধু রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা সামাজিক সম্পর্কেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল, যা এখনো রয়ে গেছে।
বাংলাদেশে গত কয়েক দশক ধরে ট্যাগ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পর আমাদের সবার প্রত্যাশা ছিল, জাতি এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সব শ্রেণি-পেশা ও মতাদর্শের মানুষের জন্য নিরাপদ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে। সেই লক্ষ্যে কর্মসূচি ঘোষণা এবং তা বাস্তবায়নে সরকারসহ সব পক্ষই নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করবে। দুঃখজনক, সেই পথে এগিয়ে না গিয়ে বরং আমরা পূর্বের ধারাবাহিকতাই বহন করছি। সরকার বদলালেও ঘৃণাত্মক, তুচ্ছার্থক ট্যাগ দিয়ে ভিন্নমতকে দমানোর রাজনৈতিক ধারায় গুণগত কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না।
যে যা নয়, তাকে সেই পরিচয়ে পরিচিত করার চেষ্টা সন্দেহাতীতভাবে অপরাজনীতি বলে গণ্য হবে। ট্যাগের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে সমাজের সচেতন মানুষ মাত্রই উদ্বিগ্ন। আশাজাগানিয়া এই প্রজন্ম আমাদের নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাতে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম। আমরা তরুণদের ওপর আস্থা রেখে বলতে চাই, সব এখনো শেষ হয়নি, নতুন করে দেশকে সাজানোর অনেক সুযোগ আমাদের রয়েছে। রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করে আমরা আমাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে উদ্যোগী হতে পারি। এই উদ্যোগের প্রথম কাজটাই হতে পারে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংস্কার।
ট্যাগের রাজনৈতিক সংস্কৃতির চূড়ান্ত পরিণতি দেখছে বাংলাদেশ। প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার অনেকেই। যারা খানিকটা প্রতিবাদী ছিলেন, তারাও ট্যাগের হাত থেকে বাঁচতে চুপ থাকছেন। এটাই ট্যাগ দেওয়ার সংস্কৃতির ভয়ংকর রূপ। এটি আমাদের জাতিগত বিভাজনকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিভেদ ও সংঘাত। এই ট্যাগের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। এর উপায় হতে পারে জাতীয় ঐক্যের একটা কমন গ্রাউন্ড তৈরি করা।
কিন্তু সেই প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকা-ের মাধ্যমে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সারাদেশে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ট্যাগ রাজনীতির আক্রমণ দেখা গিয়েছে। যেজন্য ভীতসন্ত্রস্ত সাংস্কৃতিক কর্মীরাও নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।
দেশের সৃজনশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের মানুষেরা রাজনৈতিক ট্যাগের বাইরে বেশি আক্রান্ত হন ধর্মকেন্দ্রিক ট্যাগে। ভিন্নমত পোষণের কারণে তারা রাজনৈতিক ট্যাগের বাইরেও অধিকতরভাবে নাস্তিক, কাফের, মুরতাদসহ ধর্মবিরোধী ট্যাগ পান। বিশেষত সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী ও উগ্রবাদীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা ধর্ম অবমাননা বা কটাক্ষের অভিযোগে অভিযুক্ত হন।
এসব ঘটনা রাজনৈতিক ট্যাগ সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন, এমনটাও নয়। এই শ্রেণির মানুষদের নাস্তিক আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যে হত্যার ঘোষণা ও হত্যার ঘটনাও বাংলাদেশে ঘটেছে। হঠাৎ করেই তা শুরু হয়নি। স্বাধীনতার পরপরই এমন পরিস্থিতির শুরু হয়। কালপর্বে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অপ্রত্যাশিত।
ভিন্নমত সহ্য না করা শাসক, শোষক এবং আধিপত্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার এ-এক স্বাভাবিক প্রবণতা। ধর্ম, বর্ণ কিংবা রাষ্ট্রÑ যে কোনো মোড়কেই শাসন এবং শোষণের প্রক্রিয়া যখন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, তখনই প্রকাশ ঘটে চূড়ান্ত অসহনশীলতার। সহনশীলতার অভাবে কথার প্রতিবাদ কথায় না হয়ে তা সহিংসতায় পৌঁছে যায়। ট্যাগের চাবুক তখন হাতিয়ার হয়ে বৈধতা এনে দেয় সংঘাতের। অসংহত ক্ষমতা, অনিরাপত্তার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বাতাবরণেই ট্যাগ সংস্কৃতির এস্টাবলিশমেন্টকে পোক্ত করা সম্ভব হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির মানবিক পাঠ থেকে দূরে থাকা প্রজন্ম ট্যাগ সংস্কৃতিকে নানা উপায়ে উপভোগ্য করে তোলে।
বিধায় আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ রাখলেই তাদের সেই চিত্র দেখতে পাই। এই প্রজন্মের একটা অংশের ট্রল, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, মিম সূক্ষ্মভাবে ট্যাগের প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করে। ট্যাগের এই প্রক্রিয়া ও ধরনকে নিয়ে গবেষণারও প্রয়োজন। নতুনদের ভাষাভঙ্গি ও ট্যাগ সংস্কৃতিকে ভালোভাবে বুঝে উঠতে না পারলে এই রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। ট্যাগের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেভাবে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে, তাতে সমাজে ভয়ংকর বিপর্যয় আসন্ন। কালক্ষেপণ না করে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা আবশ্যক।
আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে সহনশীলতা এবং ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পরিবার, সব জায়গায় মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের কর্মীদের মধ্যে এই মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করতে হবে। গণমাধ্যম এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। তাদের অবশ্যই মিথ্যা তথ্য এবং বিদ্বেষমূলক প্রচার রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা এবং ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনাকে উৎসাহিত করা অপরিহার্য।
শুধু ক্লিক বা ভিউ বাড়ানোর জন্য বিতর্কিত ট্যাগিংকে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মিথ্যা তথ্য ছড়ানো, চরিত্র হনন বা বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। যারা অনলাইনে বা অফলাইনে ট্যাগিং রাজনীতির মাধ্যমে সমাজের ক্ষতি করছে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে এই আইনগুলো যেন ভিন্ন মত দমনের হাতিয়ারে পরিণত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নাগরিক সমাজকে সচেতন হতে হবে। কোনো তথ্য যাচাই না করে শেয়ার করা বা কোনো গোষ্ঠীকে অন্ধভাবে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
নিজেদের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যখন কোনো নেতিবাচক ট্যাগিং দেখা যায়, তখন সেটিকে রিপোর্ট করা এবং সঠিক তথ্য তুলে ধরা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ট্যাগিং রাজনীতি পরিহার করে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।
রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে তাদের বক্তৃতায়, প্রচারে এবং অনলাইন কার্যক্রমে প্রতিপক্ষকে ট্যাগ না করে গঠনমূলক সমালোচনা এবং নিজেদের নীতি ও কর্মসূচির উপর জোর দেওয়া। সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু বিদ্বেষমূলক ট্যাগিং রাজনীতি নয়।
বাংলাদেশের রাজনীতিও এখন এক সংকটময় মোড়ে। বাংলাদেশেও ট্যাগিং প্রবণতা সাময়িকভাবে কাউকে সুবিধা দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি বিপজ্জনক। রাজনৈতিক দল, কর্মী ও মিডিয়ার বোঝা উচিত যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক। কিন্তু মিথ্যা তথ্য ও বিভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। রাজনীতিবিদদের উচিত বিভক্তি বাড়ানোর বদলে বাস্তব সমস্যার সমাধানে মনোযোগ দিয়ে শাসন, অর্থনীতি ও সমাজের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা।
জনগণ চায় এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ, যেখানে জনমতকে ভুল তথ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ না করে ভালো কাজের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। যদি এই বিভ্রান্তির রাজনীতি চলতে থাকে, তাহলে তা একসময় শুধু কোনো নির্দিষ্ট দলকে নয়, বরং পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করবে। সময় থাকতেই এই ভুল না শোধরানো দরকার। তা না হলে মানুষ রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর বিশ্বাস হারাবে এবং নিজেদের প্রয়োজনে ভিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তখন তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।
লেখক : শিক্ষার্থী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়