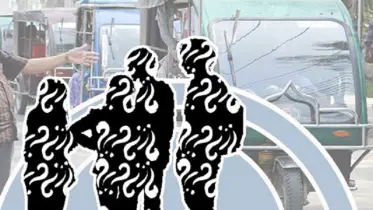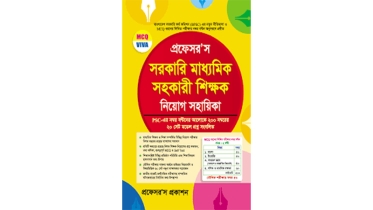রাষ্ট্র গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে।
ইংরেজি ‘কনটেক্সট’ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে অবস্থা বা পরিস্থিতি। এই নিরিখে সোশ্যাল কনটেক্স’-এর বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে সামাজিক পরিস্থিতি বা সামাজিক অবস্থা। যে কোনো একজন ব্যক্তির আচরণ, কথা, ব্যবহার সেই সামাজিক পরিস্থিতির নিরিখে হওয়ার দাবি রাখে। নরসিংদীতে নারীর পোশাক সম্পর্কিত ঘটনায় আদালতের বক্তব্যের সারবস্তু মূলত এটি। এখানে কিন্তু একটি বিষয় অনুহ্য থেকে গেছে।
আদালত তার পর্যবেক্ষণ এবং বক্তব্যে গুলশান- বনানীর বাস্তবতার সঙ্গে নরসিংদীর রেলস্টেশনের বাস্তবতার একটি তুলনা তুলে ধরেছে। তার মানে দাঁড়ায় গুলশান-বনানীর পরিস্থিতিতে এরূপ পোশাক সাযুজ্যপূর্ণ। একটি দেশের অভ্যন্তরের একই শাসনকাঠামোর এরূপ শ্রেণীকরণ কিভাবে যৌক্তিক হয়, সেটা উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। এক্ষেত্রে আমরা উপলব্ধির অপারগতা প্রকাশ করছি। আদালতে তার পর্যবেক্ষণে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেছে, নরসিংদীতে মেয়েটি যে পোশাক পরিধান করেছে, সেটি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় বলা জরুরি- আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কিন্তু তাঁর যাপিতজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় সভায় ‘কোটপ্যান্ট’ পরতেন না। জাতীয়তাবাদী নেতাগণ নিজের অজান্তেই জাতীয়াতাবাদকে মর্মে ধারণ করেন। ভুটানের রাষ্ট্রপতি যে পোশাক পরে নিজ দেশের কিংবা আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশ নেন, সেটি তার সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। বস্তুতপক্ষে সেটিই যৌক্তিক। রাষ্ট্র যদি একটি সমিতি হয়, সমিতির সভাপতি তার আচরণে ও প্রকাশে সমিতির অন্তর্ভুক্ত সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটাবেন, এটিই কাম্য।
ইউরোপ আমেরিকার রাষ্ট্র কিংবা সরকার প্রধানগণ সে দেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পোশাকই পরিধান করেন। তারা কোনোভাবেই আমাদের দেশের সমাজের পোশাক পরে সভায় অংশ নেন না। আমরা অলক্ষ্যেই তাদের আচরণ ও ধরন প্রকাশ করি। উপনিবেশের এটি একটি স্থায়ী প্রভাব। যেখানে সভাপতিই এটি করেন, সেখানে একজন সাধারণ নাগরিক যদি করে তবে তার দোষ কোথায়?
মানুষের শরীরে পোশাক উঠেছে সেই কবে। আদিম মানুষ বন্যজীবনে গাছের ছাল, পশুর চামড়া, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে শরীর আচ্ছাদন করত। সেই পর্যায় পার হয়ে মানুষ এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পোশাক মানবসভ্যতার একটি আবশ্যক উপাদান, যেমন খাবার একটি আবশ্যক উপাদান। বস্তুতপক্ষে পোশাক ছাড়া মানুষকে ভাবাই যায় না। পোশাক শরীরের ত্বকের মতোই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
শরীরে ত্বক যেমন জরুরি, পোশাকও তেমনি জরুরি। এই পোশাকবিন্যাস ও পোশাকপ্রকৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমষ্টি যে ভৌগোলিক স্থানে বাস করে, তার সেই ভৌগোলিক স্থানের প্রকৃতির ওপর। ভূমিরূপ, আবহাওয়া-জলবায়ু, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি উপাদানের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যক্তিসমষ্টির পোশাকের ধরন নির্ধারিত হয়। এ কারণেই ইউরোপের পোশাকের ধরন, মধ্যপ্রাচ্যের পোশাকের ধরন, বাংলাদেশের পোশাকের ধরন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বহমান।
এক্ষেত্রে পোশাকের নির্দিষ্টতা যুগপৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচারের ওপরও নির্ভর করে। প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষই তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক জীবনধারার উৎসজাত পোশাক বেছে নেয়। আমাদের বাস্তবতায় একটি বিষয় দেখা যায়, একজন ব্যক্তি ইউরোপ থেকে এসে সেখানকার পোশাক কোটপ্যান্ট পরে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসে জোব্বা পরিধান করে এবং এর পক্ষে যুক্তি দাঁড় করায়। কিংবা অন্য কোন অঞ্চলে কিছুকাল থেকে এসে সেখানকার পোশাক পরে প্রদর্শন করে।
বলা প্রয়োজন, ইউরোপ কিংবা আমেরিকা কিংবা অন্য অঞ্চলের মানুষ, যারা এ দেশে বিভিন্ন কারণে বসবাস করে, যাওয়ার পর আমাদের দেশের পোশাক দেশে গিয়ে আর পরে না। আমরা প্যান্ট-শার্ট পরি ইংরেজদের কাছ থেকে। ইংরেজরা দু’শ’ বছর এই দেশ শাসন করে গেলেও আমাদের পোশাকের কোন কিছুই গ্রহণ করেনি। এরই নাম দেশপ্রেম, এরই নাম জাতীয়তাবাদ। আগেই উল্লেখ করেছি, আমাদের দেশের রাষ্ট্র-সরকার প্রধানগণ (ব্যতিক্রম শাড়ি) যে পোশাক পরে পৃথিবীর নানা দেশে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই পোশাক কিন্তু আমাদের দেশের নয়।
সুতরাং, দেখা গেল পোশাকের কোন নির্দিষ্টতা আমাদের দেশে দাঁড়ায়নি। এই বিষয়টি বাস্তবিকভাবে আমাদের জাতীয়তাবাদ সংশ্লিষ্ট ভাবনাকে হাল্কা করে দেয়। আমরা দেখতে পাই যে, জাতীয়তাবাদের প্রবাদপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের পোশাক বিন্যাসটি মূর্ত হয়ে আছে নিজস্বতায়। জাতীয়তাবাদীগণ অলক্ষ্যেই নিজম্ব স্বাতন্ত্র্যতা ধরে রাখেন। রাষ্ট্র মানেই তো নিজস্বতা অর্জন। এই নিজস্বতা অর্জনের জন্যই যুগে যুগে-দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে।
সব বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে এমন কয়েকটি ধারার বিশ্লেষণ করা হলো। নরসিংদীর রেলস্টেশনের ঘটনাটি এবং একে কেন্দ্র করে আদালতের পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির পরিসর ছোট হলেও এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। এটি যে কোনোভাবেই বিশদ ও বিস্তৃত বিশ্লেষণধর্মী একটি বিষয়, যা সংবিধানের সাপেক্ষে একাডেমিক অনুসন্ধানের দাবি রাখে। আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার অংশে বর্ণিত কয়েকটি ধারা-উপধারা নরসিংদীর পোশাক ঘটনার সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হলো।
সংবিধানের মৌলিক অধিকার অংশের ২৮ (২) ধারায় বলা হয়েছে- রাষ্ট্র গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে। এটা যদি পোশাকের নিরিখে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে বলা যায় একজন পুুরুষ যদি যে কোনো পোশাক পরিধান করতে পারে, তবে সাংবিধানিক সেই সূত্রমতে একজন নারীও পারে।
অনুচ্ছেদ-৩২ আইনানুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। এই সূত্রে, নরসিংদীতে মেয়েটি তো সাংবিধানিক আইনের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেনি। মেয়েটি তার পছন্দের পোশাক পরে নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। রাষ্ট্র তাকে সেই সুযোগ দিয়েছে।
৩৬ অনুচ্ছেদে চলাফেরার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়নি কোনো নারী কিংবা পুুরুষ যখন চলাফেরা করবে তখন কোনো নির্দিষ্ট পোশাক পরতে হবে।
৩৯ অনুচ্ছেদে- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা অংশে বলা হয়েছে (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো। এই মতে নরসিংদীর মেয়েটি যদি এই যুক্তি উল্লেখ করে যে, তার পোশাক তার চিন্তার স্বাধীনতাবোধ থেকে উৎসারিত হয়েছে! তখন?
৩৯ (২) (ক) অংশে বলা হয়েছে- প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা সভ্যতার বিবর্তনের চূড়ান্ত উৎকর্ষ পর্বের অবস্থা নির্দেশ করে। যার স্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে আমাদের সংবিধানে। নরসিংদীর মেয়েটির পোশাক তার ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নির্দেশ করেছে যদি বলা হয়, তবে কি ভুল বলা হবে?
আমাদের সমাজ বাস্তবতায় দেখা যায়- হাটে, বাজারে, মেট্রোপলিটনের শপিং মলে, বিমানবন্দরে, রেলস্টেশনে ইত্যাদি নানাস্থানে অনেক তরুণ থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত ‘হাফপ্যান্ট’ পরে বিচরণ করে।
সেই পোশাকটি কি আমাদের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? এটি তো আমাদের সংস্কৃতি হতে পারে না। আমাদের দেশের মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ পরে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাড়ি পরে না। অথচ শাড়ি তো আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির পোশাক। শাড়ি না পরার কারণে কোন নারীকে তো কেউ হেনস্তা করে না। বস্তুতপক্ষে নরসিংদীর রেলস্টেশনে তথাকথিত আপত্তিকর পোশাকের জন্য আক্রমণকারী নারীটি আসলে পুরুষ। এটি হলো পুরুষতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা। বলা প্রয়োজন নারীদের মাধ্যমেও পুরুষতন্ত্রও মাত্রা পায়।
যেমন, এটি একটি অতি সাধারণ প্রত্যাশ্যা কোনো মেয়ে তার বিয়ের বেলায় যে পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে, সেই পুরুষকে তার থেকে বেশি বেতনের, বেশি শক্তির এবং বেশি প্রতিষ্ঠার অধিকারী হতে হবে। পুরুষতন্ত্রের চর্চা হয় নারীর অন্তরে অন্তরেও। নারী নিজেও জানে না যে, তার চিন্তা ও প্রত্যাশা কিভাবে দাসীর প্রকৃতি ধারণ করে। নরসিংদীর মেয়েটি একজন নারী দ্বারাও আক্রান্ত হয়েছে। এ জাতীয় প্রকৃতির অধিকারী হওয়ার ঐতিহাসিক কারণ আছে। সেই কারণ এখানে বিবৃত হলো।
আদি যুগেরও আগে, প্রাগ-ঐতিহাসিককালে, ঘর-সংসার, সমাজ-রাষ্ট্র হওয়ার বহু আগে আদিম অবস্থায় যখন মানুষ গুহায় বসবাস কিংবা যখন প্রকৃতিররাজ্যে বসবাস করত, তখন তাদের মুখ্য কাজ ছিল দুটি। এক. সংঘবদ্ধভাবে খাদ্য আহরণ করা এবং বন্যপশু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করা। সেই সময়ে সেই সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। নারীরা পুরুষের অধীন- এটি বহু বহু পরের বাস্তবতা। যখন থেকে মানুষের মধ্যে মালিকানার বোধ জেগে ওঠে, তখন থেকেই ক্রমান্বয়ে নারীরা পুরুষের অধীন হতে থাকে।
যখন থেকে বিয়ে ব্যবস্থা প্রবর্তন শুরু হয়, তখনই পুরুষের অধীন নারী এই প্রতিষ্ঠা শক্ত ভিত্তি লাভ করে। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বনের পশুপাখি শিকার করত এবং তা সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিত। যেসব ফলমূল সংগ্রহ করা হতো, সেগুলো নারীরা বসবাস স্থানের আশপাশে ফেলে রাখত এবং সেখান থেকে নতুন চারাগাছ জন্মাত। এভাবেই কৃষিকাজ নারীদের হাতে শুরু হয়। সেই সময়ে কোন বিয়ে ব্যবস্থা ছিল না। নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করত এবং এর ফলে যে সন্তান জন্ম নিত, তার কোন পিতৃত্ব ছিল না।
অর্থাৎ শিশুটি কোন্ পিতার তা নির্ণয় করা যেত না বলে মা-ই ছিল তার অভিভাবক। সেই সময়ে সন্তানের পরিচয় মায়ের পরিচয়ে হতো এবং মায়ের বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে শিশু বড় হতো। সেই সময়ের সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ছিল।
পরবর্তীতে ধাতুর ব্যবহার, গবাদিপশু পালন, কৃষির প্রচলন ইত্যাদির ফলে খাদ্য সংগ্রহসহ মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদান সহজতর হয়ে ওঠে। এর ফলে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে সমাজে বাড়তি বা উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি হয়। সমাজ চিন্তাবিদগণ ব্যাখ্যা করেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রসারের সময়ই নারীর বশ্যতা শুরু হয়, তখনই সারা দুনিয়ায় স্ত্রীজাতির পরাজয় ঘটে।
শ্রেণিবিভাজন এবং নারীর বশ্যতা দুটোই নির্দির্ষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুরুষতান্ত্রিক উত্তরাধিকার নির্বাচনের জন্য এ সময় নারী-পুরুষের বহুগামিতা নিষিদ্ধ হয়। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীরা কেবল একজন স্বামীর অধীনস্থ হয়। এর ফলে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয় করাও সহজ হয়ে যায়। যদিও পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার বলবৎ রাখা হয়। এভাবেই, নারীরা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পরিণত হতে থাকে।
উদ্ভব ঘটে বিয়ে এবং ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক পরিবারের, যা নারীর অধস্তনতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। এখানে বলা প্রয়োজন, শিকার ও সংগ্রহের যুগেই সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের প্রয়োজনে একদিকে নারীদের যেমন গৃহে খাদ্য সংগ্রহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, অন্যদিকে পুরুষ হয়েছে শিকারি। ঋতুচক্র, সন্তান জন্মদান, স্তন্যদান ইত্যাদি প্রকৃতিপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্য নারীর গতিশীলতাকে প্রভাবিত করেছে এবং তাদের হীনবল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পুরুষ সুযোগ নিয়েছে। যেমন, সন্তানদানের আগে ও পরে নারীগণ শারীরিকভাবে দুর্বল অবস্থায় থাকে।
বিধায় ভারী কাজ, শিকারের কাজ, দূরের কাজ করা সম্ভব হতো না। সেই সাময়িক দুর্বলতারই সুযোগ নিয়ে পুরুষ ধীরে ধীরে তাদের চিরস্থায়ী অধস্তনতায় নিয়ে গেছে। বিষয়টি আসলে একটি বড় ধরনের প্রবঞ্চনা। এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল নির্মাণ, ভুল প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। নরসিংদীর মেয়েটি ঐতিহাসিক সেই ভুল প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অসহায় শিকার।
লেখক : উন্নয়নকর্মী
[email protected]