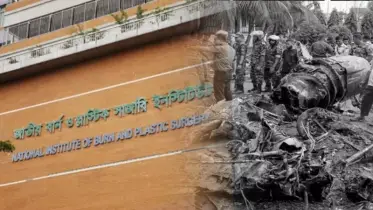.
যুগের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে চলচ্চিত্রের ধারা। বাংলাদেশেও এই ধারা প্রবহমান। পৃথিবীর চলচ্চিত্রের সূতিকাগার হিসেবে হলিউডকে মনে করা হয়। সেখানের চলচ্চিত্রের ধারা বদলালেও শিকড় থেকে বিচ্যুত হচ্ছে না। দিনকে দিন উন্নত হচ্ছে চলচ্চিত্র শিল্প। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্র এখানের সংস্কৃতির সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে বিগত বছরে দেশে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকটি চলচ্চিত্রকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের সংস্কৃতির জন্য এক প্রকার হুমকিস্বরূপ।
রায়হান রাফী পরিচালিত ‘তুফান’ চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ২০২৪ সালে। এতে গ্ল্যামারাইজ করা হয়েছে সন্ত্রাসকে। এটি শতাধিক খুন, প্রতিশোধ আর গতানুগতিক কাহিনীর প্রচলিত ধারার এক ছবি। ২০২৫ এর ৩১ মার্চ ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়া ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনার ছবি ‘বরবাদ’। এটিও ফর্মুলা রাঙানো সন্ত্রাস নির্ভর এক ছবি। হত্যা, সন্ত্রাস আর রক্তপাতের আধিক্যে ভরা শিশুদের নিয়ে না দেখার মতো এক ছবি। কথায় কথায় নায়কের কোকেন সেবন, সিগারেট বা মদ খাওয়া, জবাই করে কিংবা কুড়াল, পিস্তল, রাইফেল দিয়ে অগণিত মানুষ হত্যা আর ভিলেনের ছোট ভাইয়ের মুখে মুত্রত্যাগের দৃশ্যও রয়েছে এ ছবিতে। একই সঙ্গে ২০২৫ সালে ভিন্নধর্মী এক প্রশ্নের জন্ম দেয়ার ছবিও ‘তাণ্ডব’। দাবি করা হয়, সমাজ বাস্তবতা তুলে এসব ছবি নির্মাণ করা হয়। ‘পরাণ’ ছবির প্রচারে বাস্তব ঘটনার মিশেল বলা হয়েছিল, ‘দামাল’ ছবিটাও শতভাগ বাস্তবতা, অনুপ্রেরণা ও দেশপ্রেমের ছবি। সন্ত্রাস, খুন বা মারপিটের ফর্মুলা ছবি এ দেশে নির্মিত হতো মূলত হিন্দি ছবিকে মাথায় রেখে। হাল আমলের বাংলা ছবি দেখে মনে হয় এগুলো তামিল ছবির ছায়া, আমাদের গল্পের নয়।
তবে ঈদ কেন্দ্রিক এসব ছবি দেখার জন্য হলে দর্শকের আধিক্য বেশি দেখা যায়। এসময় অনেকে টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছে এমনও দেখা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এসব ছবি কি পরিবার নিয়ে, অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান, নিকট আত্মীয় নিয়ে দেখা যায়? ঈদের সময় বেশিরভাগ দেখা গেছে অল্প বয়সী তরুণরাই বেশি হলে ভিড় করে। ফলে এসব ছবি দেখে তারা অনুপ্রাণিত হয় মাদক সেবন ও সন্ত্রাসে।
আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের ইতিহাস খুবই ঐহিত্যপূর্ণ ছিল। ফলে দেশে বৃদ্ধি পেয়েছিল সিনেমা হল। প্রায় ১৪শ’ হলেই প্রতি সপ্তাহে ভিড় লেগে থাকত। মাঝে কিছু অসাধু লোকের জন্য এই চলচ্চিত্র শিল্প মুখ থুবড়ে পড়ে। হলের সংখ্যা কমতে কমতে এখন সচল একশ’রও কম। কিন্তু সম্প্রতি আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা এই শিল্পের।
দেশের সিনেমা হলগুলো কেন বন্ধ হচ্ছে এমন প্রশ্নে রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী সিনেমা হল মধুমিতার কর্ণধার ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সাবেক সভাপতি ইফতেখার উদ্দিন নওশাদ জনকণ্ঠকে বলেন, মধুমিতা সিনেমা হল ঐহিত্যের প্রতীক। কষ্ট হলেও এ ঐতিহ্যকে এখনো ধরে রেখেছি। দর্শক নেই সে কারণে আপাতত হল বন্ধ। তিনি বলেন, ভালো ছবির অভাব। ভালো কোনো কন্টেন্ট নেই। মাত্র দুই ঈদে ছবি আসে, অন্য সময় নেই, এভাবে তো আর চলচ্চিত্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব না। তিনি বলেন, ঈদের পরে দুই একটা ছবি এলেও খুবই নি¤œমানের। এগুলো দর্শক দেখে না। আগেতো আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে এমন অবস্থা ছিল না। আমি মনে করি আমাদের দেশে অনেক মেধা আছে, ছবি তৈরির সামর্থ্যও আছে কিন্তু প্রডিউসাররা এখন টাকা খরচ করতে চান না। ফলে হল সংখ্যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। পয়সা লগ্নি করলে তা আর উঠে আসে না। এখন হল টিকিয়ে রাখতে হলে সুপার ডুপার ছবি বানাতে হবে, নচেত ভবিষ্যতে আরও সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাবে। সারাদেশে সকল হল মালিকদের কষ্ট হচ্ছে। পকেটের টাকা খরচ করে হল টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে তাই অনেক সময় মাথা গরম হয়ে যায় তাই হয়তো বলে ফেলি হল রাখব না। তার মানে এই না সত্যি সেটা করছি।
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রধান উপদেষ্ট সুদীপ্ত কুমার দাশ জনকণ্ঠকে বলেন, আমাদের দেশে কেন সিনেমা হল বন্ধ হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে কিছুটা পেছনে ফিরে যেতে হবে। আমাদের দেশে সিনেমার সোনালী দিনে হলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১২৩৫টার মতো। সর্বশেষ ১৯৯২ থেকে ৯৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বোর্ডের সিহাব অনুযায়ী হল মালিকরা রেগুলার ট্যাক্স পে করত। পরবর্তিতে এর সঙ্গে ভ্যাট যোগ করা হলো। শুল্ক ও ভ্যাট মিলে একশ’ তেরো শতাংশ করা হয়। যে কারণে সিনেমা হলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি আকাশ উন্মুক্ত করে দিল অর্থাৎ কোনো রকম কোনো নিয়ম নীতিমালা অনুসরণ না করেই ডিস এন্টেনার মাধ্যমে টেলিভিশনে ছবি দেখার সুযোগ করে দেওয়া হলো। ১৯৯৪/৯৫ সালের দিকে এসে এটা যখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেল, সিনেমার দর্শক যারা পরিবার নিয়ে অথবা একসাথে দশ পনেরো জন মিলে হলে গিয়ে নিয়মিত সিনেমা দেখত, সেই দর্শক হলে আসা বন্ধ করে দিল। কারণ, ঘরে বসে ভারতীয় অনেক জনপ্রিয় ছবি দেখার সুযোগ পেল দর্শক। ভারতীয় ছবির অনুকরণে আমাদের দেশের ছবি দেখার তেমন আগ্রহ দর্শকের ছিল না। তবে মাঝে মধ্যে হলে দর্শক আসত, যখন যে ছবিগুলো ছিল একেবারে মৌলিক ও স্যোসাল সেন্টিমেন্টের সেগুলো ফ্যামিলি দর্শক দেখত। কিন্তু সেটার পরিমাণ একেবারেই কম। যে কারণে সিনেমা হলের ইনকাম কমতে থাকে। পাশাপাশি সরকারি ট্যাক্স আদায়ও কমতে থাকে। আমাদের কাছে যে হিসাব আছে তাতে দেখা যায়, ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে ট্যাক্স আদায় কমতে থাকে। ২০০০ সালে এসে একেবারে ২০ শতাংশে নেমে যায়। এই অবস্থায় ২০০২ সাল থেকে সিনেমা হল বন্ধ হওয়া শুরু হয়। যখন হল বন্ধ হওয়া শুরু হলো তখন আমাদের ছবিগুলোর জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। কারণ ডিস এন্টেনা দিয়ে যে ছবি দেখে, সেই ছবিরই রিমেক দেখে হলগুলোতে। সেই কারণে দর্শকের আকর্ষণ হলের প্রতি অনেক কমে গেল। ফলে এক শ্রেণির প্রযোজক ও পরিচালক এই দুর্বলতার সুযোগে নোংরা যাকে বলে অশ্লীল ছবি তৈরি শুরু করে। এতে প্রথমে কিছু ভালোগার দৃশ্য থাকত, যে অংশ সেন্সরবোর্ড কেটে দিত, সেই দুশ্যগুলো চুপচাপ প্রিন্টের সঙ্গে জুড়ে দিত। এভাবেই শুরু হলো অশ্লীল নোংরা ছবির রাজত্ব। এক পর্যায়ে সরাসরি শূট করত অশ্লীল দৃশ্য। এগুলো ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দিত। ছবিগুলো যখন সিনেমা হলে চালানো শুরু হলো, তখন ফ্যামিলি দর্শক টোটাল হলবিমুখ হয়ে গেল। এটা আমাদের চলচ্চিত্রটাকে ধস নামিয়ে দেয়। এটাই হচ্ছে প্রধান কারণ। পরে পাইরেসিসহ আরও কিছু কিছু বিষয় আছে। দুদিন পরেই টিভিতে দেখা যেত পাইরেটেড ছবি। লোকাল ছবিগুলো দারুণভাবে লোকসানের মুখে পড়ে যায়। এ কারণেই আমাদের এই ব্যবসাটা মুখ থুবড়ে পড়ে।
চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন উজ্জ্বল জনকণ্ঠকে বলেন, চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরে আসছে আমরা মনে করছি। তার কারণ কিছু কিছু ছবি এখন বেশ ভালো হচ্ছে, যা দর্শককে হলমুখী করছে। তবে এটা দুই ঈদ কেন্দ্রিক হয়ে গেছে। আমরা আশা করছি এবার ঈদে ভালো ভালো ছবি আসবে। যদি আসে তাহলে নতুন করে হলগুলো খুলবে। এরকম যদি সারাবছর চলে তাহলে হলগুলোকে ধরে রাখা সম্ভব হবে।
শুধুমাত্র ঈদের জন্য ছবি দিল প্রযোজকরা কিন্তু ঈদের পরে আর ভালো কোনো ছবি না থাকে তাহলে তো হল ধরে রাখা যাবে না। আমরা প্রযোজকদের কাছে ও পরিচালকদের কাছে অনুরোধ করব দর্শক যাতে হলে গিয়ে ছবি দেখতে পারে তারা যেন সারাবছর এরকম ভালো ভালো ছবি তৈরি করে। আমরা হল থেকে সার্বিক সহযোগিতা করব। পাশাপাশি বলব শুধু ঈদের ছবি দিলে হবে না, সারাবছর ছবি দিতে হবে।
প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্র শিল্পকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে সপরিবারে দেখা যায় এমন গল্প নির্ভর ভালো ভালো ছবি নির্মাণ করতে হবে। শুধুমাত্র মাদক ও সন্ত্রাসকে প্রাধান্য দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করলে আবারও এই শিল্প ধ্বংসের কবলে পড়বে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা।
প্যানেল