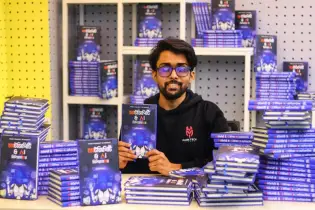ছবি: প্রতীকী
বর্তমান ডিজিটাল যুগে মানুষ খুব দ্রুত তথ্য পেতে চায়। সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ বা টিকটকের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমরা নানা খবর, ছবি ও ভিডিও দেখছি। এর ভেতর অনেক তথ্য সত্য হলেও অনেক কিছুই ভুল, বিকৃত বা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনেক সময় পুরনো ছবি বা ভিডিওকে নতুন করে পরিবেশন করা হয়, আবার ইচ্ছাকৃতভাবে স্ক্রিনশট এডিট করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। ফলে মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, আতঙ্কিত হয় বা কাউকে দোষী ভাবতে শুরু করে। তাই এখন সবচেয়ে জরুরি হলো ফেক নিউজ ও এডিটেড স্ক্রিনশট চেনার উপায় জানা।
প্রথমেই বুঝে নিতে হবে, ফেক নিউজ মানে শুধু মিথ্যা খবর নয়, বরং আংশিক সত্য তথ্যও ফেক নিউজ হতে পারে। কেউ হয়তো সত্য ঘটনার সঙ্গে মিথ্যা তথ্য মিলিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করে যাতে পাঠকের মনে ভুল ধারণা তৈরি হয়। যেমন: একটি ভিডিওর মাঝখান থেকে কিছু অংশ কেটে এমনভাবে দেখানো যে মনে হবে কেউ খারাপ কিছু বলেছে, অথচ পুরো ভিডিও দেখলে দেখা যাবে তিনি সেটি বলেননি। আবার কোনো সত্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করাও ফেক নিউজের আওতায় পড়ে।
ফেক নিউজ বোঝার জন্য প্রথমেই দেখতে হবে সূত্রটি কী। যেসব পেজ বা ওয়েবসাইট আগে থেকেই মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়, তাদের খবর বিশ্বাস না করাই ভালো। কোনো খবর দেখে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে খোঁজ নিতে হবে। বড় পত্রিকা, স্বীকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সেই খবর আছে কি না, তা যাচাই করা দরকার।
এছাড়া কিছু সাধারণ লক্ষণ থাকে যেগুলো দেখে সন্দেহ করা যায় খবরটি সত্য নয়। যেমন: শিরোনাম অতিরঞ্জিত, চটকদার বা ভীতিকর হলে, যেমন “এইমাত্র খবর...”, “সতর্ক হোন”, “সরকার গোপন তথ্য ফাঁস করল” — এসব শুনলেই সাবধান হওয়া উচিত। কারণ এসব শিরোনাম সাধারণত ক্লিক করানোর জন্য বানানো হয়, যাকে বলে "ক্লিকবেইট"। এমন খবর অনেক সময় মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর হয়।
এডিটেড স্ক্রিনশট চেনার ক্ষেত্রেও কিছু লক্ষণ থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি বা সেলিব্রেটি কিছু বলেননি, অথচ তার নামে মিথ্যা বক্তব্য বা পোস্ট ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের স্ক্রিনশট তৈরি করা খুব সহজ। ফটোশপ, মোবাইল অ্যাপ বা এডিটিং সফটওয়্যার দিয়ে খুব সহজেই ফেসবুক, টুইটার বা ইউটিউবের স্ক্রিনশট বানানো যায়। আপনি যদি কোনো স্ক্রিনশটে টাইম, তারিখ বা লেখার ফন্টে অস্বাভাবিক কিছু দেখেন, তাহলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কোনো মন্তব্য বা পোস্ট খুব চটকদার বা অবিশ্বাস্য মনে হলে সেই প্রোফাইলে গিয়ে যাচাই করা দরকার সত্যিই এটি বলা হয়েছে কি না।
অনেক সময় ফেক স্ক্রিনশটে ভুল বানান, অতিরিক্ত গাঢ় কালার বা অদ্ভুতভাবে কাটা ছবি দেখা যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে ছবির পেছনে অন্য কিছু থাকলেও সেটি ব্লার করে দেওয়া হয় যাতে আসল তথ্য গোপন থাকে। যদি স্ক্রিনশটটি বিতর্কিত কোনো বক্তব্য নিয়ে হয়, তাহলে সেটি নিজের চোখে না দেখে শেয়ার করা উচিত নয়।
বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো ছবিকে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখা যায় এটি আগে কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে। যদি দেখা যায়, ছবিটি অনেক আগের বা অন্য দেশের ঘটনার, তাহলে বোঝা যায় এটি বর্তমান ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।
এছাড়া এখন অনেক ফ্যাক্ট-চেকিং ওয়েবসাইট রয়েছে যারা প্রতিদিন ফেক নিউজ শনাক্ত করে। বাংলায় যেমন "ফ্যাক্ট-ওয়াচ", ইংরেজিতে "AltNews", "BoomLive", ইত্যাদি। এসব সাইটে সন্দেহজনক খবর বা ছবি দিয়ে খোঁজ করলে তারা আগে সত্য-মিথ্যা বিশ্লেষণ করে দিয়েছে কি না তা দেখা যায়।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজের ভেতরে সচেতনতা গড়ে তোলা। যে কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে নিজে একবার যাচাই করে নেওয়া। শুধু নিজের নয়, অন্যদেরও উৎসাহিত করা যেন তারা যাচাই না করে কিছু শেয়ার না করে। কারণ একটি ফেক নিউজ বা স্ক্রিনশট মুহূর্তেই অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, কারো সম্মান নষ্ট করতে পারে, এমনকি হিংসাত্মক পরিস্থিতিও সৃষ্টি করতে পারে।
তাই প্রযুক্তি যেমন আমাদের সামনে অসংখ্য সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি দায়িত্বও বেড়েছে। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য চিনে নেওয়া এখন আমাদের নাগরিক দায়িত্বের অংশ। সচেতন থাকলে, যাচাই করলে এবং নিজের বিবেক অনুসরণ করলে আমরা ফেক নিউজ ও এডিটেড স্ক্রিনশটের ধোঁকা থেকে নিজেকে এবং অন্যদের রক্ষা করতে পারি।
এম.কে.