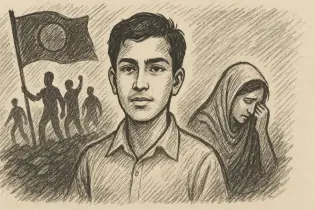.
৭৫০-১১৬১ খ্রিস্টাব্দ গোপালদেব ও তাঁর বংশধরগণ সুদীর্ঘ চারশত বছর প্রাচীন গৌড়-বঙ্গ ও মগধে রাজত্ব করেছেন। তাঁদের রাজত্বকালের ধারাবাহিক কোনো নির্ভরযোগ্য, তথ্যভিত্তিক ইতিহাস নেই। এ সময়ে নালন্দাসহ বরেন্দ্রভূমিতে অসংখ্য বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল; এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বৌদ্ধ পন্ডিতদের রচিত ঠাসা ছিল শতশত ধর্মীয় ছাড়াও মূল্যবান গ্রন্থরাজি। তৎকালীন সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজাদের শাসন আমলের বর্ণনা ছিল গ্রন্থগুলোতে। তাঁদের রাজ্য অবসানের সময়েই হামলা চালিয়ে বিহারগুলো ধ্বংস করা হয়; অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয় এসব মূল্যবান গ্রন্থরাজি। বহির্শত্রুর হামলায় বৌদ্ধ পন্ডিতরা কিছু গ্রন্থ নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নেপালে পালিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পরে পন্ডিত গবেষকরা সেসব নেপালের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার থেকে উদ্ধার করে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত পুঁথি, মূর্তি, মুদ্রা, তাম্রশাসন ও শিলালিপি ইত্যাদির পাঠ উদ্ধার করে বৌদ্ধ শাসন আমল সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের উদ্ধার ও গবেষণা পুঁজি করে আলোচ্য নিবন্ধটি সাজানো হয়েছে।
চর্যাপদ বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো নমুনা। চর্যাপদের পুরো নাম চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়। এগুলো বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত গান। শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপালে গিয়ে কোনো কোনোটার সামান্য পরিবর্তিত রূপে দেখতে পান। সেই গানগুলো এবং সেরকমের আরও কিছু গান তিনি রেকর্ড করে আনেন। এই গানগুলোর মধ্যদিয়ে একেবারে প্রাচীন বাংলা ভাষা এবং তার ঠিক আগেকার ভাষার নমুনা পাওয়া যায়, অন্যদিকে জানা যায় সেকালের সমাজের কিছু খবর। নেপাল থেকে একান্নটি চর্যা পাওয়া গেলেও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশটির; তবে আশ্চর্যের বিষয় বংালাদেশের কোনো অঞ্চল থেকে নয়, সুদূর নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে এগুলো উদ্ধার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ‘হাজার বছরের পুরনো বাংলা গান ও বৌদ্ধ দোহা’ নামে এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (১৯০৯) ; তিব্বতি টিকা থেকে এগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। বাংলা ভাষার এই নমুনাগুলো বঙ্গদেশে পাওয়া গেল না; পাওয়া গেল নেপালে। এর কারণ নিয়ে প-িতেরা নানা রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৌদ্ধরা যখন বাংলা ছেড়ে নেপালে পালিয়ে যান, তখন তারা গ্রন্থ ও গানগুলো সঙ্গে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক নেই। এমনকি প্রতিকূল পরিবেশে অথবা নির্যাতনের মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন; এ নিয়েও বিশেষ মতভেদ নেই। তবে কখন তারা দেশ ছাড়েন সেটা নিশ্চিত নয়। যদি বলা হয় সেন আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করেন, তা হলে তাকে অযৌক্তিক মনে হয় না। তবে দোষটা পড়ে হিন্দু রাজাদের ওপর। অপর পক্ষে যদি বলা হয় তারা দেশ ছাড়েন ইন্দো-মুসলিম শাসন আমলে তখন দোষের ভাগি হন মুসলিম শাসকরা। এই শাসকরা বৌদ্ধদের বিহার ধ্বংস করেছিলেন এবং অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন; এর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে; এই আমলে বৌদ্ধরা প্রাণ ভয়ে নেপাল, ভুটান যাওয়া অব্যাহত রেখেছিলেন, এ কথা বললেই বোধ হয় সঙ্গত হয়। তবে তাদের দেশত্যাগ সেন আমলে আরম্ভ হয়েছিল বলে মনে করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ এই আমলেই ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান এবং বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয়। (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি— গোলাম মুরশিদ, পৃষ্ঠা—২৬৭)
সেনরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাঁরা বৌদ্ধ অধ্যুষিত এই বাঙলাদেশে নতুন করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সমাজ, আচার রীতি-নীতি, বর্ণানুগ, শ্রেণিবিন্যাস প্রভূতি অত্যুৎসাহে রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সমাজ ও নিম্নবিত্তের মানুষ তাদের হাতে পীড়িত হয়। এ কালের নাথ-যোগী (তাঁতি) ধর্ম ঠাকুরের পূজারি, সহজযানী, মীননাথ-গোরক্ষনাথপন্থি বিভিন্ন শাখার বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্নভাবে শূদ্ররূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রান্তে ঠাঁই করে নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। বৌদ্ধদের নির্বাণ ও সাম্যের সমাজ এভাবে বর্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিণত হয়। ফলে এ সমাজের এক বৃহৎ অংশ মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্বের ও লাঞ্ছিতের অভিশপ্ত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। শূদ্রাদি অস্পৃশ্যের এবং নিম্নবিত্তের পেশাদারি শ্রেণির লেখাপড়ার অধিকার হরণ করা হয়। কৃত্রিম বর্ণবিন্যাসের ফলে উচ্চবিত্তের অধিকাংশ মানুষ যেমন আভিজাত্য গৌরব লাভ করে, তেমনি এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব কোন্দল ও সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে (১৩ শতক) বাংলায় ছিল ব্রাহ্মণ ও ছত্রিশবর্ণের শূদ্র ও বর্ণশঙ্কর বা মিশ্ররক্তের। (বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য—আহমদ শরীফ, পৃষ্ঠা-২৫)
গৌড় ও মগধ বিজেতা তুর্কি সমরনায়ক মুহম্মদ বখতিয়ারের অত্যাচার নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ মিহহাজ-ই সিরাজ। সুলতান মহম্মদ কর্তৃক চৌহান গহডবাল রাজ্য বিজিত হলে বখতিয়ার অর্থোপার্জনের চেষ্টায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। বখতিয়ার যখন সৈন্যদল নিয়ে গোবিন্দপালের রাজধানী আক্রমণ, তখন মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে নগর রক্ষা মগধ রাজের পক্ষে অসম্ভব দেখে সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সধর্ম ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। উদন্তপুর নগরের গিরিশীর্ষে অবস্থিত সঙঘারাম দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত এই সঙগারামে আশ্রয় গ্রহণ করে গোবিন্দপাল মুষ্টিমেয় সৈন্য ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সাহায্যে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন; সে চেষ্টা সফল হয়নি। তখন আর্যাবত্তের কোনো রাজা মগধেশ্বরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন নাই। উদন্তপুর, সঙগারাম অধিকৃত হলে সসৈন্য গোবিন্দপাল নিহত হন।
দুর্গ অধিকৃত হলে দেখা গেল যে, সেটি একটি বিদ্যালয়; সেখানে রাশি রাশি গ্রন্থ সঞ্চিত আছে। কিন্তু তখন দুর্গরক্ষী সৈন্য ও ভিক্ষুগণ নিহত হয়েছে। মগধ দেশে এমন কেউ ছিল না যে, বিজেতৃগণের কৌতূহল নিবারণার্থ ওই সকল গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করতে পারে। এইরূপে ধর্মপাল ও দেবপালের বিশাল সম্রাজ্যের অবসান হয়। গোবিন্দপাল নিহত হলে মগধদেশ মহম্মদ-ই- বখতিয়ারের পদানত হয়। বিজেতার আদেশে উদন্তপুর ও বিক্রমশীলা বিহারের শতশত বর্ষব্যাপী যত্নে অমূল্য পুস্তকরাজি ভস্মীভূত হয়। বিজেতৃগণের অত্যাচারে দলে দলে নর-নারী-শিশু মগধ পরিত্যাগ করে পর্বতসঙ্কুল দেশ বিশেষ করে নেপাল-ভুটানের দিকে রওনা দেয়। সঙ্গে নিয়ে যায় অমূল্য ধর্মগ্রন্থনিচয় ও দেবমূর্তিসমূহ। এ কারণে পরবর্তীতে নেপাল ও ভুটানে পাল রাজগণের বহু বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। মগধ জয়ের পরে তুর্কি সমরনায়ক বখতিয়ার বঙ্গ ও কামরূপ পর্যন্ত দখল বিস্তৃত করেন। দিল্লি হতে প্রত্যাবর্তন করে বখতিয়ার সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। তিনি গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করেন; অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নদীয়া নগরে উপস্থিত হন। নগরবাসী প্রথমে তাঁকে অশ^বিক্রেতা বণিক মনে করেছিল। তিনি প্রসাদে উপস্থিত হয়ে অবিশ^াসীদিগকে আক্রমণ করেন। এ সময় রায় লখমনিয়া আহার করছিল। মুসলমানগণের আগমন শুনে মহিলা-পুরুষ সকলেই ধন-রত্ন-সম্পদ, দাস-দাসী পরিত্যাগ করে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়ে বঙ্গে পলায়ন করেছিলেন।
ইতিহাসবিদ মিনহাজ গৌড় বিজয়ের চত্বারিশৎ বর্ষ পরে নিজামউদ্দিন ও সমসামউদ্দীন নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বখতিয়ারের বিজয় কাহিনী শুনেছিলেন। মিনহাজ ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী নগরে, গৌড়ে সমসামউদ্দীনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন (বাংালার ইতিহাস রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা, ২২০.২২১,২২২)। নালন্দার উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। কারণ বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন নালন্দাতে আসেন তখন সেখানে কোনো বৌদ্ধবিহার বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। (বি এন মিশ্র, নালন্দা সোর্সেস অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড, খন্ড- ১)। গুপ্তযুগে নালন্দা বিহার থেকে মহাবিহারে রূপান্তরিত হয়েছিল মূলত রাজকীয় অনুদানের দ্বারাই। আর কোনো মহাবিহার নালন্দার মতো রাজকীয় অনুদান পায়নি। পাল রাজারাও ছিলেন নালন্দার পৃষ্ঠপোষক। এই পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী আর নালন্দা ছিল তাদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র; যার ফলে তারা মুক্তহস্তে এই প্রতিষ্ঠানে দান করত। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ উৎখননে ধারণা হয়েছে, এখানে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী আবাসিকভাবে বসবাস করত। ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে ইৎ-সিং নামে এক বৌদ্ধ চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক নালন্দা পরিদর্শন করেন। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ স্বয়ং নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে পড়াশোনা করেন। (আর সি মজুমদার, এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, দিল্লি, ১৯৭৪)।
ঐতিহাসিক কে কে কানুনগোর ‘জানাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এ প্রকাশিত শরৎচন্দ্র দাশের অ্যান্টিকুইটি অফ চিটাগাঁও’ প্রবন্ধ অনুযায়ী কামিরের বৌদ্ধ পন্ডিত শাকা শ্রীভদ্র ৬৭০ খ্রিস্টাব্দের পরে মগধে গিয়ে দেখেছিলেন যে বিক্রমশীলা ও উদন্তপুরী বিহার ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুর্কিদের ভয়ে শ্রীভদ্র ও ওই বিহার দুটির ভিক্ষুরা বগুড়া জেলার জগদ্দল বিহারে আশ্রয় নেন। শরৎচন্দ্র দাশ তাঁর ওই প্রবন্ধে বলেন, বিক্রমশীলা ও উদন্তপুর বিহার দুটি ধ্বংস করা হয়েছে; তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস অবস্থায় ও উদন্তপুরীকে তুর্কি সামরিক ঘাঁটিরূপে দেখতে পান। এছাড়া সপ্তম শতকের মাঝামাঝি মগধে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের শিকারও হতে পারে নালন্দা। ঐতিহাসিক এস এন সদাশিবন নালন্দা ধ্বংসের জন্য মুসলমান ও ব্রাহ্মণ্যদের দায়ী করেছেন। (এস এন সদাশিবন এ সোসাল হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া, নিউদিল্লি, পৃষ্ঠা- ২০৯)। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার সোমপুর বিহার ধ্বংস হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে। একাদশ শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ চন্দ্রবংশ উৎখাতিত হয়ে অবিভক্ত দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মণ রাজবংশ। এই বংশেরই শাসক ছিলেন জাতবর্মা। তিনি সোমপুর বৌদ্ধবিহারে হামলা চালিয়ে লুণ্ঠন করেন; অবশেষে অগ্নি সংযোগ করে বিহারটি ভস্মীভূত করেন। (এগ্রিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খন্ড-২১) ওই বিহারের মঠাধ্যক্ষ বৌদ্ধ পন্ডিত কক্ষণাশ্রী মিত্রকেও অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেন (এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খন্ড-২১)
‘রামচরিত’ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপালে আবিষ্কৃত হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণীতে রামচরিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী নেপাল থেকে সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থ এবং অর্দ্ধগ্রন্থের টিকা এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য এনেছিলেন। এই গ্রন্থ এখন কলকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। রামচরিত মূল ও টিকা তালপত্রে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত। মূলগ্রন্থ অপেক্ষা টিকার অক্ষর প্রাচীন বলে বোধ হয়। এই টিকাতেই রামপালের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। (বাংলার ইতিহাস, ১ম খন্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা—১৮)
প্রাচীন আমলের বরেন্দ্রভূমির সীমানা বর্তমানে অনেকটাই খন্ডিত। বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুরের কিয়দংশ বরেদ্রভূমির সীমানা হিসেবে গণ্য করা হয়। পালদের শাসন আমলে অনান্য জেলার চেয়ে বৃহত্তর দিনাজপুর ছিল বৌদ্ধ অধ্যষিত অঞ্চল। প্রত্নতত্ত্ববিদ আ কা মো যাকারিয়া ১৯৬৮ সালের দিকে দিনাজপুরের জেলা প্রশাসকের দায়িত্বে থাকাকালীন জেলার দক্ষিণাঞ্চলীয় উপজেলা পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাটে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ অনুসন্ধান চালান। এ সময় এ অঞ্চলে অসংখ্য ঢিবি, স্তূপ তার চোখে পড়ে। কৃষি কাজে মাটি সমান করায় এগুলো নিচিহ্ন হয়ে গেছে। ১৯৬৮ সালে নবাবগঞ্জ উপজেলার ফতেপুর- মাড়াস মৌজায় জঙ্গালাকীর্ণ একটি বৃহৎ ঢিবি খননে সীতাকোট বিহার উন্মোচিত করা হয়। খুব সম্ভব পঞ্চম শতাব্দী কি তার পরে এ বিহার নির্মিত হয়েছিল।
পরবর্তীতে এটি পরিত্যক্ত হয়। এ সময়ে বিরামপুর উপজেলায় অবস্থিত চোরচক্রবর্তীর ধাপে উৎখনন চালায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। এই ঢিবির আয়তন প্রায় ১১৫ মিটার ঢ১০০ মিটার। সামান্য উৎখনননে ইমারতের যে কাঠামো বের হয়, তাতে ধারণা করা হয় এখানে একদা প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ছিল। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ১২ কি, মিটার দ, পূর্বে মামুদপুর ইউনিয়নের চকজুনিদ-চকদিয়ামত মৌজায় এক সময় অসংখ্য ঢিবি ছিল। এখনও ৩০টি ঢিবির অস্তিত্ব বিদ্যমান। তার মধ্যে অরুনধাপে ১৯৮৩—-৮৪ সালে প্রত্মতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রত্মতাত্ত্বি খনন কার্য করা হয়। খনন পরিচালনা করেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ^বিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক স্বাধীন সেন। তার ধারণা এই স্থাপত্যটি একটি বৌদ্ধস্তূপ। নির্মাণকাল আনুমানিক ৭ম—১১শ শতাব্দীর মধ্যে হতে পারে। এর আগে তাঁর (স্বাধীন সেন) নেতৃত্বে একটি দল বিরামপুরের চন্ডিপুর ও সুন্দলপুরে খনন কাজ পরিচালনা করেন। এতে চন্ডিপুরে একটি মন্দির ও সুন্দলপুরে বৌদ্ধ স্তূপের অবশেষ পাওয়া গেছে। ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড, অরুন নাগ ও ড, শীলা পাঁজা এ এলাকার পুরাকীর্তি সাইট ও খনন স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। এগুলো বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁরা মনে করেন।
২০২১ সালের ৩০ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ইসবপুর মৌজার ধাপের হাটের স্তূপটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও প্রত্মতত্ত্ব অধিদপ্তরের অর্থায়নে ও বেগম রোকেয়া বিশ^বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যৌথভাবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সোহাগ আলীর নেতৃত্বে উৎখনন করা হয়। এ যাবত এ অঞ্চলে যতগুলো প্রত্ন সাইট উৎখনন করা হয়েছে তা অর্থাভাবে সম্পন্ন করা হয়নি; তাই সেগুলো পলিথিন দিয়ে মুডিয়ে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। ইদানীংকালে প্রাচীন পুকুর পুস্করিণী, বিল-ঝিল, নদীতে কাল পাথরে (আগ্নেয় শিলার ব্লাক ব্যাসল্ট) নির্মিত বৌদ্ধ মূর্তি শিলালিপি ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের নারী-পুরুষ-শিশু সম্মিলিত বৌদ্ধ পরিবাররা বহির্শত্রুর আক্রমণে তাড়িত হয়ে ঘন বনজঙ্গল পেরিয়ে উত্তর দিকে হিমালয়ের পাদদেশ নেপাল-ভুটানের দিকে রওনা দেয়। এ সময় পূজার্থে ব্যবহৃত মূর্তিসমূহের যাতে অমর্যাদা না হয় সে কারণে এগুলো জলে বিসর্জন দিয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে। ধারণা করা যায় দিনাজপুর, রংপুর, পঞ্চগড় সীমান্ত পেরিয়ে তারা দেশ ত্যাগ করেছে। ওই সময়ের বৌদ্ধ শরণার্থীদের সঙ্গে বাংলাদেশে একাত্তরে জীবন রক্ষার্থে ভারতে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? প্রশ্ন জাগে বৌদ্ধ অধ্যুষিত এই অঞ্চল কি কারণে বৌদ্ধ শূন্য হয়ে গেল; কারা গ্রন্থগারসহ বিহার ধ্বংশ করল, তা শুধুই ইন্দো -মুসলিম শাসন আমলে ও সেনবংশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার-নির্যাতনেই তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে নাকি আরও অন্য কারণ আছে, ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব।