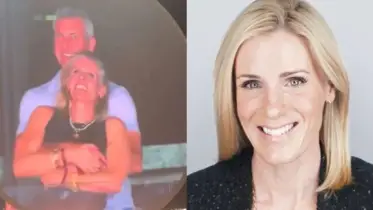বৈশাখের হালখাতার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের এবং জিনিসপত্রের দরদামের নিবিড় একটা সম্পর্ক থাকে। সবাই জানেন, এ সময়ে গ্রাম-গঞ্জে মেলা বসে; হাট-বাজার নানাবিধ গৃহস্থালি নিত্যপণ্যে সয়লাব হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন গৃহস্থরা প্রায় সারা বছরের হলুদ-মরিচ, চাল-ডাল, তেল-নুন কিনে থাকেন পাইকারি দরে। আজকাল অবশ্য এর প্রচলন কমে এসেছে অনেকটাই। কেননা বেচাকেনা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ধরন অনেক পাল্টেছে। বর্তমানে ঘর-গৃহস্থালির নিত্যপণ্য প্রায় সারা বছরের জন্য কিনে মজুদ করতে চান না কেউ। আমদানি-রফতানি অনেক সহজ এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় শুধু শহর-বন্দরে নয়; এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রায় সবই পাওয়া যায় পাইকারি ও খুচরা দরে। ছোট-বড় নানা প্যাকেটে। তদুপরি বাজার প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় দরদামেও তেমন হেরফের পরিলক্ষিত হয় না। তবু মাঝে-মধ্যে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী কিছু চাহিদাসম্পন্ন পণ্যের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে দাম বৃদ্ধির অপপ্রয়াস চালান। সচরাচর এটা হয়ে থাকে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর অতি মুনাফা প্রবৃত্তির কারণে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে এই শ্রেণীর আধিপত্যই তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবরও আছে বৈকি। আজকাল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় মুহূর্তে সে খবর ছড়িয়ে পড়ে দেশে ও বহির্বিশ্বে। এর ফলে স্বভাবতই নড়েচড়ে বসে সরকার। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর নেতাদের সঙ্গে তড়িঘড়ি করে বৈঠকের পর বৈঠক করে কিছু পদক্ষেপ নেয়। খোলাবাজারে ট্রাকে করে অথবা বিকল্প উপায়ে জরুরী ভোগ্যপণ্য, খাদ্যশস্য বিক্রির ব্যবস্থা করে। ব্যবসায়ীরা লোক দেখানো হলেও কিছু সান্ত¡নার বাক্য শোনান। তবে ততদিনে মুনাফার নামে বাজার থেকে হাতিয়ে নেয়া হয় কোটি কোটি টাকা। মুক্তবাজার অর্থনীতির এ এক তেলেসমাতি খেলা।
সত্যিকারের মুক্তবাজার অর্থনীতির দেশগুলোতে যেমনÑ আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় এমনটা কখনই সম্ভব হয় না। সেখানে নিয়মিত খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ব্যবসায়ীদেরও একটা সততা ও নৈতিকতা থাকে। আমাদের দেশে যার বালাই নেই। সে জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালুর চেষ্টা চললেও প্রায়ই সরকারী খবরদারি, নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়ে। তবে সেসব ক্ষেত্রেও প্রায়ই দেখা যায় যে, ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে যেমন মুনাফা লুটে নেন, তেমনি সরকারকেও নানা ফন্দি-ফিকিরে নয়-ছয় বুঝিয়ে আদায় করে নেন অনেক সুযোগ-সুবিধা। অর্থাৎ তারা একদিকে যেমন গাছেরও খান, তেমনি তলারও টোকান। আর অতি মুনাফা লোটার হীন মনোবৃত্তি তো আছেই।
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ তথা গ্রীষ্মের প্রচ- দাবদাহের প্রভাব নিত্যপণ্যের বাজারে অনুভূত হবে না, এমন তো হতে পারে না। অতঃপর ধান ও চাল ছাড়া প্রায় সব নিত্যভোগ্যপণ্যেই একটা তেজিভাব তথা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে চালের ব্যাপারেও একটা কথা আছে। গত কয়েক বছর ধরে সরকারের কৃষিনীতি তথা কৃষকের প্রাণপণ শ্রমের বিনিময়ে হলেও মোটামুটি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। তবে দুঃখজনক হলো, কৃষক তার উৎপাদিত ধান-চালের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। প্রধানত আমলাতান্ত্রিক কারণে সরকারের ক্রয়নীতির আদৌ কোন সুফল পাচ্ছেন না প্রান্তিক কৃষকরা। বরং এই সুবিধার ফল ভোগ করছে মধ্যস্বত্বভোগী তথা চাতাল মালিকরা। অন্যদিকে দেশে যেমন একদিকে প্রচুর চাল উৎপাদিত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রচুর চাল আমদানিও হচ্ছে, বিশেষ করে ভারত থেকে। বেসরকারী খাতে এই চাল আমদানি করছেন ব্যবসায়ীরা। প্রায় সব দেশেই তিন বছর পর পর সরকারী খাদ্যগুদাম খালি করে দেয়ার বিধান রয়েছে। ব্যবসায়ীরা সেই নিম্নমানের চালই আমদানি করছেন ভারত থেকে এবং দেশীয় বাজারে তা বিক্রি করছেন। এই বিপুল পরিমাণ চাল আমদানিও হচ্ছে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এলসি খুলে। সরকার সব জানে, সব বোঝে। তারপরও আদৌ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অন্যদিকে সরকারী খাদ্যগুদাম খালি করে দেয়া হচ্ছে নতুন ধান-চাল সংগ্রহের অভিপ্রায়ে। এসবই নিম্নমানের চাল। সাধারণ মানুষ তাই কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন। মাঝখানে সরকার দশ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে চালের দাম আরও কমে যাওয়ার ভয়ে সম্ভবত তা থেকে পিছিয়ে এসেছে আপাতত। সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ বাজারে ধান-চালের মূল্য নির্ধারণসহ বেচা-বিক্রিতে সরকারের একটি সুষ্ঠু সমন্বিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি প্রণয়ন এবং অনুসরণ করা দরকার। ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছ আমদানি বন্ধের পাশাপাশি দেশে উন্নতমানের ধান-চাল উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে যথেষ্ট ভাল কাজ করেছে। তবে তারা যেন উফশীর পাশাপাশি মানসম্মত চাল উৎপাদনে গুরুত্বারোপ করে। তা না হলে আগামীতে বিশ্ববাজার থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ব।
আরও একটা কথা। কেবল ধান-চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে তো কোন লাভ নেই। অন্যবিধ ফসল যেমন ডাল, পাট, তৈলবীজ, গম ইত্যাদি উৎপাদনের দিকেও সবিশেষ নজর দিতে হবে। বর্তমান বাজারে মসুর ডালের দাম অত্যন্ত চড়া। অথচ দেশে ভাল মসুর ডাল উৎপাদন হয় না। আমদানি করতে হয় নেপাল, তুরস্ক ও অন্য দেশ থেকে। অন্যান্য ডালও হয় খুব কম। রমজানের একটি নিত্যভোগ্যপণ্য বুট বা ছোলা। বেশ দাম। চাহিদা মেটাতে হয় আমদানি করে। অথচ দেশেই উৎপাদন সম্ভব। বর্তমানে বেশ কয়েকটি ভোগ্যপণ্যের মোড়কে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়ায় চাহিদা বেড়েছে পণ্যটির। অথচ পাটের উৎপাদন কমছে দিন দিন। কোন একদিন যদি কাঁচাপাট আমদানি করে বস্তা বানাতে হয় তাহলে তা হবে নিতান্তই লজ্জার। আসলে আমাদের উৎপাদিত বিবিধ কৃষিপণ্যের চাহিদার সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নেই। ফলে ভাঁড়ারে টান পড়ে প্রায়ই। যেমন পেঁয়াজ, প্রতিবছর বিশেষ করে রমজান এলে এই পণ্যটির চাহিদা ও গুরুত্ব সম্যক বোঝা যায়। অথচ দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন হয় খুব কম। প্রতিবছর রমজানে গরম মসলা যেমনÑ এলাচি, গোলমরিচ, আদা, রসুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা ইত্যাদির চাহিদা বেড়ে যায় বিপুল পরিমাণে। চাহিদা মেটাতে হয় বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় করে আমদানির মাধ্যমে। অথচ সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এলাচ, গোলমরিচ, দারুচিনি, রসুন, আদা ইত্যাদি উৎপাদনের সম্ভাবনা বিপুল। অন্তত না হওয়ার কোন কারণ নেই। কেরালা এবং তামিলনাড়ুর আবহাওয়া ও অঞ্চল অনুরূপ। যতদূর জানি, বগুড়ায় একটি সরকারী মসলা গবেষণা ইনস্টিটিউট আছে। তবে তাদের আদৌ কোন কার্যক্রম সারাবছরেও দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলে স্বভাবতই এখাতে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে মুনাফা লুটে নিচ্ছে ব্যবসায়ী আমদানিকারকরা। এ যেন একেবারে ছেড়ে দে মা লুটেপুটে খাই। আমাদের মুক্তবাজার অর্থনীতি যেন অনেকটা লুটেপুটে খাওয়ার অর্থনীতি, যা একেবারে সম্প্রসারিত ব্যাংক-বীমা থেকে শুরু করে পাইকারি ও খুচরা বাজার পর্যন্ত। আর সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে যেন শিখ-ীর। আর জনগণ আষ্টেপৃষ্ঠে জিম্মি।
সেদিন একটি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত দৈনন্দিন বাজার সম্পর্কিত সচিত্র প্রতিবেদন দেখে চমকে উঠলাম। সাধারণ স্তরের ক্রেতারা, যাদের মধ্যে আছেন গৃহিণীরাও, বলছেন তারা গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে আপাতত শাক-সবজির দিকে ঝুঁকছেন। বাজারের মাছ অবশ্য অধিকাংশই পচা, ফরমালিন ও বরফ দেয়া সত্ত্বেও, বিশেষ করে গুঁড়াগাড়া মাছ। নেহাত প্রোটিন খেতে হলে ঝুঁকছেন মাংস ও ডিমের দিকে। সেটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। যদিও দাম চড়া। ঠাটারীবাজারের মতো বড় পাইকারি ও খুচরা বাজারে মানসম্পন্ন এক নম্বর বাচ্চা গরুর মাংস প্রতি কেজি কমবেশি ৪৫০ থেকে ৪৮০ টাকা। আবার গড়পড়তা ৪০০ থেকে ৪২০ টাকায়ও পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশই মহিষের মাংস। ওই বাজারের কসাইখানায় প্রতিদিন দলে দলে মহিষ ঢোকে আর খোলাবাজারে বিক্রি হয় গরুর মাংস হিসেবে। কসাইদের চরিত্র বোঝা ভার। তারা বুঝি মানবচরিত্রে অমর নাট্যকার শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অব ভেনিসের চরিত্র শাইলককেও হার মানাতে প্রস্তুত। মহিষের মাংস, গরুর মাংস তারা আলাদাভাবে বিক্রি করতেই পারেন। অনুরূপ খাসি বকরি, ছাগল ও ভেড়ার মাংস। তা তারা কিছুতেই করবেন না। সাধারণ ক্রেতার কাছে যে মাংসের চাহিদা সর্বাধিক এবং দামও বেশি, সে হিসেবেই বিক্রি করবেন। অর্থাৎ ক্রেতাদের সর্বতোভাবে ঠকাতে তারা প্রস্তুত। সুতরাং মহিষের মাংস হয়ে যায় গরুর মাংস। বকরির মাংস বিকোয় খাসির মাংস হিসেবে। তার মানে ক্রেতারা দামেও ঠকছেন একদিকে; অন্যদিকে প্রতারিত হচ্ছেন কাক্সিক্ষত পণ্য থেকে। আর ওজনের কথা কী বলব? গ্রাহকদের ওজনে ঠকানো এদেশে একটি বহুচর্চিত পেশা। সেইসঙ্গে ভেজাল। তবে এ নিয়ে অন্য কোন একদিন লিখব। এমনিতে আমরা বাজারে গিয়ে মহিষ কিংবা ভেড়ার মাংস কিনতে গিয়ে দেখেছি কসাই প্রথমে মাথা ঝাঁকিয়ে না করেন। অর্থাৎ তিনি মহিষ কিংবা ভেড়ার মাংস বেঁচেন না। তবে অর্ডার দিলে কাক্সিক্ষত পশু সংগ্রহ করে জবাই করে দেবেন। দাম পড়বে ভাল গরু কিংবা খাসির মাংসের সমান। বুঝুন ঠ্যালা। কত ধানে কত চাল! গরুর মাংসের দামের ঠ্যালায় খাসির মাংসের দাম বলতে ভুলে গেছি। বর্তমানে প্রতি কেজি ভাল মানের খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায়। গরু ও খাসির মাংসের উচ্চমূল্যে দাম বেড়েছে ব্রয়লার মুরগিরও। আর দেশী জাতের মুরগি তো কুলীন হয়েছে অনেক আগেই। অর্থাৎ ধরাছোঁয়ার বাইরে। বাকি রইল ডিম। না, ডিমের বাজারেও আপাতত কোন সুসংবাদ নেই। গরমে ডিম পচে যায় বলে দাম চড়া। আর পচা ডিমের চালান অধিকাংশ চলে যায় কনফেকশনারিতে রুটি-বিস্কুট-কেক তৈরিতে।
গরু ও খাসির মাংসের উচ্চমূল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মিলল মজার তথ্য। এমনিতে গরুর মাংসের দাম চড়তে শুরু করেছে ভারত থেকে চোরাপথে গরু আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই। তবে এই উচ্চমূল্যে সর্বশেষ অবদান ঢাকার হাজারীবাগের। সবাই জানেন, হাজারীবাগ থেকে ট্যানারিগুলো সাভারের চামড়া শিল্প নগরীতে সরিয়ে নেয়া নিয়ে সরকারের সঙ্গে ট্যানারি মালিকদের নানা টালবাহানা ও লুকোচুরি খেলা চলছে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনাও রয়েছে। অনেকবারই সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। অনেকবার তা অমান্যও করা হয়েছে। সর্বশেষ, হাজারীবাগে কাঁচা চামড়া ঢোকার ব্যাপারেও আরোপ করা হয়েছে পুলিশি বাধা ও নিষেধাজ্ঞা। তবে সকলই গরল ভেল। হাজারীবাগ থেকে সাভারে চামড়া শিল্প স্থানান্তরে দেখা দিয়েছে প্রায় স্থবিরতা। সর্বশেষ, হাজারীবাগ ট্যানারি সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি, তারা ঈদুল আজহা তথা কোরবানির ঈদের এক মাসের মধ্যে চলে যাবেন সেখানে। তবে আপাতত সেখানে কাঁচা চামড়া প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করায় এর প্রভাব পড়েছে মাংসের দামে। কেননা কসাইরা চামড়ার দাম পড়ে যাওয়ায় সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চাচ্ছে মাংসের দাম বাড়িয়ে। কেননা কসাইকে তো শেষ পর্যন্ত চামড়াসমেত আস্ত জ্যান্ত গরু বা খাসিটি কিনতে হয় দাম দিয়েই। সুতরাং চামড়া বিক্রি করতে না পারলে বা কম দামে বিক্রি করতে হলে সে লাভালাভ তুলবে গ্রাহককে জবাই করেই।
অন্যদিকে, অপ্রিয় হলেও সত্য যে, হাজারীবাগ থেকে চামড়া শিল্প সাভারে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি শুরু থেকেই সুষ্ঠু, সমন্বিত ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় করা হয়নি। চামড়া শিল্প সরানোর অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল বুড়িগঙ্গাকে বাঁচানো। কেননা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত নানা রাসায়নিক পদার্থ যেমনÑ ক্রোমিয়াম, সালফিউরিক এসিড, লবণ ইত্যাদি মিশ্রিত কঠিন ও তরল যাবতীয় বর্জ্য গিয়ে পড়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে। ফলে তা নদী দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রতিকারে সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপন করা হচ্ছে বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)। তা না হয় হলো। কিন্তু যেসব শ্রমিক চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে জড়িত তাদের কি হবে? কাজটা যেহেতু টেকনিক্যাল এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রমিক প্রয়োজন, সেহেতু তাদের পুনর্বাসন না করে কীভাবে চামড়াশিল্প স্থানান্তর সম্ভব? সাভারের হেমায়েতপুরে ১৯৯ দশমিক ৪০ একর স্থানে মোট শিল্প প্লটের সংখ্যা ২০৫, যা বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫৪টি ট্যানারিকে। এসব কারখানার সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার শ্রমিক ও পরিবার-পরিজন। শুধুই কি তাই! আরও আছে চামড়াশিল্প সংশ্লিষ্ট কেমিক্যাল ব্যবসায়ী, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারক, রফতানিকারক ও কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী, ট্যানারি প্রকৌশল ও অন্য ৮টি উপখাত সংশ্লিষ্ট সমিতি ও সংগঠন। তাদের জন্য আবাসন, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ইত্যাদি আবশ্যক। মোট কথা, শ্রমিকদের বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত কীভাবে যে একটি পরিবেশবান্ধব চামড়াশিল্পনগরী গড়ে তোলা সম্ভব হবে, তা বোধগম্য নয় কিছুতেই। সুতরাং হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে চামড়াশিল্পনগরী স্থানান্তরে এখনই বসতে হবে সবাইকে নিয়ে, সব পক্ষের সঙ্গে। তা না হলে এর স্বল্পমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী দুর্ভোগ পোহাতে হবে সবাইকেÑ চামড়ার দাম সংযুক্ত অতিরিক্ত দাম দিয়ে গরুর মাংস কিনে সাধারণ ক্রেতাকে পর্যন্ত। জানি না, মুক্তবাজার অর্থনীতির এটাই নিয়ম কিনা!
ঢাকা, বাংলাদেশ শনিবার ১৯ জুলাই ২০২৫, ৩ শ্রাবণ ১৪৩২