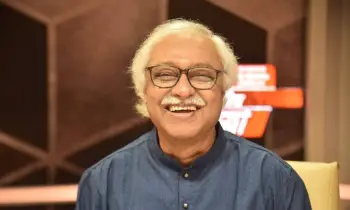ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। এই আলোচনা কেবল রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নয়, বিস্তৃত হয়েছে সাধারণ মানুষ, শিক্ষিত তরুণ সমাজ, বিশ্লেষক ও নাগরিক সমাজের মধ্যেও। এ আলোচনা ঘিরে একটাই প্রশ্ন—বাংলাদেশে কি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা বা Proportional Representation (PR) পদ্ধতি চালু করা উচিত?
বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে প্রথম-প্রাপ্ত-প্রথম (First Past the Post - FPTP) পদ্ধতি। যেখানে একটি আসনে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান, তিনিই জয়ী হন। তবে এই ব্যবস্থার একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো—একটি দল ৩০-৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭০-৮০ শতাংশ আসন পেয়ে যেতে পারে। আবার অন্য একটি দল ২০ শতাংশ ভোট পেয়েও একটি আসন পর্যন্ত পায় না। ফলে বিশাল একটি ভোট কার্যত অপচয় হয়ে যায়। এই অপচয় ঠেকাতে প্রস্তাব আসে PR পদ্ধতির—যেখানে একটি দল যত শতাংশ ভোট পায়, সে অনুপাতে আসন পায়।
এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ভোটের ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়, সংসদে মতের বৈচিত্র্য থাকে, সংখ্যালঘু বা ছোট দলগুলোও প্রতিনিধিত্ব পায় এবং ভোটারের মর্যাদা রক্ষা পায়। তবে এই সুবিধাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ নির্ভর করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও দলীয় আচরণের ওপর।
বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো—দলগুলো এখনো দলীয়ভাবে গণতান্ত্রিক নয়। মনোনয়ন চলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে, মাঠের কর্মী-সমর্থকের মতামত সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। PR পদ্ধতিতে যেহেতু সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন দলীয় তালিকা অনুযায়ী, তাই এই কেন্দ্রীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়া আরও দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে ত্যাগী ও জনসম্পৃক্ত নেতার পরিবর্তে সুবিধাবাদী, বিতর্কিত ও লবিংনির্ভর ব্যক্তিরাই অধিকতর প্রাধান্য পান।
আরেকটি গুরুতর সমস্যা হলো—জনগণ ও জনপ্রতিনিধির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ PR পদ্ধতিতে ভোট দেওয়া হয় প্রতীক বা দলকে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নয়। ভোটার জানতেও পারবেন না, তাঁর প্রতিনিধি কে? এই প্রতিনিধিত্ব কেবল কাগজে থাকবে, বাস্তবে নয়। এতে দায়বদ্ধতা কমে যাবে এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনগণের দাবি পৌঁছানো কঠিন হয়ে উঠবে।
সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এই পদ্ধতিতে মাত্র ১-২ শতাংশ ভোট পেলেই কোনো দল সংসদে প্রবেশ করতে পারে। এই সুযোগে উগ্রপন্থী, ধর্মান্ধ কিংবা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সংসদে ঢুকে রাজনৈতিক ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
PR পদ্ধতিতে সাধারণত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কঠিন হয়, ফলে সরকার গঠনের জন্য দরকার পড়ে জোট। আর জোট মানেই আপস, সমঝোতা, ভাগাভাগি ও ক্ষমতার লেনদেন। এসবের ফলে একটি দুর্বল ও অনিশ্চিত সরকার গঠিত হয়, যা প্রশাসনের ধারাবাহিকতা ও সুশাসনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।
তবে এও ঠিক যে, এই পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাজ্য নয়। অনেক দেশেই এটি সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছে—বিশেষ করে যেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিণত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শক্তিশালী, এবং দলগুলো জবাবদিহিমূলক আচরণ করে। বাংলাদেশে যদি দলগুলো গণতান্ত্রিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়, মনোনয়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয় এবং দলীয় শৃঙ্খলা জনগণের মতামতের প্রতি সংবেদনশীল হয়—তাহলে ভবিষ্যতে আংশিক বা সংকর PR পদ্ধতি চালুর কথা ভাবা যেতে পারে।
তবে বর্তমান বাস্তবতায় সবচেয়ে জরুরি হলো—জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যেই দরকার তৃণমূল নেতৃত্বকে মূল্যায়ন, স্বাধীন প্রার্থীদের সুযোগ, এবং জনপ্রতিনিধিকে জনগণের কাছেই জবাবদিহি করার ব্যবস্থা। ভোট যেন শুধু সংখ্যা নয়, বরং হয়ে ওঠে আস্থার প্রতীক।
গণতন্ত্র তখনই টিকে থাকে, যখন জনগণ বিশ্বাস করে—তাদের ভোটেই ঠিক হবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। সেই বিশ্বাস অটুট রাখতে হলে দরকার এমন নির্বাচন ব্যবস্থা, যেখানে জনগণই হবে কেন্দ্র, দল নয়।
আসিফ