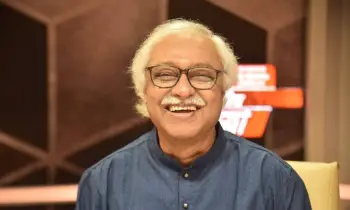.
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে পদ্ধতিগত দিক নিয়ে কোনো পক্ষ নেবে না সরকার। সরকার চায়, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করুক তারা কোন্ পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে চায়। ফলে ড. বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত ‘নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন’ তাদের দীর্ঘ প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত সুপারিশ করা থেকে বিরত থেকেছে। এমতাবস্থায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন গতানুগতিক পদ্ধতিতে হবে, না-কি সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে হবে তা নির্ভর করছে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ওপর।
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন তার প্রতিবেদনে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা এবং পিআর পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেও আগামী নির্বাচন কোন্ পদ্ধতিতে হবে, সে সম্পর্কে কোনো সুপারিশ করেনি। সুপারিশের জায়গায় বলা হয়, ‘রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবের কারণে নির্বাচন পদ্ধতি পরির্তনের বিষয়ে কোনোরূপ সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিষয়টি সম্পর্কে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সম্মানিত রাজনীতিবিদদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই যৌক্তিক বলে আমরা মনে করি।’
যদিও জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি এখন আলোচনার কেন্দ্রে। দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি পিআর পদ্ধতির কঠোর বিরোধিতা করছে। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ কিছু রাজনৈতিক দল এই পদ্ধতির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এ নিয়ে দলগুলোর পক্ষে-বিপক্ষের বক্তব্য রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫৫টি। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে চারটি দলের নিবন্ধন বাতিল রয়েছে এবং আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত রয়েছে। ফলে, ৫০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৮টি দল পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের পক্ষে। বিপক্ষে অবস্থান ২৮টি দলের। চারটি দল তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। কিছু দল আংশিকভাবে এই পদ্ধতির পক্ষে। বিপক্ষে থাকা দলগুলো মূলত বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের সঙ্গী। এর বাইরে জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) পিআর পদ্ধতির পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। মূলধারার ইসলামী দলের মধ্যে পাঁচটি দল পিআর পদ্ধতির পক্ষে, দুটি বিপক্ষে এবং দুটি দল অবস্থান পরিষ্কার করেনি।
কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই একটি রাষ্ট্রে দায়বদ্ধতামূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুই ধরনের দায়বদ্ধতা বিরাজমান। একটি নিম্নমুখী দায়বদ্ধতা, আরেকটি সমান্তরাল দায়বদ্ধতা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে যদি ভোটের জন্য জনগণের দোরগোড়ায় ধরনা দিতে হয়, তাহলেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন ও অন্যান্য অপকর্মে লিপ্ত হওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে এবং তাদের জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে কাজ করতে হয়। কারণ, অপকর্ম ও জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়লে জনগণের পক্ষে সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হবে। এভাবেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নিম্নমুখী দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়।
সমান্তরাল দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় কমিটি ও অন্যান্য সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের সল্ডিয় হওয়া সম্ভব হয় এবং তারা নির্বাহী বিভাগকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। সরকারের পক্ষে তখন আর অন্যায় এবং অপকর্ম করে পার পেয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। একইভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নগ্ন দলীয়করণের শিকার হয় না এবং তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে সকল সরকারি কার্যল্ডমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তাই গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।
বাংলাদেশে বর্তমানে আসনভিত্তিক ‘ফাস্ট পাস্ট দ্য পোস্ট’ (এফপিটিপি) বা আসনভিত্তিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি একটি জনপ্রিয় এবং অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি। আমাদের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে “একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য” নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দেশের আইনসভার নির্বাচনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটার অনেক প্রার্থীর মধ্যে একজনকে ভোট প্রদান করেন এবং যিনি বেশি ভোটে এগিয়ে থাকেন তিনিই বিজয়ী হন।
এফপিটিপি বা আসনভিত্তিক পদ্ধতির অনেক গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে মন্তব্য করে কমিশন রিপোর্টে বলা হয়, যার অন্যতম হলো এ পদ্ধতিতে অনেক সময় রাজনৈতিক দল তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে আসন পায় না। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের হার কাছাকাছি হলেও তাদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যায় প্রায়শই ব্যাপক তারতম্য ঘটে। ফলে, এ ব্যবস্থায় প্রাপ্ত আসনের সংখ্যায় দলের জনসমর্থনের যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না। বাংলাদেশের অতীতের চারটি নির্বাচনের (পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম) ফলাফল। যে নির্বাচনগুলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত এবং দেশি-বিদেশি পর্যক্ষেকদের কাছে কম-বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।
দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি গ্রাফ প্রদর্শন করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রায় সমসংখ্যক ও সমহারের ভোট পেলেও তাদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যায় ব্যাপক তারতম্য ঘটে। বিএনপি প্রায় এক কোটি পাঁচ লাখ বা ৩০.৮১ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৮০ আসন পেলেও আওয়ামী লীগ প্রায় এক কোটি দুই লাখ বা ৩০.০৮ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ৮৮টি আসন পায়। একই ধরনের ড্রামাটিক বা নাটকীয় বিভাজন বরং আরও বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম এবং ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও দুই প্রধান দলের মধ্যে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ও ভোটের হারের সঙ্গে ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়, যাতে তাদের জনপ্রিয়তার প্রতিফলন ঘটেনি। অর্থাৎ বিদ্যমান পদ্ধতিতে সংসদে রাজনৈতিক দলের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।
কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, এটি সুস্পষ্ট যে, বিদ্যমান আসনভিত্তিক এফপিটিপি পদ্ধতির কারণে সামান্য ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েও সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়। আর এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে আমাদের সরকারগুলো ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে অতীতে একাধিকবার সংবিধান সংশোধন করেছে, যা আমাদের দেশে ‘টিরানি অব দ্য মেজরিটি’ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার সৃষ্টি করেছে। নারী আসনে আমাদের বিদ্যমান সংরক্ষণ পদ্ধতিও যে পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসন প্রত্যেক দলের ভোট প্রাপ্তির অনুপাতের পরিবর্তে, সংসদে তাদের সদস্য সংখ্যার অনুপাতে ভাগ করা হয়Ñ সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন স্বৈরাচার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের চরম ফ্যাসিস্টে পরিণত হওয়ার এটিও একটি কারণ।
আসনভিত্তিক এফপিটিপি পদ্ধতির প্রতিনিধিত্বশীলতার সমস্যা এবং এর সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতির পাশাপাশি আরও গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের তাদের নিজ সংসদীয় আসনে আধিপত্য সৃষ্টির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তাদের পক্ষে স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ তৈরি হয়। বস্তুত, আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বহুলাংশে সংসদ সদস্যদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যদিও এটি সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের লঙ্ঘন।
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা তাদের জাতীয় অঙ্গীকারও উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, যে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তার মূল অঙ্গীকার ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে রচিত সংবিধানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার সুষ্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়, যার পূর্বশর্ত হলো সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমেও আমরা জাতি হিসেবে সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। গণতান্ত্রিক এবং শোষণ-বৈষম্যহীন শাসন কায়েমের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারগুলো এখনও বহুলাংশে অধরাই রয়ে গেছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ও কার্যকর কাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং বিধি-বিধান তৈরি করতে পারিনি। বরং যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান ছিল, তাও আমরা একে একে অকার্যকর, এমনকি ধ্বংস করে ফেলেছি। নির্বাচনকে আমরা নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সততা ও ন্যায়-নীতিবোধকে চরমভাবে বিসর্জন দিয়েছি। এই প্রক্রিয়ায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক চরম কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদের ওপর সওয়ার হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ওই ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদের পুরো জাতির ওপর অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়েছে। মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে চরমভাবে পদদলিত করেছে। গোষ্ঠীতন্ত্র, চোরতন্ত্র ও কোটারি স্বার্থ চরিতার্থ করার মাধ্যমে এক চরম বৈষম্যমূলক সমাজ সৃষ্টি করেছে, বাংলাদেশকে একটি দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। এ সকল অনাচার, অবিচার ও বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যেই ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান। চরম জালিয়াতির নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত দখলদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পলায়ন আমাদের জন্য বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।