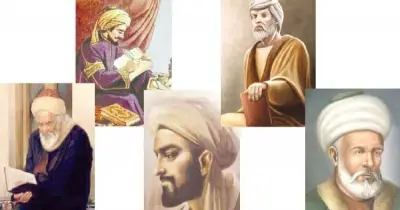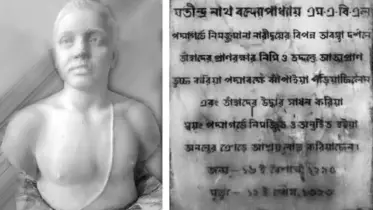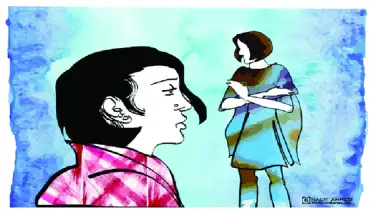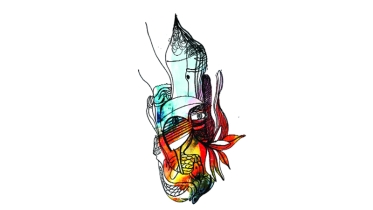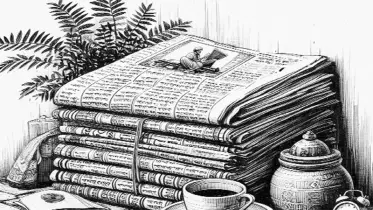এক হাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া
এক হাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলোবাতাসে শীতবোধ করিয়া, ‘বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গনেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে।’ ভরা বর্ষায় প্রতিরাতে ইলিশ ধরেই চলে কুবের মাঝিদের জীবনযাপন। ইলিশের মৌসুম শেষ হলেই বিপুল পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়।
নৌকা-জাল সবই মহাজনের, তাই যেটুকু মাছ ধরা পড়ে তার অর্ধেকটা মহাজনের আর বাকি অর্ধেকটা দুজনে ভাগাভাগি করে নেয়। রাতে মাছ ধরা শেষে ভোরবেলায় গঞ্জের আড়তে মাছ বিক্রির কাজটা মহাজনই করে থাকে। ভাগের অঙ্কে ফাঁকি থাকলেও কিছুই করার থাকে না কুবের মাঝিদের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে জেলে কৈবর্তদের জনজীবনকে অসামান্য দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন।
নদী, হাওড়-বাঁওড়, জলাভূমি বেষ্টিত এই বাংলায় জালিক কৈবর্ত সমাজ যুগ যুগ ধরে তাদের পেশায় টিকে আছে। বর্ণাশ্রম প্রথায় বর্ণবহিস্থ বা অন্ত্যজ শ্রেণীর এই পেশাজীবী মানুষেরা জীবন জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত বিপদের সম্মুখীন হয়। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। মহাজনী ঋণের আবর্তে ঘুরপাক খায় তাদের জীবন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই দারিদ্র্যের সঙ্গে লডাই করতে হয় তাদের।
বাংলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতিমান কথাশিল্পীর রচনায় এই কৈবর্ত জনজীবন উঠে এসেছে সংগ্রামী মানুষের জীবনধারার প্রতীক হিসেবে। কৈবর্ত পুরুষের পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলো প্রেম ও দৃঢ়তায় টিকে থাকার লড়াইয়ে সাহসী সঙ্গী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। ‘ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণার দেবতা, হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।’
এভাবেই দারিদ্র্যে জর্জরিত পশ্চাৎপদ সমাজে লৌকিক প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে চলে তাদের জীবন। সমাজের ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে তারা অচ্ছুত, শূদ্র,আবার প্রকৃতির রুদ্ররোষের শিকার হয় তারাই। রোগ-শোকে মৃত্যু আর টিকে থাকার লড়াইয়ে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, কাড়াকাড়ি স্বার্থ ও সংকীর্ণতায় ভরা সমাজে শিশু জন্মেরও যেন কোনো আনন্দ নেই। কারণ অভাবের সংসারে আরেকটি নতুন মুখ তেমনই অনাকাক্স্ক্ষিত।
কুবের-মালার প্রতিদিনের ঘরকন্নার জীবনে কপিলা যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। নানা ছুতায় সে কুবেরের ঘনিষ্ঠ হতে চায়। কুবের মালার সঙ্গ উপভোগ করে। কপিলা দুরন্ত, উচ্ছল, কৈশোরে সে গাছের ডালে কঁাঁচা বেতের দোলনা বেঁধে দোল খেত। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অবলীলায় সাঁতার কাটত, কিংবা একা একা ডিঙ্গি নিয়ে ভেসে বেড়াত। পঙ্গু মালার বিপরীতে উচ্ছল প্রাণবন্ত এই কপিলার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ কুবেরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।
কুবের যখন মাছ ধরতে যাবার প্রস্তুতি নেয়, তখন কপিলা ভ্রুকটি মাখানো চোখে আবদারের সুরে বলে ‘আমারে নিবা মাঝি সঙ্গে? কুবের আপত্তি করলে সে বলে ওঠে, আরে পুরুষ! মালার ঈর্ষা হয়, পস এটা বোঝে যে তার পঙ্গুত্বের কারণে কুবেরের সব প্রয়োজনের সঙ্গী সে হতে পারে না।’ উপন্যাসে বলা হয়েছে ‘ভাঙা চালার নিচে সংকীর্ণ শয্যায় পঙ্গু মালার তুলনা জগতে নাই।
কিন্তু অন্ধকার রাতে তামাক পৌঁছাইয়া দিতে সে তো কোনদিন নদীতে ছুটিয়া আসিতে পারে না, বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে পারে না সোজা হইয়া দাঁড়াইতে।’ এই দ্বৈরথে কপিলারই জয় হয়। কুবের একটা মিথ্যা চুরির অভিযোগে পুলিশের সাজার ভয়ে হোসেন মিয়ার নতুন উপনিবেশ বঙ্গোপসাগরের ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে দেশান্তরী হয়। তখন কপিলা সমাজ-সংসার লোকলজ্জার ভয়, সবকিছু উপেক্ষা করে কুবেরের নৌকায় গিয়ে ওঠে! তার সেই অমোঘ আহ্বান- ‘আমারে নিবা মাঝি সঙ্গে? এই আহ্বানে সাড়া দেয় কুবের।
অনিশ্চিত অথচ এক নতুন জীবনের হাতছানিতে কপিলা কুবেরের সঙ্গী হয়।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তারিণী মাঝি’ ছোট গল্পের নায়ক তারিণী ময়ূরাক্ষীর বুকে নৌকা চালায়। একদিন তীর্থযাত্রীদের নৌকা থেকে এক ধনী ঘরের বধু উত্তাল ভয়ঙ্করী ময়ূরাক্ষীর জলে পড়ে যায়। তারিণী তীব্রগতিতে সাঁতার কেটে তাকে উদ্ধার করে। মেয়েটির স্বামী ও শ্বশুর নদীর ঘাটে এসে উপস্থিত হয়ে তারিণীকে পুরস্কার দিতে চায়। সে কি চায় জানতে চাইলে তারিণী শুধু মাথা চুলকিয়ে বলে ‘এক হাঁড়ি মদের দাম আট আনা।’
মেয়েটি তখন তার সোনার নথখানি তারিণীর হাতে তুলে দেয়। ওর শ্বশুর ঘোষ মশাই বললেন ‘দশহরার সময় পার্বণী রইলো তোর, কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী! এই নে পাঁচ টাকা। তারিণী আকণ্ঠ মদ গিলে বাড়ি ফিরে তার স্ত্রী সুখির হাতে সব তুলে দেয়। তারিণীর স্ত্রী সুখি চরিত্রটি একজন কর্তব্যপরায়ণা আর সহনশীল গৃহবধূ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে ‘সুখির জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।’ শুধু বর্ষাকালে ময়ূরাক্ষীর এই মাঝিদের সুদিন। খরার সময় দেশে হাহাকার।
জেলেপাডার মানুষেরা জন্মভিটা ছেড়ে কাজের সন্ধানে দূর দেশে চলে যায়। মহাজনি ঋণের থাবায় সর্বস্বান্ত হয়ে অতঃপর দেশান্তরী হওয়া যেন কৈবর্ত জীবনের এক অনিবার্য নিয়তি। ভয়াল দুর্ভিক্ষে চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধা মাকে পথে ফেলে যাওয়া আর তার করুণ মৃত্যু ও দেহ শিয়াল কুকুরে ছিন্নভিন্ন করার বর্ণনা তাদের অসহায় জনজীবনকে তুলে ধরেছে। এমনই এক খরায় দেশে যখন খাদ্যাভাব, তারিণী তখন তার স্ত্রী সুখির হাত ধরে গ্রাম থেকে ভিন্ন অঞ্চলে চলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে।
কিন্তু পথে বেরিয়ে সে উপলব্ধি করে হঠাৎ বাতাস যেন পশ্চিম দিক থেকে বইছে। এ যেন আসন্ন জল-বন্যার সংকেত। ময়ূরাক্ষীর অভিজ্ঞ মাঝি তারিণী সুখির হাত ধরে ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু সে রাত্রেই ঝড় বৃষ্টি আর হঠাৎ ঢলের পানিতে বন্যা নেমে আসে। সমস্ত গ্রাম প্লাবিত হয়ে যায়, তখন সে স্ত্রী সুখিকে সঙ্গে নিয়ে সাঁতরে ডাঙ্গা খুঁজতে বের হয়। কিন্তু একসময় উত্তাল ঢেউয়ের তোড়ে দুজনেই তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সুখি বাঁচার জন্য প্রবলভাবে তারিণীকে জাপটে ধরে।
একবার তারা স্রোতের পাকে তলিয়ে যায় আবার ভেসে ওঠে। এভাবে দুজনেই ডুবে মরার উপক্রম হয়। তারিণী অনেক চেষ্টাতেও সুখীকে ছাড়াতে পারে না। তখন সে সুখির গলায় চাপ দিয়ে নিজেকে ভার মুক্ত করে। সুখি ধীরে ধীরে অতল জলে তলিয়ে যেতে থাকে। তারপর তারিণী জলের ওপর ভেসে উঠে বুক ভরে বাতাস নেয়। সমরেশ বসুর গঙ্গা উপন্যাসে ইছামতি রাইমঙ্গলের মোহনায় জোয়ার ভাটায় জেলে, কৈবর্ত, নিকরী, চুনুরি, মালো, এমনকি রাজবংশী কালে কালে জমি হারিয়ে যারা মৎস্যজীবী হয়েছে, তাদের সুখ-দুঃখ জীবনচর্চা আর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকার অসাধারণ বর্ণনায় পরিপূর্ণ।
সাইদার নিবারণ মাঝি, পাঁচু, গণেশ নিবারণের ছেলে বিলাস, এরা সুন্দরবনের মোহনায় মাছ ধরে। এদের পূর্বপুরুষ কেউ একজন সুন্দরবনের বাঘের রাজা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে মালো বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিল, এই কিংবদন্তিতে তারা বিশ্বাস করে গর্ববোধ করে। এখানেও মহাজনের কাছে নৌকা বাঁধা দেয়ার কথা আছে, তারপর চক্রাকারে সেই দেনা বাড়তে বাড়তে এক সময় সেই নৌকা মহাজনের হয়ে যায়।
ভাটির টানে গভীর সমুদ্রে ভেসে যাওয়া নৌকার সঙ্গে কিভাবে চিরদিনের জন্য জেলে মাঝিরা হারিয়ে যায় সেই বেদনাভরা কাহিনীর বর্ণনা আছে এই উপন্যাসে। মাছ ধরতে গিয়ে সুন্দরবনে বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায় নিবারণ মাঝি। তার ছেলে বিলাস বড় হয়ে স্বপ্ন দেখে সেও বাবার মতো সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে। বাতে পঙ্গু অমর্ত্য, ঘরে তার জোয়ান বউ। অমর্ত্যরে অক্ষমতা তাকে পীড়া দেয়। অমর্ত্যরে বউ বিলাসের সঙ্গে এক অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।
এদিকে জেলে পাড়ার তরুণী পাঁচি বিলাসের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়। গঞ্জের মহাজন দামিনী এখন বিগত যৌবনা। ‘তার পড়ন্ত যৌবন যেন আশ্বিনের নদী।’ তার নাতনি হিমি, সে দামিনীর ব্যবসা দেখাশোনা করে। বিলাস মাছ বিক্রি করতে এসে হিমির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বিলাসকে বেঁধে রাখতে পারে না হিমি। একদিন বিলাস বলে ‘আমার প্রাণ জুড়িয়েছ তুমি, আর জুড়িয়েছ বলেই আমি সমুদ্রে যাব।
মালোপাড়ার গৃহবধূরা নির্ঘুম রাতযাপন করে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায়। স্বামী পুত্র স্বজন নদীতে কিংবা মোহনায় মাছ ধরতে যায়। যেখানে পদে পদে বিপদের হাতছানি। জেলে পরিবারের কঠোর বাস্তবতা ‘তুমি মাছ মারার বউ, তুমি জাগো বারো মাস।’ তাদের জীবনে সুদিন বলতে তারা বোঝে পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাত, কখনো ডাঁটার সঙ্গে দু’চারটে গোল আলু এই ‘শখের খাওয়া’।
অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এই উপন্যাসে তিতাস আর বিজয়ের পাড়ে জেলেপাড়া। এখানে আছে গোপাল, গৌরাঙ্গ মালো, নিত্যানন্দ, বোধাই মালো, দীননাথ, জোতদার চাষী জোবেদ আলীসহ অনেকে। সেই সঙ্গে দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী। মালোপাড়ার অন্য মেয়েদের মতো মাঘের শেষে বাঁশের চোয়ারী জলে ভাসানোর ব্রত অনুষ্ঠান করে। পাড়ার ছেলে সুবল ও কিশোর দুজনেই মনে মনে বাসন্তীকে ভালোবাসে।
বাসন্তীর ভাসিয়ে দেয়া চোয়ারী সুবল আর কিশোর দুজনে কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নেয়। এ যেন বাসন্তীর ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। একটু বড় হলে পাড়ার প্রবীণ জেলে তিলকচাঁদের সঙ্গে নৌকা ভাসায় সুবল আর কিশোর। বাসন্তী কিশোরকে মনে মনে ভালোবাসে আবার সুবলও বাসন্তীকে ভালোবাসে। এরপর সুবল আর বাসন্তীর বিয়ে হয়।
একদিন প্রচ- ঝড়ে মহাজনের নৌকা ডুবে যেতে থাকে তখন নৌকা বাঁচানোর জন্য তীরের কাছে এসে সুবল লাফ দেয়। হঠাৎ স্রোতের তোড়ে নৌকা তীরে উঠে এসে সুবলকে চাপা দেয়। অকাল বৈধব্য নেমে আসে বাসন্তীর জীবনে। একাকী বাসন্তী অনন্ত নামে এক বালককে সন্তানস্নেহে বড় করতে থাকে। একদিন অনন্ত তাকে ছেড়ে চলে যায়। উপন্যাসে মালোদের নিজস্ব সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাদের সাংস্কৃতিক আবহ, ভাটিয়ালি, কীর্তন, পদাবলী, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদের পালা, গোষ্ঠ মিলন- সবকিছুই একসময় অস্তিত্বের সংকটে পড়ে।
শহরের যাত্রাদলের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা। সেই সঙ্গে বিলাসী জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ঋণগ্রস্ত হয়ে নিজ নিজ নৌকা জাল এমনকি ভিটামাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। তবুও নিজের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ‘সুবলার বউ’ বাসন্তী আর গ্রামের ছেলে মোহন একাই লড়ে যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই উপন্যাসে বিশাল এক চালচিত্রে তিতাস পাড়ের মালোদের জীবন গাঁথা রচনা করেছেন তার নিজস্ব শ্রেণিচেতনা আর উপলব্ধির বাস্তবতায়।
একাদশ শতকে বরেন্দ্রীর কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। সত্যেন সেনের ‘বিদ্রোহী কৈবর্ত’ মহাশ্বেতা দেবীর ‘কৈবর্ত খ-’ উপন্যাসে পালযুগে কৈবর্তদের জয়গাথা বর্ণিত হয়েছে। কৈবর্ত নেতা দিব্যোকের নেতৃত্বে সম্রাট দ্বিতীয় মহিপালকে যুদ্ধে পরাজিত করে বরেন্দ্রীতে কৈবর্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
তার মৃত্যুর পর তার ভাই রুদ্রক, রুদ্রকের ছেলে ভীম একাদিক্রমে সাঁইত্রিশ বছর বরেন্দ্রীকে পালশাসন থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তার ‘রামচরিতম’ গ্রন্থে কৈবর্ত বিদ্রোহকে বলেছেন ‘অলীক ধর্ম বিপ্লব’ কিংবা ‘ভবস্য আপদম’ এমনকি দিব্যোককে তিনি খল, ছলনাময় ও দস্যু নামে অভিহিত করেছেন।
সমকালীন কথাসাহিত্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে জাকির তালুকদারের উপন্যাস ‘পিতৃগণ’ আমাদের একাদশ শতকের পাল যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কাহিনীতে ভূমিপুত্র বট্যব সন্তান জন্মের সময় ধাত্রী বিল্ববালার ঋণ শোধ করতে না পেরে নিজেই কামরূপ রাজ্যের সামন্ত দেবর্ষি রামশর্মার কাছে বিক্রি হয়ে তার ভূমিদাসে পরিণত হয়। কিন্তু এক জীবনে গতর খেটে সেই বিপুল ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয় তাই তার শিশুপুত্র পপিপকেও রেহাই দেয়না রাজপুরুষেরা।
একদিন তাকেও মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তার পিতার সঙ্গে দাসত্ব করতে বাধ্য করা হয়। এই শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে আসে পপিপ। ভুজপত্রে ভূষাকালি আর খাগের কলমে লিখে চলে কৈবর্তদের জয়গাথা। তবে কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা দিব্যোকের ভাই রুদ্রকের ছেলে ভীমের শাসনামলে আবার রাজত্ব হারায় কৈবর্তরা। রাজ্য শাসনভার আবার পাল রাজাদের হাতেই চলে যায় এই পটভূমিতে হরিশংকর জলদাস লিখেছেন ‘ ‘মোহনা’।
বরেন্দ্রীর রাজা ভীমের অন্যতম সেনানায়ক চন্দ্রক আর বারাঙ্গনা পল্লীর শ্রেষ্ঠা মোহনা। হাতির পিঠে চড়ে অমিত বিক্রমে রামপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভীম পরাজিত ও নিহত হন। এর মূল কারণ চন্দ্রকের বিশ্বাসঘাতকতা। রামপাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চন্দ্রককে পাল সাম্রাজ্যের সেনাপ্রধান করার। তাই মোহনার নিজ হাতে এ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে চন্দ্রককে হত্যা করে।
সমুদ্রগামী জেলেদের জীবন নিয়ে হরিশংকর জলদাসের ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের ভুবনেশ্বরী। যার স্বামী চন্দ্রমণি এক অন্ধকার রাতে সাগরের জোয়ারে মাছ ধরতে গিয়ে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রে হারিয়ে যায়। তারপর তিন বছরের ছেলে গঙ্গাপদকে নিয়ে শুরু হয় ভুবনেশ্বরীর জীবনযুদ্ধ। এখানে শোষণ, নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িকতা, জেলে জীবনের অপমান এসব কিছু নিয়েই কর্ণফুলীর মোহনার কৈবর্তদের জনজীবন।
বড় হয়ে ভুবনেশ্বরীর ছেলে গঙ্গাপদ গ্রামের আর সব জেলে মাঝিকে সংগঠিত করে। তাদের জাগিয়ে তুলতে চায়। তারপর একদিন খালের ধারে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় গঙ্গাপদকে। মা ভুবনেশ্বরী স্তব্ধ ও নিথর পাথরের মতো গঙ্গাপদর লাশের পাশে বসে থাকে। তার দৃষ্টির আলোয় তখন গঙ্গাপদর অনাগত সন্তান বনমালীর জন্য প্রতীক্ষা। এ যেন বংশ পরম্পরায় মানুষের জ্বলে ওঠার গল্প।
হরিশংকরের ‘দহনকাল’ উপন্যাসের চন্দ্রবালা জেলেপাড়ার অন্য দশজন বিধবা জেলেনির মতো। স্বামী রামকানাই সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে পড়ে যায়। তারপর নিজেই বিহিন্দি জালে আটকা পড়ে আর উঠে আসতে পারেনি। চন্দ্রবালার তিন বছরের ছেলে রাধানাথকে নিয়েই কাটতে থাকে তার বৈধব্য জীবন। রাধানাথের ছেলে হরিদাস বড় হয়ে জেলে সমাজকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে।
এই উপন্যাসের শেষ দিকে মুক্তিযুদ্ধ তার ভয়াবহতা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। জেলেপাড়ার গণহত্যা নির্যাতন আর লুটপাটের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। জেলে রাধেশ্যামের বউ পাক হানাদার কর্তৃক লাঞ্ছিত হলে পরিণামে সে আত্মহত্যা করে। এরপর শান্ত ধীর চরিত্রের রাধেশ্যাম দা হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাকে ঘিরে জেলেপাড়ার বাসিন্দারা সংগঠিত হয়। এভাবেই কৈবর্ত জনজীবন ও সেখানে কৈবর্ত নারী চরিত্রগুলো বঞ্চনা দারিদ্র্য অপমান মাথায় নিয়ে তার প্রেম দ্রোহ সংগ্রাম আর লড়াকু জীবনগাথা আমাদের কথাসাহিত্যকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।