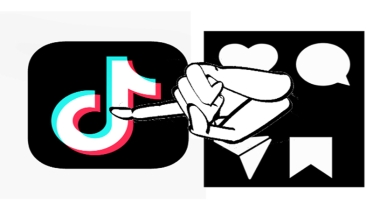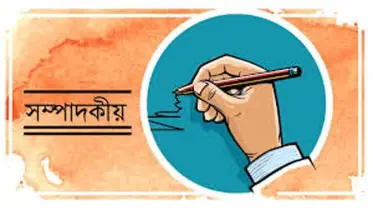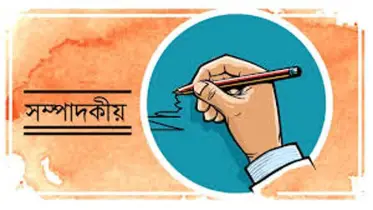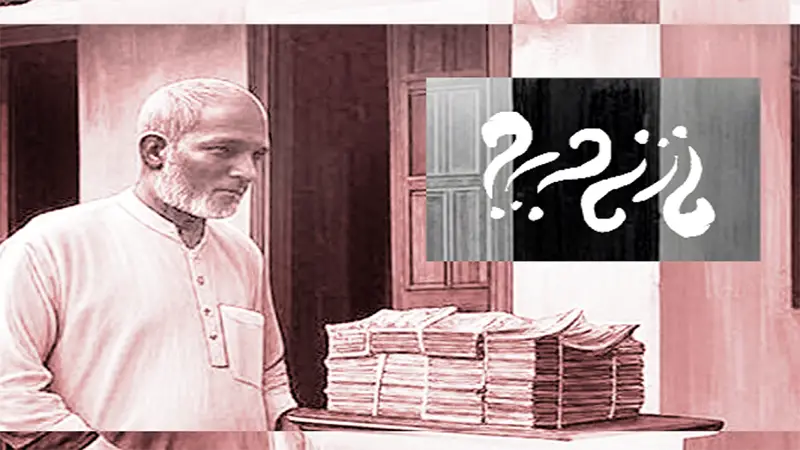
সমাজকল্যাণ ও মানব উন্নয়নের এক মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী ট্রাস্ট ফান্ড ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচনসহ নানা জনহিতকর কাজে এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ট্যাক্স বা কর ছাড়ের মতো সুবিধাদি এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহিত করে। তবে মুদ্রার অপর পিঠের মতো, এই সম্ভাবনাময় খাতের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো গুরুতর অভিযোগ। অথচ মানুষের সচেতনতা ও ধনীতুষ্টিকারী আর্থ-সমাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিষয়টি অনেকের আড়ালেই রয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রবাহের উন্মুক্ত এই সময়ের অগণিত আলোচনার ভিড়ে ট্রাস্ট ফান্ড ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান নিয়ে তুঘলকি কাণ্ডের সবার অগোচরেই রয়ে যাচ্ছে। একজন অর্থনীতিবিদের নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে ট্রাস্ট ফান্ড ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে, তা কেবল প্রকৃত জনকল্যাণকেই বাধাগ্রস্ত করছে না, বরং জাতীয় অর্থনীতিতেও ফেলছে এক দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব।
বাংলাদেশে দুর্নীতির সংস্কৃতি বিকাশে ট্রাস্ট ফান্ড ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের একটি বিস্ময়কর ও উদ্বেগজনক ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত এসব প্রতিষ্ঠান সামাজিক কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বিমোচনের মতো মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গঠিত হলেও, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো পরিণত হয়েছে দুর্নীতির রক্ষাকবচ ও অর্থপাচারের নিরাপদ চ্যানেলে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে নিবন্ধিত প্রায় ১২,০০০ ট্রাস্ট ও এনজিওর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংস্থার অর্থ ব্যয়, অডিট ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নেই। বিশেষ করে রাজনৈতিক সংযোগসম্পন্ন ব্যক্তিরা এসব ট্রাস্টের আড়ালে কালো টাকা সাদা করছে এবং প্রকল্পের অর্থ ব্যক্তিস্বার্থে যথেচ্ছা ব্যবহার করছে। ২০২৩ সালের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হওয়া ব্যয়ের ৩৫ শতাংশের বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত দাতব্য কাঠামো শুধু আর্থিক স্বচ্ছতাকে বিপন্ন করছে না, বরং সমাজে দুর্নীতিকে একটি গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করছে। সুবিধাভোগী মহলগুলোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবের কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত, যা বিচারহীনতার এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। ফলে জ্ঞানাভিজ্ঞ তো বটেই ন্যূনতম জ্ঞান রাখা সাধারণ মানুষও এখন দাতব্য বা ট্রাস্ট ফান্ড বলতে কেবলই কর ফাঁকি, প্রভাব বিস্তার ও আত্মীয়কেন্দ্রিক সুবিধা গ্রহণের প্রতীক হিসেবে দেখে। এই অবস্থার পরিবর্তনে শুধু আইন প্রয়োগ নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, জনসচেতনতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছাও অত্যাবশ্যক। নতুবা দুর্নীতি আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিটি স্তরে আরও গভীরে শিকড় গেড়ে বসবে।
বাংলাদেশে দাতব্য ট্রাস্টগুলোকে প্রদত্ত কর অব্যাহতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। উদ্দেশ্যটি হলো, ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজিকে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা, যা সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই মহৎ উদ্দেশ্যটিই অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির এক উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য প্রতিষ্ঠান কেবল নামেই ‘দাতব্য’, তাদের মূল উদ্দেশ্য কর ফাঁকি দিয়ে আর্থিক সুবিধা হাসিল করা। এসব ‘কাগুজে দাতব্য’ প্রতিষ্ঠান দাতব্য কাজের কোনো বাস্তব প্রমাণ ছাড়াই আইনের ফাঁক গলে কর ছাড়ের সুবিধা ভোগ করে চলেছে। এর প্রথম এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে রাষ্ট্রীয় রাজস্বে। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ কর হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা হয়ে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় হতে পারত, তা কিছু অসাধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পকেটে চলে যাচ্ছে। এটি এক ধরনের সুবিধাবাদ, যেখানে আইনের দুর্বল প্রয়োগ এবং তদারকির অভাবকে পুঁজি করে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা হয়। এর চেয়েও সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হলো, এ ধরনের অসাধু কর্মকাণ্ড প্রকৃত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করছে। যখন সাধারণ মানুষ জানতে পারে যে তাদের দানের অর্থ বা রাষ্ট্রের প্রদত্ত সুবিধা জনকল্যাণে ব্যবহৃত না হয়ে আত্মসাৎ করা হচ্ছে, তখন পুরো ব্যবস্থার প্রতিই এক গভীর অনাস্থা তৈরি হয়। ফলে, যেসব প্রতিষ্ঠান সত্যিই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের জন্যও তহবিল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
ট্রাস্ট ব্যবস্থার অবক্ষয়ের আরেকটি ভয়াবহ দিক হলো রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ। বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায়, অনেক ট্রাস্ট বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলের নেতা, ব্যবসায়ী বা প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য জনসেবা থেকে বিচ্যুত হয়ে গোষ্ঠীগত বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে পর্যবসিত হয়। ট্রাস্টের তহবিল ব্যবহৃত হয় রাজনৈতিক প্রচারণা, অনুসারী তৈরি করা বা ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের কাজে। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো সংকটকালে সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ বা সহায়তা কেবল দলীয় সমর্থকদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়, যা দাতব্য নীতির পরিপন্থি। এই ধরনের প্রভাব বিস্তারের ফলে ট্রাস্টের পরিচালনা পর্ষদ একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে কাজ করতে পারে না, বরং প্রভাবশালী ট্রাস্টিদের ব্যক্তিগত অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়।
এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রথমত, যেসব ট্রাস্টের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে কাজ করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠবে, অবিলম্বে তাদের সমস্ত কর সুবিধা ও সরকারি অনুদান স্থগিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মতো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে এসব ট্রাস্টের আর্থিক কার্যক্রম, ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন ও সম্পাদিত কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। তদন্তে অনিয়ম, অর্থ আত্মসাৎ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি এবং তাদের পেছনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হবে, যার মধ্যে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং ফৌজদারি মামলা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। প্রয়োজনে, আইন সংশোধন করে ট্রাস্টি বোর্ডে ‘স্বার্থের সংঘাত’ নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যেখানে কোনো ট্রাস্টির ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ ট্রাস্টের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকবে না। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলোতে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট ‘গভর্নেন্স কোড’ অনুসরণ বাধ্যতামূলক, যা পরিচালনা পর্ষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশেও অনুরূপ একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে ট্রাস্টগুলোর কার্যক্রম তদারকি করবে।
ট্রাস্ট ফান্ডকে ঘিরে সবচেয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধটি হলো অর্থ পাচার। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আড়ালে এটি একটি নিরাপদ ও সহজ কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অসাধু ব্যক্তিরা তাদের অবৈধ আয়কে ‘দান’ হিসেবে দেখিয়ে ট্রাস্টের তহবিলে জমা করে এবং পরবর্তীতে ‘দাতব্য কাজের’ নামে সেই অর্থ বিদেশে পাচার করে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে কম যাচাই-বাছাইয়ের মুখোমুখি হয়, এই সুযোগটিই অর্থ পাচারকারীরা গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় দেশের বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিদেশে পাচার হয়ে যায়, যা বিনিয়োগ সংকট তৈরি করে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। এটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও একটি বড় হুমকি, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এই অর্থ সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের মতো ভয়াবহ কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে।
এই অর্থ পাচার রোধ করতে একটি সমন্বিত ও প্রযুক্তিনির্ভর কৌশল গ্রহণ করা আবশ্যক। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইফনিটকে (বিএফআইইউ) এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সমস্ত ট্রাস্ট ফান্ডের, বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান বড় অঙ্কের বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করে বা বিদেশে অর্থ প্রেরণ করে, তাদের প্রতিটি লেনদেন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে ‘বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ’ বা ‘প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচয়’ নিশ্চিত করা। অর্থাৎ ট্রাস্টের পেছনে নিয়ন্ত্রণকারী কারা, তা একটি কেন্দ্রীয় রেজিস্টারে নথিভুক্ত করতে হবে, যাতে বেনামে বা শেল কোম্পানির আড়ালে কেউ অর্থ পাচার করতে না পারে। পাশাপাশি, অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (এফএটিএফ) সুপারিশমালা কঠোরভাবে মেনে চলা এবং বিভিন্ন দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।
এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে ট্রাস্ট ফান্ড ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করলেও দুর্বল তদারকি, রাজনৈতিক প্রভাব ও আইনের ফাঁকফোকরের কারণে তা অনেকাংশে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। এ খাতের ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং এর প্রকৃত সুফল নিশ্চিত করতে একটি সামগ্রিক সংস্কার অত্যাবশ্যক। কঠোর ও নিয়মিত নিরীক্ষা, আর্থিক প্রতিবেদনের প্রকাশ্য স্বচ্ছতা, প্রযুক্তি-নির্ভর মনিটরিং, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ গঠন এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এই খাতকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব। উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ যদি তার ট্রাস্ট ব্যবস্থা ও দাতব্য খাতকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, তবেই এসব প্রতিষ্ঠান কেবল কর ফাঁকির হাতিয়ার না হয়ে প্রকৃত অর্থেই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের এক শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
প্যানেল/মো.