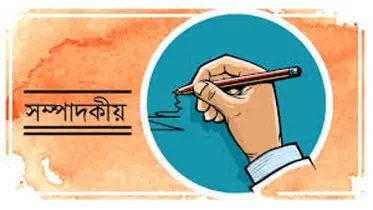মাত্র দেড় যুগ আগেও সন্ধ্যা নামলে উঠোনজুড়ে মিশে যেত শিশুদের কলরব। গাছের ছায়ায়, পুকুরঘাটে কিংবা বাড়ির পাশের বাঁশবাগানে জন্ম নিত কল্পনার রাজ্য। তখন ‘মানুষ হওয়া’র শিক্ষা শুরু হতো গল্পের ছায়ায়। জ্ঞানের ছোঁয়ায় থাকতো প্রকৃতির শুদ্ধতা। এখন সে সময় নেই। সময় পাল্টেছে। পাল্টেছে বিনোদনের ধরন। জীবনের প্রকৃতি এখন পর্দায় বন্দি। আজকের শিশুরা মুখোমুখি নয়-স্ক্রিনে বন্দি। কল্পনা নয়- কন্টেন্টে বিভোর। ভাবনার জগতে নয়- ভিউয়ের সংখ্যাই হয়ে উঠেছে আত্মতৃপ্তির মানদণ্ড। মোবাইল মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করছে। মস্তিষ্কের জাল বিস্তৃত যান্ত্রিকতায়। এই যুগের নাম-ডিজিটাল অভিশাপ যুগ। এই প্রজন্মের অলিখিত পাঠ্যবই-টিকটক। পনেরো সেকেন্ডে তৈরি হয় একেকটা মিথ্যে বাস্তবতা। হাসি, নাচ, রং, আলোর ঝলক- সব যেন আত্মার গভীরতা ঢেকে রাখে। আর শিশুমন ভুলে যেতে বসে- আত্মসম্মান কী, শিক্ষা কী, মেধা কী। এ এক নীরব ক্ষরণ। যান্ত্রিক যুগের আর্তনাদ, যার শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি না- কারণ সে শব্দ আসে নিঃশব্দে। প্রযুক্তি কখনই শত্রু নয়। শত্রু হচ্ছে ব্যবহারবিধি ও সঠিক চেতনার অভাব। আজ সময় এসেছে প্রশ্ন তোলার- আমরা কী তৈরি করছি? একজন সৃষ্টিশীল নাগরিক, নাকি একটি কনটেন্টভিত্তিক আত্মবিস্মৃত প্রজন্ম? একটি জাতির ভবিষ্যৎ কেবল বিনোদনের ধোঁয়াশায় বুঁদ হয়ে থাকলে পতন অনিবার্য।
প্রযুক্তির উৎকর্ষে তরুণরা অন্ধভাবে ধাবিত হচ্ছে। চিন্তা আর চেতনার জায়গাটি প্রতিনিয়ত সংকুচিত হয়ে পড়ছে। যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে মন-মানসিকতা গড়ে ওঠার সবচেয়ে ভয়ংকর দিকটি দেখা যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তার মধ্যে টিকটক আজকের সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সামনে এসেছে। টিকটক একটি বহুমাত্রিক প্ল্যাটফর্ম। যেখানে একজন ব্যবহারকারী তার সৃজনশীলতা তুলে ধরতে পারে মাত্র ১৫ বা ৩০ সেকেন্ডের ভিডিওতে। শুরুতে এটি একটি নিরীহ অ্যাপ মনে হলেও, বর্তমানে এর বিপজ্জনক দিকগুলোই বেশি দৃশ্যমান। অল্পবয়সীরা এই প্ল্যাটফর্মে যেভাবে যুক্ত হচ্ছে, তা সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য অশনিসংকেত। বাংলাদেশে ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, শহরাঞ্চলের ৭১ শতাংশ কিশোর-কিশোরী দিনে গড়ে তিন ঘণ্টা টিকটক ব্যবহার করে। পিউ রিসার্চের ২০২৪ সালের জরিপে বলা হয়, আমেরিকার ১৩-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ টিকটক ব্যবহার করে, যার মধ্যে ১৯ শতাংশ ‘প্রতিনিয়ত’ এই অ্যাপে সময় কাটায়। প্রযুক্তি এখন মানুষের চিন্তন, মনন ও জাগরণের নিয়ন্ত্রক। যাদের হাতে গড়ে উঠবে আগামী সমাজ সেই তরুণ প্রজন্ম আজ যন্ত্রের সুরে বাঁধা পড়ছে। তাদের কল্পনা, সৃজন ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে।
টিকটক নামের অ্যাপটি এ যুগের অন্যতম আকর্ষণ। এটি বিনোদনের মোড়কে প্রযুক্তির একটি ফাঁদ। এই ফাঁদে ব্যবহারকারী নিমিষেই মোহগ্রস্ত করে যায়। এই অ্যাপে কিশোর-কিশোরী বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ডে নিজেকে হাজির করে। কেউ হয় নায়ক, কেউ নায়িকা, কেউ হাসায়, কেউ কাঁদায়, কেউ আবার ধ্বংস ডেকে আনে নিজের অজান্তেই। টিকটক যেন এক প্রতিযোগিতার মঞ্চ। কে কতটা সাহসী, কে কতটা অদ্ভুত, কে কতটা অশ্লীল- এই মাপকাঠিতে চলে এর সফলতা। এর ফলে নৈতিকতা, শালীনতা ও মূল্যবোধের জায়গাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ঘরের মেয়েটি যখন নিজেকে টিকটকের সামনে উন্মুক্ত করে, তখন সে হয়তো বোঝেই না, সে কেবল নিজের দেহ নয়, তুলে দিচ্ছে পুরো পরিবারকে সমাজের কৌতূহলী চোখে। টিকটকে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। এই টিকটক বই, খেলাধুলা, গল্পের জগৎ, কল্পনার জগৎ প্রায় ধ্বংস করে দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে গড়ে তিন ঘণ্টা বা তার বেশি সময় তারা টিকটক অ্যাপে কাটায়। এই প্ল্যাটফর্ম মানসিক স্বাস্থ্যেও আঘাত করছে। একটানা স্ক্রলিং, একের পর এক ভিডিও দেখা, ‘লাইক’ আর ‘ফলোয়ার’-এর পেছনে দৌড়ানো সবকিছুই মানুষকে করে তোলে আত্মকেন্দ্রিক ও হতাশ। স্বীকৃতি না পেলে তারা বিষণ্নতায় ভোগে। আত্মমর্যাদা বিলীন হয়ে যায় অনলাইন প্রশংসার দাসত্বে।
টিকটককে নিছক একটি অ্যাপ মনে করা ভুল। এটি একটি কালচার, একটি দর্শন, একটি চলমান আগ্নেয়গিরি, যার উত্তাপে পোড়ে সমাজের ভিত্তি। নৈতিকতার পরতে পরতে যখন চমকপ্রদতা ঢুকে পড়ে, তখন সভ্যতা কেঁপে উঠে। তখন শিক্ষকের কণ্ঠ নিস্তব্ধ হয়। তখন পিতার পরামর্শ মূল্যহীন মনে হয়। তখন মায়ের চোখের জলও সস্তা হয়ে পড়ে। এই আসক্তি শিশু-কিশোরদের মনোজগতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলছে। একজন কিশোর যখন তার স্বাভাবিক জীবনের চাইতে বেশি সময় কাটায় ডিজিটাল বাস্তবতায়, তখন তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে সেই অনুযায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের ইউসিএসএফ পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে ২ ঘণ্টার বেশি সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটানো শিশুদের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ, আত্মমর্যাদাহীনতা এবং মুড সুইং-এর প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। ২০২৫ সালে প্রকাশিত ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অল্পবয়সীদের ডিজিটাল আসক্তি তাদের সামাজিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। তারা বাস্তব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। টিকটকের ফোর-ইউ ফিড অ্যালগরিদম একদিকে যেমন ব্যবহারকারীর আগ্রহ অনুযায়ী ভিডিও পরিবেশন করে অন্যদিকে শিশুদের মনে অহেতুক চাহিদা এবং আকাক্সক্ষা জাগিয়ে তোলে। তারা বারবার দেখে কে কত সুন্দর, কে কত লাইক পাচ্ছে, কার ভিডিও কত ভাইরাল। এই তুলনামূলক মনোভাব একসময় জন্ম দেয় হীনম্মন্যতা।
একটি স্প্যানিশ গবেষণায় এসেছে, প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশি টিকটক ব্যবহারকারী কিশোরীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশই নিজেদের শরীর ও চেহারা নিয়ে অসন্তুষ্ট। এই প্ল্যাটফর্মে ‘চ্যালেঞ্জ কনটেন্ট’-এর ব্যাপকতা ভয়াবহ রকমের। কখনো আগুন খাওয়ার চ্যালেঞ্জ, কখনো উঁচু বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ, কখনো দম বন্ধ করে রাখার চ্যালেঞ্জ। এসব ভিডিওতে যেসব কিশোরেরা অংশ নিচ্ছে, তারা বুঝতেই পারছে না এতে কী পরিণতি হতে পারে। ‘ব্ল্যাকআউট চ্যালেঞ্জ’ নামক একটি চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে গিয়ে ইতোমধ্যে বহু কিশোর-কিশোরী প্রাণ হারিয়েছে। ইউনিসেফ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন উভয়ই এসব ‘চ্যালেঞ্জ’ নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশেও শিশু-কিশোরদের মধ্যে অশ্লীলতা, কুরুচিপূর্ণ ভাষা এবং অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার উদ্বেগজনকহারে বেড়েছে। গ্রামেগঞ্জের স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মে ভিডিও বানাচ্ছে। তাদের তৈরি কনটেন্টে অনেক সময় থাকে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্য। থাকে অশালীন সংলাপ যা স্পষ্টত অপসংস্কৃতির ছায়া। এসব ভিডিও ভাইরাল হওয়াকে তারা তাদের অর্জন মনে করে। অথচ তারা বোঝে না, এই ‘ভিউ’ তাদের আত্মিক পরিপক্বতা কেড়ে নিচ্ছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে ২০২৩-২৪ সালে ১৫ বছরের কম বয়সী মানসিক রোগীর সংখ্যা ৪৩ শতাংশ বেড়ে গেছে যার বড় একটি অংশ ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরিক্ত সম্পৃক্ত।
আরও ভয়ংকর হচ্ছে- টিকটক এখন অর্থ উপার্জনের মাধ্যমেও পরিণত হয়েছে। যাদের বয়স ১২-১৪, তারা ‘কনটেন্ট ক্রিয়েটর’ হয়ে টাকা উপার্জন করছে। এতে তাদের মনোজগতে ভেসে উঠছে বিকৃত বাস্তবতা। তাদের মনে হচ্ছে, পড়াশোনার প্রয়োজন নেই, মেধার প্রয়োজন নেই, শুধু মেকআপ আর মোবাইল থাকলেই তারকা হওয়া যায়। পিউ রিসার্চ জানায়, ১৩-১৭ বছর বয়সী ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ মনে করে, ভবিষ্যতে তারা ‘ইনফ্লুয়েন্সার’ বা ‘সোশ্যাল সেলিব্রিটি’ হবে। প্ল্যাটফর্মটি যে মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে না তা নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অভাবে তার সম্ভাবনাই আজ আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। টিকটক কর্তৃপক্ষ কনটেন্ট মনিটরিংয়ের জন্য যে ব্যবস্থা রেখেছে, তা প্রান্তিক দেশগুলোয় কার্যত অকার্যকর। বাংলাদেশের মতো দেশে ভিডিওগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ হয় না বললেই চলে। যে কারণে অশালীন ভিডিও, বিভ্রান্তিকর বার্তা এবং মানসিকভাবে ক্ষতিকর ট্রেন্ড খুব সহজে ভাইরাল হয়। প্রযুক্তির ব্যবহার যেন মেধা বিকাশের সহায়ক না হয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছে। এখান থেকে শিশু-কিশোরদের সরানো না গেলে টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্ম তাদের ভবিষ্যৎ কেড়ে নেবে। আনন্দের নামে তারা হারাবে তাদের শৈশব, ভাবনার নামে তারা করবে ভুলের চর্চা। কোনো প্ল্যাটফর্মই একটি সুশিক্ষিত বিবেকবান সমাজের মতো শক্তিশালী নয়। আমাদের এখন সেই সমাজ গড়ার সময়। নিঃশব্দে ধ্বনিত হওয়া যান্ত্রিক যুগের এই হাহাকার আমাদের সময়ের সবচেয়ে গভীর ট্র্যাজেডি। আমরা এখন নতুন একটি সভ্যতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। এই সন্ধিক্ষণে আলোও আছে, অন্ধকারও। কোন পথে আমরা হাঁটব, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই।
সমাজের প্রত্যেক পরিবারকে হতে হবে সচেতন ও দৃঢ়। সন্তানের ডিজিটাল অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে নিয়ম আর শৃঙ্খলার ছায়ায়। পিতামাতা ও শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকাই সভ্য সমাজ সৃষ্টির মূল নিয়ামক। সন্তান কী দেখছে, কী শিখছে, কী শেয়ার করছে সেসব বিষয়ে পরিবারের সচেতন থাকা জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রযুক্তি ব্যবহারের ইতিবাচক দিক শেখাতে হবে সৃজনশীলতা, গবেষণা ও আত্মনির্ভরতার পাঠ দিয়ে। রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে নীতিমালার মাধ্যমে। প্রযুক্তিকে শত্রু নয়, সহচর করতে হবে, তবে তার লাগাম অবশ্যই মানুষের হাতে থাকতে হবে। সময়ের হাত ধরে আগানোই সভ্যতার ধর্ম। কিন্তু অন্ধ অগ্রগতি নয়, প্রজ্ঞার সঙ্গে পথচলাই হোক আমাদের লক্ষ্য। টিকটক হোক নিয়ন্ত্রিত, সীমিত ও অর্থবহ। স্কুল পর্যায়ে ডিজিটাল লিটারেসি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে পাঠ্যক্রমে। সরকারের পক্ষ থেকে টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মে আলাদা শিশু-নিরাপদ সংস্করণ চালু করার অনুরোধ করা উচিত। ইউনিসেফ ইতোমধ্যে প্রতিটি দেশে ‘ডিজিটাল চাইল্ড প্রটেকশন অ্যাক্ট’ চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিসরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ‘চাইল্ড ডিজিটাল ওয়েলবিয়িং’ আইন তৈরি হচ্ছে। এসব আইনে বলা হয়েছে, ১৬ বছরের কম বয়সীদের তথ্য সংগ্রহ, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ও এলগরিদমিক ম্যানিপুলেশনে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। আমাদের দেশেও এ ধরনের নীতিমালা তৈরি সময়ের দাবি। কারণ, একটি প্রজন্ম যদি বিকৃত বিনোদনের অভ্যেসে বড় হয়, তবে সে জাতির চিন্তা-সৃজন-সভ্যতা একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তরুণরা অবশ্যই হবে প্রযুক্তিজ্ঞানসমৃদ্ধ তবে থাকতে হবে মননের দীপ্তি, মূল্যবোধের দীপ্তি আর মানবিকতার সূর্য। তবেই আগামী হবে আলোকিত, সমাজ হবে সুস্থ এবং আমরা ফিরব এক সজীব চেতনার জগতে।
প্রজন্মের চেতনা, নৈতিকতা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাই একটি সমাজ সভ্যতা গড়ে তোলে। এই মূল্যবোধগুলো কখনই একা তৈরি হয় না। তৈরি হয় পারিবারিক ঘরানায়, পাঠ্যবইয়ের পাতায়, গল্পের বইয়ের চরিত্রে, শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় এবং প্রকৃতির কোলে। অথচ আজকের শিশুরা এসব থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা বড় হচ্ছে এক ধরনের ভার্চুয়াল অলীক বাস্তবতায়। এই সংস্কৃতি থামাতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এই সংস্কৃতি মানব মননে প্রোথিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। আমাদের দরকার এক যৌথ জাগরণ। অভিভাবককে হতে হবে শিশুর প্রথম শিক্ষাগুরু, শিক্ষককে হতে হবে চিন্তার অনুপ্রেরক, আর সমাজকে হতে হবে একটি নিরাপদ ও সজীব কাঠামো। একটি ভিডিওর উচ্ছ্বাস যেন কোনো শিশুর ভাবনার গভীরতা ঢেকে না দেয়। একটি কনটেন্টের তাৎক্ষণিক খুশি যেন তার চিরন্তন শৈশবকে গ্রাস না করে। আমাদের প্রয়োজন এক নতুন সকাল, যেখানে শিশুরা আবার খেলবে উঠোনজুড়ে, স্বপ্ন দেখবে গাছের ছায়ায় বসে আর শিখবে মানুষ হয়ে উঠার পাঠ। এই রূপান্তরের শুরু হোক এখানেই এই উপলব্ধি থেকে, এই কলমের আঁচরে, এই শব্দের দীপ্ত আলোয়। জাতির ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি ও সঠিক প্রযুক্তিবোধ সম্পন্ন মানবিকতার হাতেই নিরাপদ।
লেখক : শিক্ষক, কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর
[email protected]
প্যানেল/মো.