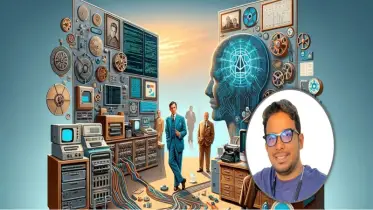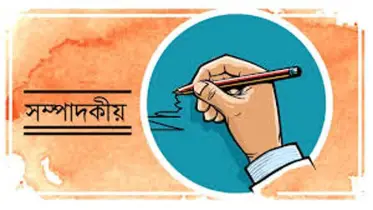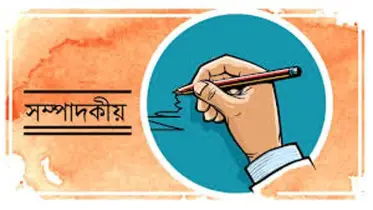একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন জানায়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে শতকরা ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী ভালোভাবে শিখছে না। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বেশির ভাগ শিক্ষার্থী বাংলাই ভালোভাবে পড়তে পারে না, গণিত ও ইংরেজির অবস্থা আরও খারাপ। পঞ্চম শ্রেণির শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ শিশু বাংলায় এবং ৩৩ ভাগ গণিতে আশানুরূপ দক্ষতা অর্জন করতে পারছে, যার অর্থ শতকরা ৭৫ ভাগ ও ৬৭ ভাগ শিশু আশানুরূপ দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। এর চেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো এর পরও এসব শিশুর অনেকে উপরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থীর শেখার মাত্রা খারাপ তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি। ঝরে পড়ার পর এক পর্যায়ে তারা অনানুষ্ঠানিক কর্মবাজারে প্রবেশ করে।
সঙ্গত প্রশ্ন জাগে- কেন তারা ঝরে পড়ে অনানুষ্ঠানিক কর্মবাজারে প্রবেশ করে? ‘শিক্ষাই জীবনের মূল, ঝরে পড়া বিরাট ভুল।’ কার ভুল? বক্তব্যের ধরনে মনে হয় শিক্ষার্থীর। বিদ্যাশিক্ষার গুরুত্ব না বুঝে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ছেড়ে মাঠে গিয়ে কৃষক বাবা, রাস্তায় গিয়ে দিনমজুর বা কারখানার শ্রমিক বাবার সঙ্গে কাজ করছে। ঝরে পড়া বা ড্রপআউট নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান গবেষণা ইত্যাদি হয়েছে। সে সবের জন্য বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকাও এসেছে।
শোনা যায়, একবার পাশ্চাত্যের এক পশু মনস্তত্ত্ববিদ এসেছিলেন এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত মানব শিশুদের ওপর শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা করতে। এখন অবশ্য দেশেই প্রচুর বিশেষজ্ঞ আছেন। যারা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে নতুন নতুন নিরীক্ষা করছেন। নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছেন। এক পদ্ধতি ঢাক ঢোল পিটিয়ে চালু হল- কয়েক বছর চলল। তারপর আরেক দল আরেক পদ্ধতি আবিষ্কার করে চালালেন আরও কয়েক বছর। দেখা গেল এ পদ্ধতি তেমন ফল দিচ্ছে না সুতরাং আবার বদল। এভাবেই চলছে বছরের পর বছর। বলার অপেক্ষা রাখে না এর সঙ্গে রাজনৈতিক ওঠানামা বা ক্ষমতা বদলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। কথা হচ্ছে এত গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষা, এত অর্থব্যয়ের পরও ঝরে পড়া বন্ধ হয়নি কেন? কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তাদের বেশির ভাগের জীবন আবর্তিত হয় প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায়। ঝরে পড়া এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা একে অন্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এদের জীবনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার স্থায়ী সমাধানের কথা দেশি বিদেশি কোনো গবেষকই বলেন না। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর না করে ঝরে পড়া সম্পর্কে যত সদুপদেশ দেওয়া হোক কাজের কাজ কিছুই হবে না।
আমাদের দুর্ভাগ্য, উনিশ শতকে সেই যে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ডিজাইন করে দিয়েছিলেন হুবহু সে অনুযায়ী আজও চলছে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাজ। যারা গণমানুষ থেকে নিজেদের সব সময় বিচ্ছিন্ন মনে করে। ঔপনিবেশিক কূটবুদ্ধি খাটিয়ে এই শিক্ষিত এলিট শ্রেণির হাতে নিম্নবিত্তের শিক্ষার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন মেকলে। কিন্তু শিক্ষায় জ্ঞান গরিমায় বিকশিত হয়ে নিজেদের যারা দেশের অধিকাংশ মানুষ থেকে উন্নত জাতের মানুষ ভাবে তারা তাচ্ছিল্য ভরে সে দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে। যাদের দেখে নাক সিটকে দশ হাত দূরে থাকেন তাদের শিক্ষিত করা এদের পক্ষে সম্ভব নয় জেনেই মেকলে এ দায়িত্ব ওই শিক্ষিত এলিটদের ওপর দিয়েছিলেন। এখানকার এলিট শ্রেণির জন্ম সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়নি। ঔপনিবেশিক প্রভুর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এদের জন্ম হয়েছিল। চিরকাল তারা প্রভুভক্ত থেকেছে। সেই যে ব্রেনওয়াশ হয়েছিল তা থেকে বেরোতে পারেনি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশও। বিচ্ছিন্নতার সেই ধারাটি এখনো সমান বহমান। একটি সমাজ কাঠামো গঠনের জন্য যতটুকু দক্ষতা প্রজ্ঞা শিক্ষা ও উদারতা প্রয়োজন তা আজও অর্জিত হলো না। ভিন্ন ফর্মে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই চলছে। এক দিকে উচ্চশিক্ষার লাভজনক ব্যবসার উচ্চকিত আলোয় চোখ ঝলসে যায়, অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত তলিয়ে আছে গভীর অন্ধকারে। বদ্ধ ডোবার মতো অবস্থা তার। মাঝে মাঝে নিরীক্ষার ঢিল পড়ে সামান্য ঢেউ ওঠে। দ্রুতই মিলিয়ে যায় তা। তারপর আবার ঘোর অন্ধকার। এমন অদ্ভুত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে একটি দেশের পক্ষে কতটুকু এগুনো সম্ভব? অল্প কিছু মানুষ, যাদের হাতে প্রচুর টাকা তারা তা দিয়ে সন্তানের জন্য শিক্ষা কিনছে। তারা জনসংখ্যার কতভাগ? হয়তো দশ ভাগ কিংবা আরেকটু বেশি। বাকি বিশাল জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সত্যিই কি ভাবনা আছে কারো?
শুরুতে যে প্রতিবেদনের উল্লেখ করেছি সেখানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কী করে শিখছে এবং সামগ্রিকভাবে কতটুকু বুঝতে পারছে, তা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকরা। এ শিক্ষকদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। তারা বাধা ধরা পদ্ধতিকে মুখস্থ পড়ান। পড়ানোর বিষয়ে তাদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শেখার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
শিক্ষকদের গুণগতমানের প্রশ্ন তো আছেই, প্রশ্ন আছে শিক্ষার্থীদের মান নিয়েও। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মূলত কারা? অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা। এদের মধ্যে কেউ কেউ মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেও বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চতর স্তরে পৌঁছানো এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছানো তো সুদূরপ্রসারী ঘটনা, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছতেই ঝরে যায় অনেকে। সামান্য সচ্ছল অভিভাবকও সন্তান নিয়ে কিন্ডারগার্টেন বা ওই মানের অন্য স্কুলে ছোটেন। তারা সন্তানের প্রতিদিনের পড়াশোনা তদরকির বিষয়ে প্রখর সচেতন। শিক্ষকরাও অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি সচেতন। সন্তানকে উচ্চশিক্ষার শিখর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই অভিভাবকরা তার শিক্ষার ভিতের প্রতি মনোযোগী হন। কিন্তু অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত যে অভিভাবক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজের সন্তানকে পাঠান তার সচেতনতা ওই পাঠানো পর্যন্তই। তিনি জানেন না, সন্তান স্কুলে কি পড়ছে। ভুল শিখছে কিনা। শিক্ষককে ভুলের জন্য অভিভাবকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর মতো বিদ্যা বা অর্থের জোর তার নেই।
দেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সাল থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস নিম্নমুখী। সাতচল্লিশ সালে সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার ৬৩৩টি। ১৯৭০ সালে তা নেমে আসে ২৯ হাজার ২৯টিতে। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। সেখানে ঘাটতি থাকলে উচ্চ শিক্ষায় যত চাকচিক্য থাক শিক্ষাব্যবস্থাটা ঠিক মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এখনো করুণ। বেসরকারি প্রাথমিকের অবস্থা তো ভয়াবহ।
১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অতগুলো প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে সরকারি করা সম্ভব নয় বলে সে সময় ধাপে ধাপে করার জন্য কয়েক বছর সময় নেওয়া হয়েছিল। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় পাঁচ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। চুয়াত্তর সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর করা এবং তিরাশি সালের মধ্যে তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। তাদের প্রস্তাব ছিল, আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। গত আওয়ামী শাসন আমলের প্রথম দফায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও জাতীয় শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলেছিল এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। তাদের মতে, এটা করতে হলে সরকারি-বেসরকারিসহ প্রায় ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ এবং অবকাঠামো সুবিধা বাড়াতে হবে। এ সংক্রান্ত যেসব প্রস্তাব ছিল তা বাস্তবায়ন করতে যে টাকা ও অবকাঠামো সুবিধা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করতেই তাদের মতে ছ’সাত বছর লাগবে। ছ’সাত বছরের বেশি সময় তারা পেয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অন্য সব সেক্টরের মতো লুটাপাটই হয়েছে শুধু।
প্যানেল