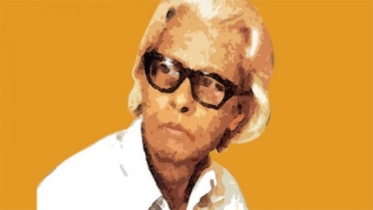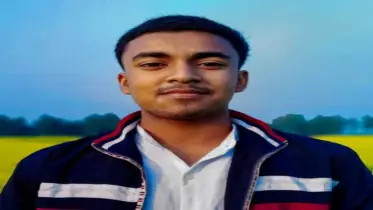.
কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন একজন কাল সচেতন ও ইতিহাস সচেতন কবি। আধুনিক কাব্যকলার বিচিত্র ইজম প্রয়োগ ও শব্দ নিরিখের ক্ষেত্রেও তার অনন্যতা বিস্ময়কর। বিশেষত কবিতার উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দের নৈপুণ্য তুলনাহীন। কবিতাকে তিনি মুক্ত আঙ্গিকে উত্তীর্ণ করে গদ্যের স্পন্দন যুক্ত করেন, যা পরবর্তী কবিদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। জীবনবোধকে নাড়া দিয়েছে।
কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন স্কুল শিক্ষক ও সমাজসেবক। ‘তিনি ব্রহ্মবাদী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মাতা কুসুম কুমারী ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। জীবনানন্দ দাশের বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হয় মায়ের কাছেই। তারপর তিনি বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএ প্রথম বিভাগে এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন। ১৯২২ সালে কলকাতা সিটি কলেজে ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। জীবনানন্দ দাশ ১৯৩৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছু আগে তিনি সপরিবারে কলকাতায় চলে যান।
১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরাপালক’। ১৯৩০ সালের ৯ মে বিয়ে করেন রোহিণী কুমার গুপ্তের মেয়ে লাবণ্য গুপ্তকে। বিবাহিত জীবন তার মোটেই সুখের ছিল না। জীবনানন্দ দাশ বৈবাহিক জীবনে কখনও সফলতা পাননি। বারবার ভাবতেন আত্মহত্যার কথা। ভেবেছিলেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে সাগরের জলে ডুবে মরবেন। সারাটা জীবন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান মনে করতেন আমাদের এই বাংলাদেশকে। জীবনানন্দ দাশ কবি হলেও অসংখ্য ছোট গল্প, কয়েকটি উপন্যাস ও প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবদ্দশায় তিনি এগুলো প্রকাশ করেননি।
তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে- ধূসর পান্ডু লিপি (১৯৩৬ খ্রিঃ), বনলতা সেন (১৯৪২ খ্রিঃ), মহাপৃথিবী (১৯৪৪ খ্রিঃ), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮ খ্রিঃ) রূপসী বাংলা (১৯৫৭ খ্রিঃ), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১ খ্রিঃ)। এছাড়াও বহু অগ্রন্থিত কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে- মালাবান (১৯৭৩ খ্রিঃ), সুতীর্থ (১৯৭৭ খ্রিঃ), জলপাই হাটি (১৯৮৫ খ্রিঃ), জীবন প্রণালী (অপ্রকাশিত), রাসমতির উপাখ্যান (অপ্রকাশিত) ইত্যাদি। তার রচিত গল্পের সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। কবিতার কথা (১৯৫৫ খ্রিঃ) নামে তার একটি মননশীল ও নন্দন ভাবনামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে তার গদ্য রচনা ও অপ্রকাশিত কবিতার সঙ্কলনরূপে “জীবনানন্দ সমগ্র” (১৯৮৫-১৯৯৬ খ্রিঃ) নামে বারো খন্ড রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিঃ) নিবিড় প্রকৃতি চেতনাময় নিঃসর্গ ও রূপকথা- পুরাণের জগত তার কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্র রূপময়। বিশেষত ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে যেভাবে আবহমান বাংলার চিত্ররূপ ও অনুসূক্ষ্ম সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি রূপসী বাংলার কবি হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পেক্ষাপটে জীবনানন্দের কবিতার ভূমিকা ঐতিহাসিক। ষাটের দশকে বাঙালীর জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় বাঙালী জনতাকে তার ‘রূপসী বাংলা’ গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।
জীবনানন্দ ছিলেন আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘বনলতা সেন’ নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে ১৯৫৩ সালে পুরস্কৃত হয়। জীবনানন্দের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থটি ১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে জীবনানন্দ দাশ অকালে মৃত্যুবরণ করেন।
জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তার কবিতার চিত্রময়তা, যার সঙ্গে আমরা অনায়াসে ঘনিষ্ঠবোধ করি। এটি তার জনপ্রিয়তার অন্যতম একটি কারণ। যে প্রকৃতির বর্ণনা জীবনানন্দ করেন, বাস্তবে তাকে আমরা আর খুঁজে পাই না, পাই না বলেই হয়ত হারানো সেই সৌন্দর্যকে আমরা নিজের ভেবে ও প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরি। অনেক সময় তার উচ্চারিত শব্দচিত্র আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। সম্রাট বিম্বিসার কে, বির্দভ নগর কোথায়, তা না জেনেই মনে মনে নিজের মতো এক চিত্র ও ধ্বনির জগত আমরা গড়ে নেই। আগাগোড়া তার কবিতার সুর বিষণœ, সবচেয়ে উজ্জ্বল যে রং তাও ধূসর, অথচ তা’ সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমরা ব্যক্তিগত প্রণোদনার উৎস খুঁজে পাই।
ইতিহাসখ্যাত অর্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর রাজবাড়ী নাটোর, উত্তরা গণভবন নাটোর, কাঁচা গোল্লার শহর নাটোর, কবি জীবনান্দ দাশের বনলতা সেনের বাড়ি নাটোর। বনলতা সেন বলে কোন নারী কি ইতিহাসে ছিল? নাকি এটি শুধু কবির নিছক কল্পনা। বিখ্যাত বনলতা সেন কবিতায় তিনবার বনলতা সেনের নাম নিয়েছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। তার মধ্যে দুবার কবি সরাসরি ইঙ্গিত করেছেন বনলতা সেনের আবাস ভূমি বাংলাদেশের নাটোর। কে এই সুন্দরী নারী? কী তার পরিচয়? নাটোরে বনলতা সেন নামের কোন মায়াবতী মেয়ের সঙ্গে কী জীবনানন্দ দাশের আদৌ পরিচয় ছিল? তারচেয়ে বড় কথা কবি কি কখনও নাটোরে পদার্পণ করেছিলেন? বনলতা সেন বইটি হাতে নিয়ে গোপাল চন্দ্র রায় একবার কবিকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন ‘দাদা আপনি যে লিখেছেন নাটোরের বনলতা সেন, এই বনলতা সেনটা কে? এই নামে সত্যি আপনার পরিচিত কোন মেয়ে ছিল নাকি?” এত প্রশ্ন শুনে শুধু মুচকি হেসেছেন কবি কিন্তু কোন উত্তর দেননি। বনলতা সেন বিষয়ে আজীবন এই নীরবতা বজায় রেখেছেন কবি, মনের অজান্তেও কখনও কোন প্রিয়জনের কাছে বনলতা সেনের কোন কাহিনী বর্ণনা করেননি। তবে কবি নীরব থাকলেও গবেষকরা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। বনলতা সেনের অন্বেষণে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাননি তারা। এমনকি জীবনানন্দ দাশ কখন নাটোরে পদার্পণ করেছিলেন কিনা এ বিষয়েও কোন তথ্য উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছেন গবেষকরা। জীবনান্দ দাশের অন্য লেখায়ও নাটোরে তার আগমন সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে, গবেষকদের কাছে বনলতা সেন রয়ে গেছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে এক রহস্যময়ী নারী। তবে গবেষকরা বনলতা সেনকে রহস্যময়ী মানবী হিসেবে চিত্রিত করলে কী হবে, নাটোরের মানুষের কাছে কিন্তু অদ্যাবধি বনলতা সেন রক্ত মাংসের মানুষ, পরম আপনজন। এমন কি তাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠেছে কয়েকটি কাহিনী। যদিও এসব কাহিনী ইতিহাসের কোন সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়নি। তথাপি আসুন কাহিনীগুলো শোনা যাক-
জীবনানন্দ দাশ একবার ব্যক্তিগত কাজে ট্রেনে করে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন। তখনকার দিনে নাটোর হয়ে যেত দার্জিলিং মেল। একাকী নির্জন কামরায় বসে আছেন কবি। হঠাৎ নাটোর স্টেশনে অপরূপ সুন্দরী একটা মেয়েকে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নাম ভুবন সেন। তিনি নাটোরের বনেদি সুকুল পরিবারের ম্যানেজার। ভুবন সেনের সঙ্গিনী কামরায় তারই বিধবা বোন বনলতা সেন। অচিরেই পথের ক্লান্তিতে ট্রেনের কামরায় ঘুমিয়ে পড়েন ভুবন সেন। কামরায় জেগে থাকেন শুধু দুজন- জীবনানন্দ দাশ আর বনলতা সেন। এই নীবর মুহূর্তে বনলতা সেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন কবি। এমনিতেই মুখচোরা কবি, একান্ত একসঙ্গে কেটে যায় অনেকক্ষণ। এক সময় মাঝপথে কোন এক স্টেশনে নেমে যান বনলতা সেন।
কামরায় আবার একা হয়ে যান জীবনানন্দ। বনলতা সেন চলে গেলেন। কিন্তু রেখে গেলেন কবির মনে এক বিষণœতার ছাপ। তারই অবিস্মরণীয় প্রকাশ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ‘থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন’। দ্বিতীয় কাহিনীর কেন্দ্রেও আছেন ভুবন সেনের বিধবা বোন বনলতা। তবে ঘটনাস্থল এবার ট্রেন নয়, ভুবন সেনের বাড়ি। নাটোর বেড়াতে গেছেন জীবনানন্দ দাশ। অতিথি হয়েছেন নাটোরের বনেদি পরিবার সুকুল বাবুর বাড়িতে। এক দুপুরে সুকুল এস্টেটের ম্যানেজার ভুবন সেনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। ভুবন সেনের বিধবা বোন বনলতা সেনের ওপর পড়েছে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব। খাবারের বিছানায় বসে আছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। হঠাৎ অবগুণ্ঠিত এক বিধবা বালিকা শ্বেতশুভ্র বসনের চেয়েও অপরূপ এক সৌন্দর্যম-িত মুখ। চমকে উঠলেন কবি। এত অল্প বয়সে বিধবা বসন! কবির মনকে আলোড়িত করে। হয়ত বা সে সময় দু’একটি কথাও হয় কবির সঙ্গে বনলতা সেনের। তারপর একসময় নাটোর ছেড়ে যান কবি। সঙ্গে নিয়ে যান এক অপরূপ মুখের ছবি। সেই ছবি হয়ত পরবর্তীতে কবিকে পথ দেখিয়েছে অন্ধকারে, চারিদিকে সমুদ্র সফেনের ভেতরও খুঁজে পেয়েছেন শান্তির পরশ। তৃতীয় কাহিনীর ঘটনাস্থলও নাটোর।
নাটোর রাজবাড়ীর চাকচিক্য তখন ভুবনজোড়া। অর্ধবঙ্গেরশ্বরী রাণী ভবানীর রাজবাড়ীতে যে ঐশ্বর্যের সমাবেশ ঘটিয়ে ছিলেন, তার মৃত্যুর পরও সেই সৌন্দর্যের অনেকটাই ধরে রেখেছিলেন পরবর্তী বংশধররা। বিখ্যাত কীর্তিমান মানুষদের নিয়মিত পদচারণায় তখনও মুখরিত রাজবাড়ী। তাদের আদর-আপ্যায়নে কাহিনীও ছিল কিংবদন্তিতুল্য। এমনই সময়ে নাটোরের কোন এক রাজার আমন্ত্রণে রাজবাড়ীতে বেড়াতে আসেন কবি জীবনানন্দ দাশ। সেখানে দুদিন অবস্থানও করেন। কবির দেখাশোনার জন্য কজন সুন্দরীকে নিয়োগ করেন স্বয়ং রাজা। তাদের সেবায় ও অতিথিপরায়ণে মুগ্ধ হন কবি, এদের একজনের প্রতি জেগে ওঠে কবির আলাদা মমতা। সেই মমত্ববোধ থেকে কবি তাকে নিয়ে লিখতে চান কবিতা। লোকলজ্জার ভয়ে শিউরে ওঠে ওই নারী। কবিকে অন্য কোন নামে কবিতা লিখতে অনুরোধ করেন তিনি। রোমান্টিক কবি তার এই মানসপ্রিয়ার নাম দেন ‘বনলতা সেন’। এভাবেই কল্পনা ও কাহিনীকে ঘিরে সবার কাছে এক রহস্যময়ী নারীসত্তা হিসেবে চিরঞ্জীব হয়ে আছে জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন। আর নাটোরের নামটি বাংলা সাহিত্যে হয়ে উঠেছে আর এক কিংবদন্তি নগরী। জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ ও বিস্ময় প্রায় অন্তহীন। বিশ শতকের অন্যকোন বাঙালী কবি আমাদের কল্পনায় এমন প্রবলভাবে দাগ কাটেনি। আজও তার কবিতার অলঙ্কার, শব্দ ব্যবহার এবং অধুনা আবিষ্কৃত গদ্যের ভাষা আমাদের ক্রমেই বিস্মিত করে চলেছে। জীবনানন্দের মৃত্যুর ৬৬ বছর পরও তিনি সমকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রধান কবি হিসেবে অধিষ্ঠিত।