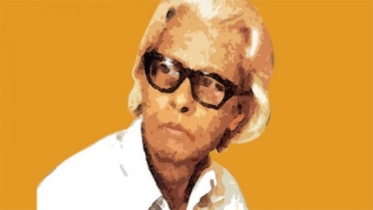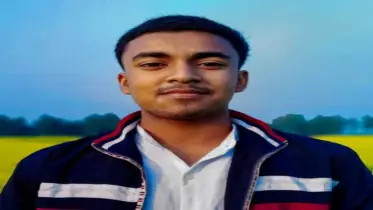দর্শন
বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চায় সরদার ফজলুল করিম একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। দর্শনশাস্ত্রের একাধিক ধ্রুপদী গ্রন্থকে বাংলায় রূপান্তর করেছেন তিনি। শুধু অনুবাদেই থেমে থাকেননি। নিজেও দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার চাষাবাদ করেছেন। যে দর্শনে আস্থা রাখতেন, তার জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন। তুলনামূলক আরামদায়ক ও স্থিতিশীল জীবনের বিনিময়ে সংগ্রামমুখর জীবন কিনেছেন। তার পরিষ্কার চিন্তাভাবনার সৎ রূপান্তর ঘটেছে কাজ-কর্মে। এমন একজন কর্মঠ দার্শনিকের নিজস্ব দর্শন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন অধ্যাপক ড. মোঃ আনিসুজ্জামান।
সরদার মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এঙ্গেলসের ‘এন্টি ড্যুরিং’-কে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় ‘দর্শনকোষ’ রচনা তার একটি বড় কৃতিত্ব। পশ্চিমা বস্তুবাদী দর্শন তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নিজের যাপিত জীবনে তিনি চিন্তা ও কাজের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সাধন করেছেন। নিজস্ব চিন্তাচর্চা এবং জীবনযাপনের গুণে তিনি নিজেও একজন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হয়ে উঠেছেন বলে মনে করেন মো. আনিসুজ্জামান। ‘সরদারের দর্শন’ বইটি তার সেই মতামতকেই বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে।
মোঃ আনিসুজ্জামান এর আগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনার মধ্যে থেকে তাদের জ্ঞানতত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। এই তালিকায় রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আহমদ শরীফ, আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। একই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ সংযোজন হলেন সরদার ফজলুল করিম। চিন্তার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বিখ্যাত বহু দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীগণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মেনে চিন্তাচর্চা করেননি।
তাদের বহুমাত্রিক লেখালেখির মধ্যে তারা বিভিন্ন জায়গায় দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেসব লেখালেখির মধ্যে থেকে মোঃ আনিসুজ্জামানের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বগণ তাদের চিন্তা-ভাবনাকে কাঠামোবদ্ধ করে নানা ভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে বুঝতে চেয়েছেন। ইতিহাসজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক দর্শনচর্চা এভাবেই বিকশিত হয়েছে।
জ্ঞানতত্ত্বের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হলো জ্ঞানের উৎপত্তি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, শর্ত, বৈধতা, সীমা ইত্যাদি। বিভিন্ন ঘরানার দার্শনিক বিভিন্নভাবে এসব বিষয়ের উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুবাদী ধারার চিন্তকেরা বস্তুজগতকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হিসেবে তারা বাস্তবজীবনের চাহিদার কথা বিবেচনা করেন। বস্তুবাদী ভাবধারায় পুষ্ট সরদার ফজলুল করিমও মনে করতেন, জ্ঞান অর্জন নিজে থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন কাজ নয়। মানুষের জীবনকে আরও বেশি যাপনযোগ্য করার তাগিদেই সে জ্ঞান অর্জন করে।
বস্তুজগতকে জেনে-বুঝে তাকে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই জ্ঞান অর্জিত হয়। ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্ব ইতিহাসজুড়ে জীবনবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের কথা প্রচার করে গেছে। তাদের এই জ্ঞানকৈবল্যবাদী মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক মনে হলেও সেগুলো সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থবাদী রাজনীতিকে মতাদর্শিক সহায়তা প্রদান করে গেছে। রাজনীতিহীনতার এই রাজনীতি সরদার বুঝেছিলেন। সে অনুযায়ী তিনি ইতিহাসের মার খেয়ে যাওয়া সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর সহায়ক জ্ঞান উৎপাদনের পক্ষপাতি ছিলেন। সরদার ফজলুল করিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার এমন একটা চেহারা দেয়া হয়েছে ‘সরদারের দর্শন’ বইটিতে।
দর্শনশাস্ত্রের অপর একটি শাখা অধিবিদ্যা আলোচনা করে জগতের মূলসত্তা, সৃষ্টিকর্তা, আত্মা, কার্যকারণ সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে। এই শৃঙ্খলাবিদ্যার সর্বপ্রাচীন এই শাখাটি সময়ের সঙ্গে বিকশিত হতে হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এসেছে। এতগুলো বছরের পথচলায় দর্শন আরো বিভিন্ন শৃঙ্খলাবিদ্যার জন্ম দিয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলো জন্ম হয়েছে দর্শনশাস্ত্রের গর্ভ থেকে।
দর্শনের সামগ্রিক আলোচনার জায়গা থেকে বিশেষায়িত হয়ে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান আলাদাভাবে বর্তমান সভ্যতায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। প্রাচীন গ্রিকযুগের অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়বস্তুর অনেকগুলোই এখন পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাপগতিবিদ্যা ইত্যাদিতে আলোচিত হচ্ছে। চিন্তার ইতিহাসে দর্শনশাস্ত্র এভাবে একের পর এক শৃঙ্খলবিদ্যার জন্ম দিয়ে তাদের কাছে নিজস্ব আলোচনার বিষয়বস্তু ‘হারিয়ে’ নিঃশেষ হয়ে যায় নি বরং দার্শনিকরা একে নতুন নতুন ভূমিকায় অভিষিক্ত করেছেন।
উনিশ শতকের যৌক্তিক দৃষ্টবাদী আন্দোলন অধিবিদ্যার সবরকম সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নাকচ করে দিয়ে দর্শনকে কেবলমাত্র মানুষের ভাষা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব দিয়েছে। এর সমালোচনায় অনেকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মোঃ আনিসুজ্জামান বলেছেন, তাতে করে দর্শনকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলা হয়েছে। সবরকম বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার মধ্যে সরদার ফজলুল করিম বিশেষভাবে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে শিরোধার্য করেছেন বলে তার নিজের নানান লেখাজোখা এবং তাকে নিয়ে চর্চা করা বই ‘সরদারের দর্শন’ সাক্ষ্য দিচ্ছে।
বস্তুবাদী সরদারের অধিবিদ্যাও গতানুগতিক বস্তুবাদী চিন্তাকাঠামো অনুসরণ করেছে। লেখকের ভাষায়- ‘সরদার ফজলুল করিম দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের মূল সূত্রগুলো অধ্যয়ন করেছেন এবং আত্মস্থ করেছেন জীবনদর্শনে।’ (সরদারের দর্শন, পৃষ্ঠা ৮৫)
‘সরদারের দর্শন’ গ্রন্থে সরদার ফজলুল করিমকে যেভাবে একজন পুরোদস্তুর বাঙালী মুসলিম দার্শনিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে অনেকে আপত্তি জানাতে পারেন। তার দর্শনের মৌলিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। আবার পরবর্তী এই প্রবণতাকে উপনিবেশের ঘোর হিসেবেও সমালোচনা করা যেতে পারে। চিন্তা-ভাবনার এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে বসবাস করেও এই ভূখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ একজন বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে জানার আগ্রহ থাকলে ‘সরদারের দর্শন’ বইটি পাঠ করা যেতে পারে।