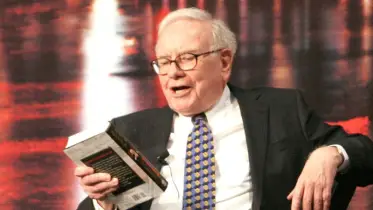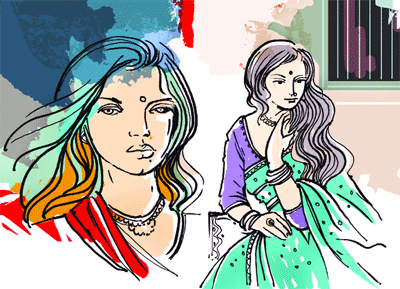
প্রাচীনকালে চর্যাপদের কবিদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। সেই যাত্রা মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে পৌঁছায় বিভিন্ন কবির মাধ্যমে। মূলত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল কাব্যনির্ভর। আধুনিক যুগে কাব্যের গন্ডি ছেড়ে গদ্যের রূপ লাভ করে বাংলার সাহিত্য। যাঁদের অবদানে বাংলা সাহিত্য আজকের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, তাঁদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রধান। একমাত্র মহাকাব্য ছাড়া বরীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সকল শাখাতেই স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর হাতেই বাংলা ছোটগল্প পেয়েছে যথার্থরূপ শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, তাঁর ছোট গল্প সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের ভা-ারকে করেছে সমৃদ্ধ। লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০), গী দ্য মাপাসা (১৮৫০-১৮৯২) প্রমুখ ছোট গল্পকারের সঙ্গে স্বীয় প্রতিভায় বিশ্ব সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর রচিত ছোট গল্পগুলো চরিত্র চিত্রনের দিক দিয়ে যেমন অসাধারণ, ঠিক তেমনই অনন্য সমাজ বাস্তবতার দিক থেকে। বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবন শিল্পী তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ করে নারীর জীবন তিনি অসাধারণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। আর এই চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজ পেয়েছে গুরুত্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুধাবন করেছিলেন সমাজকে বাদ দিয়ে সমাজের মানুষের জীবনের শোক দুঃখকে তুলে ধরা যায় না। সমাজের সঙ্গে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি তার ছোট গল্পে সেই সব নারীর হৃদয়কে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন, যারা সমাজের কোন না কোন স্থানে অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত। তার বিখ্যাত ছোট গল্প দেনা-পাওনা (১৮৯০) যৌতুক প্রথার জন্য বলিদান হওয়া একটি পরিবারের করুণ চিত্র এই ছোট গল্পটি। পণ প্রথার মতো একটি বর্বর নিয়ম কিভাবে একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়, তার বাস্তব চিত্র বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কন সুনিপুণভাবে। এক দরিদ্র পিতা, তার একমাত্র কন্যাকে যৌতুক প্রথার জন্য হারান চিরতরে। ৫ পুত্রের পরে কন্যা জন্ম নেওয়ায় আদর করে রামসুন্দর বাবু আদর করে নাম রাখেন নিরুপমা। নিজের সাধ্যের বাইরে ধনাঢ্য ধরে কন্যাদানের প্রচেষ্টা শুধু রামসুন্দরের মধ্যে নয়, আজও অনেক পিতার মধ্যে দেখা যায়। এরমূল্য শুধু অর্থ বা চোখের জলে নয় জীবন দিয়ে দিতে হয়। বড় ঘরে বিস্তর যৌতুক প্রদানের জন্য রাজি হয়ে নিরুপমার বিয়ে দেন রামসুন্দর। কিন্তু পণের টাকা পুরোপুরি পরিশোধ না হওয়ায় নিরুপমার ওপর নেমে আসে শ্বশুরবাড়ির খড়গ। স্বামী বাইরে চাকরি করে বলে নিরুপমার ওপর হওয়া অন্যায় সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল না। নিজের মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধ রামসুন্দর দেখা করতে পারতেন না, অপরাধ পণের টাকা শোধ করতে না পারা। বিভিন্ন জায়গা থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করেও তিনি নিরুপমার জীবনে সুখ এনে দিতে পারেননি। অসহায় নিরুপমা কখনই চায়নি, তার বাবা ভাইয়ের ছোট ছোট বাচ্চারা তার জন্য আশ্রয়হীন হয়ে যাক। কিন্তু তৎকালীন সমাজ নারীর কথা বলার অধিকার রেখেছিল ক্ষুণœ করে। তাই নিরুপমা কষ্ট চেপে রেখে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। হয়তো তার স্বামীর নগদ যৌতুকে পুনরায় ভাল বিয়ে হবে। কিন্তু যে মা-বাবার কাছ থেকে নিরুপমা চলে গেল তাদের শূন্যতা অপূরণীয়। বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও মেয়ের বাবা ছিলেন তৎকালীন বাঙালী সমাজে পণ প্রথা যে ভয়ানক অভিশাপ ছিল তা তিনি অন্তকরণ দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই যে বরীন্দ্রনাথ তার দেনা-পাওনা ছোটগল্পের নিরুপমার মৃত্যু ঘটিয়েছেন পণ্যের জন্য, সেই বরীন্দ্রনাথ জাগিয়ে তুলেছেন অপরিচিতার কল্যাণীকে। কল্যাণী বিয়েকে জীবনের অপরিহার্য সত্য না মেনে দেশপ্রেমকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অপরিচিতা ছোটগল্পটি প্রথম ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। সেই সময় পৃথিবীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু, বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) হয়ে গেছে। মুসলিম লিগ (১৯০৬) গঠিত হয়েছে। এসবের মধ্যে কবিতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পেয়ে বাঙালীকে গর্বিত করেছেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে এসে চিন্তনে বরীন্দ্রনাথ পরিণত হয়েছেন, তার পরিণত চিন্তার সুফল কল্যাণী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তুলেছেন নারীদের। ‘দেনা-পাওনা’ নিরুপমা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বাবাকে পণ দিতে নিরুৎসাহিত করেছেন। ঠিক তেমনি ‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণী সাহসী পদক্ষেপে নিজের বিয়ে নিজেই ভেঙে দেয়। এখানেও সমাজের অভিশাপ পণ প্রথা তার প্রবল থাবা বিস্তার করে রেখেছে। অপরিচিতা গল্পটি উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা। গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যুদ্ধ সংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালী যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধী অর্জন করেও ব্যক্তিত্বহীন পরিবারতন্ত্রের কাছে কাঠের পুতুলমাত্র। বিয়ের লগ্ন প্রস্তুত, তখন যে নিয়ম চরম বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত সেই নিয়ম পণপ্রথার জন্য অবিশ্বাসের পদাঘাতে জর্জরিত। কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন চিনতেন নিজের কন্যাকে। তাই দেরি না করে নিয়মের বাধনে সম্পর্ক তৈরির আগে বিশ্বাসহীনতার জন্য নির্মম কষাঘাতে পন্ড করেছেন সমস্ত আয়োজন অনুতাপহীন দৃঢ়চিত্তে। লৌকিকতার চেয়ে কন্যার আত্মসম্মান, জীবন তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এখানে ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌতুকের বিরুদ্ধে নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রতিবাদকে তুলে ধরলেন। পিতার বলিস্ট প্রতিরোধ এবং কন্যা কল্যাণীর দেশ চেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বে জাগরণ তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি স্বার্থক। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর সুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশ যেন, আগামীর নতুন নারীর আগমনী সঙ্গীত গেয়ে উঠেছেন। এখানেই রবীন্দনাথ ঠাকুর স্বার্থক। সমাজবাস্তবতার ভিতর দিয়ে তৎকালীন নারী মানসকে জাগিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই, বাংলা সাহিত্যের পাঠক আজও রবীন্দ্র সাহিত্যে সমৃদ্ধ ও বিমুগ্ধ।