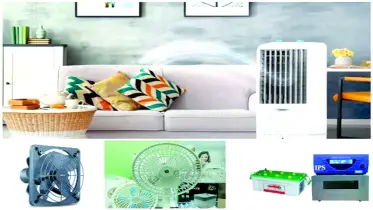বাঙালী একটি সংকর জনগোষ্ঠী। প্রাচীনকাল হতে বিশ্বের নানা অঞ্চল থেকে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলয়েড, ভোটচীন, নেগ্রিটো, সেমেটিক, আর্য ইত্যাদি নানা নরগোষ্ঠী বাংলা অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। কিন্তু তখনও বাংলা ও বাঙালী সংহত কোন সত্তা হয়ে ওঠেনি। ইতিহাসে এ সময়কে প্রত্নবাংলা হিসাবে আখ্যাত করা হয়। তখন বাংলা ও বাঙালী নৃগোষ্ঠী সৃজ্যমান (formative stage) একটা পর্যায়ে ছিল। কারণ এই জনগোষ্ঠীর কোন সাধারণ (common) ভাষা তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ভাষায় ভাবের আদান-প্রদানের স্তরে এই জনগোষ্ঠীর অবস্থান। বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে মাত্র হাজার খানেক বছর আগে। আর সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে সাত আটশ’ বছর আগে। একটি সাধারণ ও সংহত ভাষা ছাড়া কোন জাতি গড়ে ওঠে না। বঙ্গদেশে বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রাচীন অনার্য অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি ভাষার বহু কিছু ছেড়ে দিয়ে আর্য ভাষা গোষ্ঠীর মাগধি প্রাকৃত অংশ বাংলা সাধারণ ভাষায় (common language) রূপান্তরিত হয় তাতে সংস্কৃতের প্রভাব থাকল প্রবলভাবে। এভাবেই বাঙালীর জাতি গঠনের প্রাথমিক স্তরটি সম্পন্ন হয়। জাতি গঠনের অন্য সমস্যার একটা জটিল দিকও ছিল। কারণ এই সব আদিম জনগোষ্ঠী নানা আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-ধর্মমত এবং সাধনপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। এদের রক্তধারা ও সাংস্কৃতিক বোধ-বিশ্বাস, উপকরণও ছিল বহু বিচিত্র। এত বিচিত্র জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যের মানবগোষ্ঠীর জীবন পদ্ধতি নির্ধারণ এবং যাপিত জীবনকে সহনীয় করার লক্ষ্যে যে, কোন বিরোধ বা অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি হয়নি বা সর্বোব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশে সমন্বিত জীবনধারা গড়ে উঠেছে সেটিই আমাদের পূর্ব পুরুষদের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। জীবনযাত্রায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য এ ধরনের গ্রহণক্ষম ও মিলেমিশে বাস করার বোধ আমাদের প্রাচীন বংশধরদের এক অসামান্য কীর্তি।
এই আদি বা প্রত্ন-বাঙালীর ধর্ম-দর্শন, ঐতিহ্য ও সামাজিক জীবন-যাত্রায় কিছু কিছু পার্থক্য এমনকি বিপরীতধর্মিতা থাকা সত্ত্বেও সমন্বয়ের একটি ধারাই ক্রমশ বলবান হয়ে জাতিগঠনের রূপ নিতে থাকে। বাঙালীর আদি ইতিহাসের সূচনা এভাবে হয়েছে বলেই ইতিহাস থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অসাধারণ গ্রহণ ক্ষমতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিভিন্ন কৌম সমাজের মত-পথ-পন্থার গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমাদের এ অঞ্চলের নানা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ধীরে ধীরে যে সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছে তাকেই আমরা বাঙালী জীবন বলে আখ্যাত করেছি। অষ্টম শতকের পাল আমলকে এই জীবনের কিছুটা সংহত সূচনা বলে মনে করা যেতে পারে। পাল আমলে শিল্প-সংস্কৃতি-ভাস্কর্য-চিত্রকলার যে অসামান্য বিকাশ ঘটেছিল তাও বোধহয় নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সমন্বিত চিন্তনেরই ফল। শুধু শিল্প-সংস্কৃতি নয়, রাজনৈতিক জীবনধারায়ও এই কাল এক নতুন মাত্রা যোগ করে।
গণতন্ত্রের এক ধরনের অনুশীলনও পাল আমলে লক্ষ্য করা যায়। জনসাধারণ মানুষ মিলিত হয়ে গোপাল নামের এক সৎ-সজ্জন সাধারণ মানুষকে তাদের রাজা নির্বাচন করে। এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি। প্রথম কথা হলো, সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু এই শিবভক্ত রাজার রাজত্বের শেষেই তৎকালীন বঙ্গদেশে মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়। সেই অরাজক অবস্থায় নানা বিষয়ে তর্ক-তদন্ত নিশ্চয়ই অনেক হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যমান অবস্থায় কী বিহিত করা যায় তার একটা গণতান্ত্রিক পন্থা তৎকালীন সাধারণ মানুষ যে উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন সেটি ঐ জনগোষ্ঠীর প্রাজ্ঞ বিবেচনা শক্তিকেই তুলে ধরে। অন্যদিকে শক্তিশালী রাজতন্ত্র যে টেকসই ব্যবস্থা নয় এবং তাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণ নেই এই বোধ থেকেও হয়তো গণতান্ত্রিক পন্থায় একজন সাধারণ এবং সৎ মানুষকেই রাজা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে ইতিহাস আমাদের কী শিক্ষা দেয়? শিক্ষা তো এটাই যে, বিশেষ কোন ধর্ম (সেকালের শৈব ধর্ম একালে অন্য যে কোন ধর্ম) বা প্রচ- শক্তিশালী রাজতন্ত্র জনগণের সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে না। বিকল্প পন্থা হিসাবে সংলাপ, সমন্বয় এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্থিত রেখেই সাধারণ মানুষের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা সমীচীন। সেই প্রাচীনকালে জনসাধারণের ভোটে একালের মতো জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব না হলেও এই ভূখন্ডের মানুষ যে অষ্টম শতকেই গণতান্ত্রিকভাবে একজন সাধারণ মানুষকে রাজা নির্বাচন করেছিল তার গুরুত্বও ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে সামান্য নয়।
পাল রাজাদের রাজত্বকালের গুরুত্ব বাংলার ইতিহাসে অনস্বীকার্য। ইতোপূর্বে আমরা তাদের আমলের শিল্প-সংস্কৃতি-চিত্রকলা-ভাস্কর্যের অসামান্য বিকাশের কথা বলেছি। কিন্তু বাংলা ভাষার উৎপত্তিও তো ঘটে পাল আমলেই। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তাঁদের চারশ’ বছরের রাজত্বকালে ধর্মীয় নির্যাতনের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু দশম-একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের (কর্ণাটক) সেন রাজারা তাঁদের আমলে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রীয় ধর্ম-দর্শনের বিকাশের দিকেই অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। তাঁদের আত্যন্তিক ধর্মবোধ অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্য যে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আর সেজন্যই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ মাত্র শতাধিক বছর আগে নেপালের রাজদরবার থেকে উদ্ধার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী।
সেন রাজাদের ধর্মীয় উগ্র শাসনের পরবর্তীকালে প্রায় দু’শ বছরকে যে ‘অন্ধকার যুগ’ বলা হয় তা সৃষ্টির দায়িত্ব ধর্মীয়ভাবে অসহিষ্ণু সেন রাজা এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকের (১২০৪) মুসলিম বহিরাগত বিজয়ীদের উন্মত্ততার উপরেই বর্তায়। তবে বাংলাদেশ চিরকালই সমন্বয়বাদী; নানা মত-পথ-পন্থা-কাল্ট এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বাংলাদেশে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে জাতিসত্তাগত যে বিকাশ ঘটেছে তাতে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মিশ্র আর্য জাতিসত্তাগত উপাদান এবং ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধক, নাথযোগী, বাউল-সুফি, বৈষ্ণব এবং মারফতি-মুর্শিদীর অনুসারী কবিয়াল-বয়াতিসহ গ্রামীণ সাধকেরাই এদেশে এক জীবনঘনিষ্ঠ সমন্বয়বাদী জীবনধারা গড়ে তুলেছেন। বাংলা অঞ্চল চিরকালই কেন্দ্রীয় শাসন থেকে দূরবর্তী অবস্থানে থাকার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ায় তাদের এই সাধনা মানবপন্থী সাধনায় পরিণত হয়েছে। এই সাধনা ধর্মনিরপেক্ষ এবং হৃদয়সংবেদী। বাঙালী জাতিসত্তাই গড়ে উঠেছে নানা জাতিগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস ও মতাদর্শের মিশ্রণের মাধ্যমে। ফলে যে দেশজ চিন্তা-চেতনা ও দর্শনে বাঙালীর বাঙালিত্ব বা দেশগত-সত্তা তার ভিত্তি পরমত সহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় সহনশীলতায়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ না হলে বাঙালী হওয়া সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন : ‘মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজ নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত সংস্কারমুক্ত।’
বাঙালীর ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন এই ঐতিহাসিক বিকাশ ধারার মধ্যেই অনুসন্ধেয়।
২.
আধুনিককালে পাশ্চাত্য বিশ্বে জাতিরাষ্ট্রের মৌল রাষ্ট্রনীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে সেক্যুলারিজম। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে সেকুলারিজম, ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠে। রাজকীয় স্বৈরাচার এবং যাজক সম্প্রদায়ের অনাচারও ছিল তার মূলে। অন্যদিকে মধ্যযুগের ইউরোপের অন্যত্র তিক্ত ধর্মীয় হানাহানি ও ধর্মযুদ্ধের বিনাশী অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছিল এই সেক্যুলারিজম। ফলে রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব, রিফরমেশন, আলোকায়নের প্রজনন জাতিরাষ্ট্রের ধর্মই হয়ে ওঠে আমরা যাকে বলি ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বা পাশ্চাত্য অভিধায় ‘সেকুলারিজম’। এই সেকুলারিজমের সৃষ্টিতে দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তক মিল, কোঁত, রুশো, ভলটেয়ারের অবদান বিরাট। তাঁদের প্রভাবে প্রথমে ফরাসী দেশে, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি গড়ে ওঠে। ঠিক সেই অর্থে যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটলেও ধর্মনিরপেক্ষতা সেখানে প্রাধিকার পায়নি। সেখানে রাজাকে বিশেষ ধর্মের হতে হয় এবং রাজার ধর্মই হয় প্রজার ধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম। তাই বলা যায়, পাশ্চাত্যের নবজাগরণের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে যে খ-িত জাগরণ ঘটেছিল তার সামান্যকিছু প্রভাব পড়েছিল নগরবাসী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে। গ্রাম-বাংলার বিপুল বিশাল অঞ্চলকে তা স্পর্শ করেনি। গ্রাম-বাংলায় যে পাশ্চাত্য রেনেসাঁর প্রভাবিত জাগরণের চেয়েও শক্তিশালী অসাম্প্রদায়িক তথা সমন্বিত সংস্কৃতি ও জীবনধারা গড়ে উঠেছিল তার পেছনে ছিল বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলের বাউল, বৈষ্ণব, সুফি, সাধক, নাথযোগী, বৌদ্ধ-জৈনদের অবদান। তারাই বিশাল বাংলায় পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণু এবং সহঅবস্থানের নীতিতে অভ্যস্ত এক বাঙালী জীবনদর্শন গড়ে তোলেন।
৩.
সেন রাজাদের ধর্মীয় উগ্রশাসনের পরবর্তীকালে দুশ’ বছরের যে ‘অন্ধকার যুগে’র সৃষ্টি হয় তার দায় উগ্রহিন্দুত্ববাদী সেন রাজাদের এবং প্রথম দিকের বহিরাগত মুসলিম দখলদার উভয়ের উপরই বর্তায়। তবে রাষ্ট্র পরিচালনায় বহু মত-পথ-গোত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য ধর্ম-নিরপেক্ষতার কোন বিকল্প নাই। ভারতবর্ষে শাসন করতে এসে মুসলিম শাসকেরা এ বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেই ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র শাসননীতির উদ্ভাবন করেন। আমরা বর্তমান আলোচনায় প্রথম পর্বেই দেখেছি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু আগে থেকেই নানা ধর্মমতের সহ-অবস্থান থাকলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম নিরপেক্ষকতার প্রবর্তক মুসলিম শাসকেরাই। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলিম ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দিন বারানির ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে লেখা তিনখানা বইয়ে। বইগুলোর নাম : তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ফতোয়া-ই জাহানদারি এবং শাফিয়া-ই-নাট-ই আহমদি। তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে বারানি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন : ‘আমার প্রভু ইলতুৎমিশ বলতেন যে, সুলতানের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস (দীনদারি) মেনে রাষ্ট্রশাসন করা সম্ভব নয়; ধর্মবিশ্বাস রক্ষা (দীনপানাহি) করতে পারাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। সুলতানের ঘোষিত আদর্শ ছিল ‘ন্যায় বিচার।’ মধ্যযুগের ভারতে ন্যায় বিচারের অর্থ ছিল : ‘সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা অর্থাৎ ধর্মনির্বিশেষে সকলের অধিকার রক্ষা; সমাজ বা ধর্মসম্প্রদায়ের এক অংশ যেন অন্য অংশের উপর আধিপত্য না করে এমন ব্যবস্থা’। বারানি আলাউদ্দিন খলজির (১২৯৬-১৩১৬) মত উদ্ধৃত করে বলেন, তিনি বলেছিলেন, ‘শরিয়তে কি লেখা আছে, তার পরোয়া না করে রাষ্ট্রের স্বার্থে যা করা উচিত বলে মনে করবেন, সুলতানের তাই করা উচিত২’ একেই বলা হয়েছে ‘জাহানদারি’ বা ইহজাগতিকতা অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা। রাজ্য বিস্তার, ভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভ ও শাসন পরিচালনার জন্য ধর্মনিরপেক্ষকতা ছাড়া অন্য কোন লাগসই বিকল্প তাঁরা খুজে পাননি। এমনকি রাজা ও প্রজা উভয়ই মুসলমান এমন দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিল অপরিহার্য রাষ্ট্রনীতি। উদাহরণ, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ। ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি আর শিল্প-সংস্কৃতির অপূর্ব-বিকাশ ঘটে এবং ধর্মান্ধতা এমনকি ধর্ম-প্রবনতার ফলেও সামাজিক বিপর্যয় ও সংস্কৃতির অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়।
আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে বাংলায় সুলতানী আমলের ইতিহাসের দিকে তাকালে। দিল্লীর মতো বাংলার সুলতানরাও ছিলেন বিদেশী, বিভাষী ও বিধর্মী। তবে তাঁরা শাসক হলেও শাসিতের দেশে নিজধর্মের প্রয়োগে জোরজুলুম ও জবরদস্তি করেননি। বরং বাংলা ও বাঙালীকে ভালবেসে এদেশকে আপন করে নিয়েছিলেন। হোসেন শাহী আমলে বাংলায় এক নব ভাববিপ্লবেরই সূচনা হয়েছিল। একদিকে শ্রীচৈতন্য দেবের হিন্দু ধর্মের গণমুখী সংস্কারমূলক ভক্তিবাদী আন্দোলন ও ধর্মীয় ছুঁৎমার্গমুক্ত মানবপন্থী সাধনাধারা; অন্যদিকে মুসলিম মরমী সুফি-সাধকদের অধ্যাত্মচেতনাপ্রসূত মানবতাবাদ বাংলার সামাজিক জীবনে এনেছিল এক নবতর সাংস্কৃতিক উজ্জীবন। এই ভাব-আন্দোলনকে হয়ত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলার নবজাগরণ বলে আখ্যাত করা চলে। কারণ, বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূত্রপাত ঘটে। সুলতানদের উদারতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মহাভারত ও ভাগবৎ এই প্রথম সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত হয়। ভাগবৎ অনুবাদ করে মালাধর বসু সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ’র কাছ থেকে ‘গুণরাজখান’ উপাধিতে ভূষিত হন। সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই নীতি সমন্বয়বাদী বাঙালী জাতিসত্তা গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তাই নয়, বহিরাগত এই মুসলিম সুলতানেরা বিকাশমান বাঙালী জাতি গঠনে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন ইতিহাসনিষ্ঠ কোন বাঙালীর তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। এ কথা বলাইবাহুল্য যে, এই জাতি গঠন প্রক্রিয়াটি নৃ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে শুরু করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। বাঙালী জাতি ও বাঙালিত্ব নিয়ে এক ধরনের অহঙ্কারও বোধ করেছেন সুলতানেরা। সেজন্যই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিজেকে ‘শাহে বাঙালীয়ান’ বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাবরাও বাঙালীদের দেশজ উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সুলতানদের প্রবর্তিত ধারাকে আরো গভীরতা দান করেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ও আলীবর্দী খাঁর বেড়াভাসান উৎসব, বাংলা নববর্ষে পুণ্যাহ উৎসবে যোগদান এর প্রমাণ বহন করে। অতএব, বঙ্গদেশে ধর্ম-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি নির্মাণে মুসলিম শাসকদের অবদান দিকনির্দেশক। দিল্লী ও বাংলার সুলতানদের এই প্রয়াসকে একটি গ্রহণযোগ্য ও চলমান ঐতিহাসিক ধারা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েই নেহেরু-মওলানা আজাদ স্বাধীন ভারতে এবং বঙ্গবন্ধু-তাজউদ্দিন ও তাঁদের সহযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নবীন গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। উপমহাদেশের ইতিহাস জানতেন বলেই তাঁরা ওই প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন।
মুসলিম সুলতান ও নবাবেরা বাঙালীর মানস প্রবণতাকে খুব যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই সে-স্পর্শকাতর বিষয়ে কোন বিরূপ ধারণা বা অসূয়া পোষণ না করে বাঙালীর আচার-অনুষ্ঠান উৎসবকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন থেকে দূরে থাকা গ্রামীণ বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি ধারার বিকাশে কোন বাঁধার সৃষ্টি হয়নি। তারা সব সময়েই তাদের নানা মত-পথ ও পন্থার বহুত্ববাদী (Pluralistic) সংস্কৃতিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদী নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।
বাংলার মানুষের এই মানসিক সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র গঠনের একটি প্রাথমিক উদ্যোগ চোখ পড়ে। একজন ভাষ্যকার বলেছেন : ‘অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর সুবায় সুবায় নতুন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্য করিলে এসব রাষ্ট্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব চোখে পড়ে। ইউরোপে নতুন বাণিজ্য পথ আবিষ্কারের সঙ্গে এই শ্রেণীর প্রথম সূত্রপাত; অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কৃপায় এই শ্রেণীটি ইতোমধ্যেই বিশেষ অর্থবান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া নতুন নতুন শহর বন্দর গড়িয়া উঠিল। গ্রাম, গ্রামান্তর হইতে নিপুণ কারিগর শ্রেণী ও অনিপুণ মজুরের দল সুরাট, হুগলি সুতানটি ও মুর্শিদাবাদে ভিড় জমাইল। বাংলাদেশে পলাশি যুদ্ধের সমকালে এই শ্রেণীর রূপটি খুব স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে। মুঘল সামন্ততন্তের ইতিহাসে যাহা কখনও পড়ে নাইএই সময় তাহা দেখা যায়। দেখা যায় সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্য হইতে একটি সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণী বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিলক্ষণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনাইয়া নেয়ার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। আর তাহার প্রথম ধাপ হিসাবে বাংলার মসনদে বসাইবার জন্য ‘হাতের লোক’ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাংকার জগৎ শেঠ, বণিকরাজ উমিচাঁদ, নিমকের একচেটিয়া কারবারি খোঁজা বাজিদ, ইংরেজ কুঠির সঙ্গে গোপন কারবারে প্রভূত বিত্তশালী ঢাকার ডেপুটি দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ এই নতুন শ্রেণীর প্রতিনিধি। উল্লেখযোগ্য যে ইহাদের একজন জৈন, একজন নানকপন্থী, একজন মুসলমান, অপরজন বাঙালী হিন্দু অর্থাৎ ইহাদের ঐক্যের ভিত্তি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। ইহারা আবার বণিক পুঁজির (Mercantile Capital) প্রতিনিধি। আর এই পুঁজিই সর্বদেশে ধনতন্ত্রের অগ্রদূত। এই শ্রেণীর দ্বারা এদেশেও হয়ত বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা রচিত হইত।’ কিন্তু ইংরেজরা এদেশ দখল করে নেয়ায় সৃজ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এদেশে সূচনালগ্নেই চাপা পড়ে যায়। এবং ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাকার লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকেরা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে শাসন করার লক্ষ্যে উরারফব ধহফ জঁষব চড়ষরপু চালু করে। এভাবেই তারা ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর ভারতবর্ষে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে দেয়। তারই বিষময় ফল, ধর্মের ভিত্তিকে ভারতবর্ষকে ভাগ করে ‘ভারত’ ও ‘পাকিস্তান’ নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিপুল নিরীহ মানুষের প্রাণহানি, অগণন মানুষের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশ ত্যাগ ও দুঃসহ বাস্তুহারা জীবন গ্রহণ। বাংলার সাধারণ মানুষের মানবপন্থী সাধনা, দিল্লীর সুলতানদের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন তথা ইহ জাগতিকতা এবং বাংলার সুলতানদের সমন্বিত জীবনবাদী ধারা পরিত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব গ্রহণ করায় এই বিশাল মানবিক বিপর্যয় ঘটে।
৪.
‘দুই-পাকিস্তান’ ভিত্তিক আন্দোলন অংশ নিলেও অপরাষ্ট্র [এক] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব-বাংলার বাঙালী বুঝতে পারে তারা প্রতারিত হয়েছে। এখন তারা শোষণ-নির্যাতন ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার। তাই ১৯৪৭-৪৮ সালেই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী শুরু করে নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তাভিত্তিক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সে-আন্দোলনে বাঙালীর সংস্কৃতি ও রাজনীতি একাত্ম হয়ে যায়। ফলে বাংলা ভাষা ও বাংলার ভূপ্রকৃতিভিত্তিক নবচেতনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। তখনই প্রকৃত ধার্মিক, বিবেকবান ও ইতিহাসনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতিসত্তার স্বরূপটি নির্ধারণ করে দেন এই ভাষায় :
‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন দাগ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জোটি নেই’ (পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, কার্জন হল, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮, সভাপতির ভাষণ)।
প্রখ্যাত পন্ডিত ও ধর্মবেত্তা উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক সূত্র ধরে নিজেই সংস্কৃতি ক্ষেত্র থেকে বাঙালী জাতিসত্তা রক্ষার আন্দোলন শুরু করেন। ড. শহীদুল্লাহ্র দিক-নির্দেশক চিন্তাধারাকে মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করে পূর্ব-বাংলার নবপ্রজন্মের রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সক্রিয়বাদীরা (Cultural Activists) বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পাটাতনের ওপর নবধারার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগ্রামের সূত্রপাত। এরই ধারাবাহিকতায় ২৩ বছর ধরে চলে উপনিবেশ-বিরোধী, সামরিক শাসনবিরোধী জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। ১৯৬২-এ ‘দেশ ও কৃষ্টি’ শীর্ষক পাঠ্য বইয়ে বাঙালী জাতিসত্তা-বিরোধী তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ৬ দফা ভিত্তিক পূর্ব-বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আন্দোলন বাঙালীর স্বাধিকার সংগ্রামকে গুণগত রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্তরে উন্নীত করে। এই আন্দোলন দমনে পাকিস্তান সরকার বাঙালীর জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে শুধু গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁকে মুক্ত করার দুর্বার আন্দোলনকে জনগণ ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করে। গণঅভ্যুত্থানে মুক্ত শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হয়ে পূর্ব-বাংলার অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতার মর্যাদা লাভ করেন। এই গণঅভ্যুত্থান ছিল বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের ড্রেস রিহার্সাল স্বরূপ। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয়ের পরও বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি পাকিস্তানী স্বৈর-শাসকেরা। ফলে পূর্ব বাংলার সাড়ে সাতকোটি মানুষের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েও তিনি ক্ষমতা পাননি। ফলে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ৭ মার্চ তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন : ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই অনন্য ভাষণে তিনি মুক্তি সংগ্রামের জন্য গেরিলা যুদ্ধের রূপরেখাও নির্দেশ করে দেন। বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনা ও তাঁর যোগ্য সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যদের নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাঙালীর হাজার বছরের স্বপ্নের, সংগ্রামের, সাধনার, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্যমূলক অর্থনৈতিক আদর্শভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র, বাংলাদেশ। পাকিস্তানী বন্দী শিবির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে ১৯৭১-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন : ‘আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।’ এর আগে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে ১৯৭১-এর ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রেও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রনীতি হিসাবে গৃহীত হয় এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ করা হয়। তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় : ‘ধর্মনিরপেক্ষকতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার এবং কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হলো।’
এমন এক রাষ্ট্র গঠন ও সংবিধান রচনা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিাহাসিক বোধ, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। বাঙালী জাতির এর চেয়ে বড় সাফল্য, বড় অর্জন ইতিহাসে আর নেই। বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রশংসা করে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Center for Inquiry-Transnational-এর শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালক ড. অস্টিন ডেইসি বলেন, : Thomas Jefferson could have learnt a lot about secular democracy from Sheikh Mujibur Rahman.” কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস এবং মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্র ও ধর্ম-নীতির ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বোধের পশ্চাৎপদতার জন্য স্বৈরশাসক জিয়া-এরশাদ এবং পাকিস্তানের গোপন দোসর মোশতাক ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে বাঙালীর হাজার বছরের স্বপ্নের জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের মূল স্রষ্টা শেখ মুজিবকেই শুধু হত্যা করেনি, রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিবর্তন করে একে একটি পাকিস্তানী ধাঁচের ধর্মপ্রবণ পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গোটা বাঙালী জাতিকে চার মূল রাষ্ট্রনীতির পেছনে যেভাবে সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন তার বিপরীতে উপরোক্ত তিন শাসক তাদের কূপমন্ডক ও অপরাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সরকারের দেয়া ’৭২-এর সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে এমন কলুষিত করে ফেলে যে তা এখন জাতিকে দুটি ক্ষতিকর ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশকে দুঃশাসন, সামরিক ও ছদ্মসামরিক স্বৈরাচারের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নানা প্রতিকূলতায় বিপন্ন, আর ধর্মীয় জঙ্গীবাদী ধর্মান্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জিয়ার দলের সঙ্গে জোট বেঁধে বাংলাদেশে দাঁপিয়ে বেড়াতে থাকে। স্বাধীনতাবিরোধী ও রাজাকারদের মন্ত্রী বানিয়ে তাদের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানোর সুযোগ করে দেয়া হয়। জিয়া যেখানে গোপনে স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মব্যবসায়ী জামায়াতকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন, খালেদা জিয়া সেখানে মন্ত্রিত্ব দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন এবং জিয়া-পুত্র তারেক রহমান প্রকাশ্যে বলেছেন : ‘বিএনপি ও জামায়াত একই পরিবারের সদস্য’। এই সূত্রেই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলসত্তা-বিরোধী একটি শক্তিশালী চক্র নানা ক্রুর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র-জালের ছক ফেলে লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত জনগণের এই রাষ্ট্রটিকে তার জন্ম-ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথে বিকশিত হতে দেয় নাই। আর এজন্যই বাড়-বাড়ন্ত হয় দুর্বৃত্তায়ন দুঃশাসন আর স্বৈরাচার ও জঙ্গীবাদের। ফলে মুজিব-তাজউদ্দীনসহ বহু দেশপ্রেমিকের প্রাণ নিয়েও রাষ্ট্রশক্তির গোপন কুঠুরিতে স্থায়ী আসনপাতা দুষ্ট চক্র তথা ধর্মব্যবসায়ী বা উগ্রধর্মীয় জঙ্গী ও তাদের মদদ দাতারা বাংলাদেশকে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের বৃত্ত ভেঙ্গে বের হতে দিচ্ছে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল সঙ্কট এখানেই। এদের চিরতরে দমন এবং স্বাধীনতাবিরোধিতা ও যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিতে করাতে না পারলে বাংলাদেশ বিপদমুক্ত হবে না। বর্তমান সরকার এ কাজে হাত দিয়েছে। সর্বোচ্চ বিচারালয় শাসনযন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। এরফলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের মৌল রাষ্ট্রসত্তার পুনর্গঠনের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ফাঁসির রায় আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে, দেশে আইনের শাসন ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক হত্যাকান্ড চিরতরে বন্ধ করার জন্য পলাতক খুনীদের বিদেশ থেকে নিয়ে এসে তাদেরও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে হবে।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনে বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিক ঐতিহাসিক সংগ্রাম ছিল সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। এ ব্যাপারে ১৯৬০-এর দশকে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে নিউক্লিয়াস গঠন, পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানাসহ উপযোগী স্লোগান প্রচার বিশেষ করে ‘জয় বাংলা’র মতো লক্ষ্যভেদি শস্ত্র মরণাস্ত্রে সজ্জিত হানাদার পাকিস্তানীদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অতি স্বল্প সময়ে তিনি এবং তাঁর সরকার যে সংবিধান (১৯৭২) তৈরি করেন বাংলাদেশকে তা দক্ষিণ এশিয়ার বিপুল সম্ভাবনাময় এবং মানবকল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত করে।
মনে রাখতে হবে, কোন দেশকে সেনাবাহিনী রক্ষা করতে পারে না। সামাজিক ন্যায় এবং সুশাসনই দেশকে রক্ষা করতে পারে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা দেশরক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। যে দেশ নানা ধর্মের হানাহানিতে বিভক্ত সে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সবসময়ই ঝুঁকির মুখে থাকে। পাকিস্তানে এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমাদের এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।
ঢাকা, বাংলাদেশ সোমবার ১৯ মে ২০২৫, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২