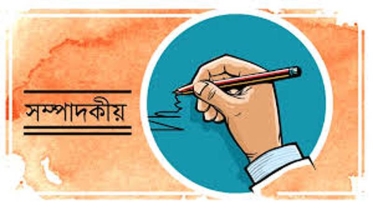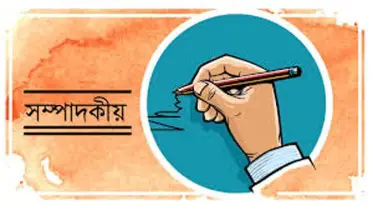ছবিঃ সংগৃহীত
কারাগারের ইতিহাস সাম্প্রতিককালের নয়। শাস্তি প্রদানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেল বা কারাগারের অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই নানা আকারে দেখা যায়। কারাগারের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয় অপরাধের বিরুদ্ধে, অপরাধী থেকে সমাজকে রক্ষা করা। কারাগারের ইতিহাস, অপরাধী ব্যক্তিদের আটক রাখার স্থান হিসেবে এর ব্যবহার অনেক পুরনো। প্রাথমিক পর্যায়ে কারাগার বিচার বা সাজা কার্যকরের অপেক্ষায় থাকা বন্দিদের আটক রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার হতো।
বলা হয় কারাগারগুলো সামাজিক প্রতীক্ষার প্রাচীনতম দেয়াল। তিন শতক ধরে কারাগার বাইরের দুনিয়া থেকে বন্দিদের রক্ষা এবং অপরাধ অনুযায়ী সাজা প্রদানের মাধ্যমে সমাজকে নিয়ন্ত্রণের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়েছে। কারা ব্যবস্থা অপরাধের প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করে। সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে যেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপরাধীদের আরো অপরাধ সংঘটিত করা থেকে বিরত রাখা যায়। ঐতিহাসিকভাবেই কারাগার এক রহস্যময় দেয়ালঘেরা ভিন্ন দুনিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে কারাগারএ উপমহাদেশে কারা ব্যবস্থার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীন ভারতে যুদ্ধবন্দি ও রাজার শত্রুদের হেফাজতের জন্য রাজধানীতে কারাগার তৈরি হয়েছিল। মহাভারত, রামায়ণ, ঋগবেদ, মনুস্মৃতির মতো শাস্ত্র কিংবা অনেক প্রাচীন শিলালিপি ভারতের ফৌজদারি আইন শাস্ত্রের উৎস। যিশুখ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগেই এসব শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতীয় সমাজে কারাগারের অস্তিত্ব বৈদিক যুগ থেকেই দেখা যায়, যেখানে অসামাজিক উপাদানগুলোকে রক্ষা করার জন্য শাসকদের দ্বারা চিহ্নিত একটি জায়গায় রাখা হয়েছিল। ব্যক্তি, জমি ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলোকে চরম ঘটনা বলে বিবেচনা করা হতো। এসব অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল অঙ্গচ্ছেদ, মৃত্যু বা প্রায়শ্চিত্ত। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল একধরনের সাজা। তবে শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড প্রাচীনকালে ততটা স্বীকৃত ছিল না। প্রথম দিকে কারাগারগুলোয় বন্দি হিসেবে রাখা হতো অপরাধের বিচার ও রায় এবং পরবর্তী সময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত। প্রাচীন ভারতে সমাজ কাঠামো তৈরি হয়েছিল মনুসংহিতা দ্বারা এবং যাজ্ঞবল্ক্য, কৌটিল্য ও অন্যরা সে নীতিগুলো বিশদ ব্যাখ্যা করে গেছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে কারাগার বিষয়ে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে কারাগারের একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থার কথা বলেছেন। অপরাধীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কারাগারে রাখা হয়। কারাবাসের মূল লক্ষ্য ছিল অন্যায়কারীদের সমাজ থেকে দূরে রাখা, যেন তারা সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের ‘অপবিত্র’ করতে না পারে।
এ কারাগারগুলো ছিল স্যাঁতসেঁতে, আলোহীন। পয়োনিষ্কাশনের কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। আদতে সুস্থ মানুষ বসবাসের কোনো পরিবেশ ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণনা করেছিলেন, একজন বন্দিকে কারাগার থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন এক ব্যক্তি, ফলে ওই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। মনুসংহিতায় একটি বিশেষ শাস্তিস্বরূপই কেবল কারাদণ্ড দেয়া হতো, যা ছিল ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ চুরি করার অপরাধ। বিষ্ণু এমন একজন ব্যক্তির জন্য কারাদণ্ডের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যিনি একজনের চোখে আঘাত দিয়েছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কারাগার নির্মাণ এবং কারা ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্য কারাগার নির্মাণে নারী ও পুরুষের আলাদা আবাসনের ব্যবস্থা ও বন্দিদের জীবনমান উন্নতির জন্য তাদের সমস্যা সমাধানে আলোচনা করেছেন। অশোকের শাসনের শুরুর দিকে একটি সংস্কারবিহীন কারাগার ছিল, যেখানে বেশির ভাগ ঐতিহ্যবাহী, নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হতো। এ কারাগার থেকে জীবিত কেউ ফিরে আসেনি। ফলে প্রতীয়মান হয় যে অশোকের সময়ে কারাবন্দিদের অবস্থা ভালো ছিল না। হিউয়েন সাংয়ের জীবনী থেকে জানা যায় ভারতে কারাবন্দিদের সঙ্গে সাধারণত কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণই করা হতো। কারাগারে অমানবিক জীবনযাপন করতে হতো। কারাগারের প্রাথমিক স্থানগুলো ছিল শহরের বড় উঁচু উঁচু কাঠের ঘর। এসব কারাগার থেকে বন্দিরা প্রায়ই পালাতেন। অঙ্গচ্ছেদ বা মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কারাদণ্ডকে প্রগতিশীল শাস্তি বিবেচনা করা হয়। প্রচীনকালে থেকে সে বিবর্তনই ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হয়।ভারতবর্ষের কারা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কাশ্মীরি কবি বিলহনের কাব্য চৌরপঞ্চশিকায়। মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় কারগারে বসে কবি এ রচনা সম্পন্ন করেন। রাজা মদনভৈরামা তার কন্যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের শাস্তি হিসেবে কবি বিলহনকে মৃত্যুদণ্ড দেন। মধ্যযুগবলা চলে মধ্যযুগীয় কারাগার ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতের মতোই ছিল। এ সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্গের ভেতরে কারাবন্দিদের রাখা হতো। কারাগারগুলোকে বর্বর নির্যাতন ও প্রতিশোধমূলক যন্ত্রণার আদিম স্থান হিসেবে গণ্য করা হতো। অপরাধীর মনে কারাগার বা শাস্তি সম্পর্কে ভয় ধরিয়ে দেয়া ছিল এমন ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। মোগল শাসনে শাস্তির বিধান ছিল চার ধরনের। হাদ, কিসাস, দিয়া ও তাজির। শাস্তির মধ্যে ছিল মৃত্যুদণ্ড, জরিমানা এবং পদবি, সম্পত্তি, অর্থ বাজেয়াপ্ত করা। অবমাননা, অঙ্গচ্ছেদ ও অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনের মতো শাস্তির বিধান প্রায় সব যুগেই ছিল। সাধারণ অপরাধীদের ক্ষেত্রে মধ্যযুগেও কারাদণ্ড বহুল ব্যবহৃত কোনো শাস্তি ছিল না। এটি প্রধানত বিচারাধীন সব ব্যক্তিকে যেমন রাজনৈতিক, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আটকের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হতো।
মারাঠা আমলেও শাস্তিস্বরূপ কারাবাসের ব্যবস্থা খুব বেশি প্রচলিত ছিল না। মৃত্যু, অঙ্গচ্ছেদ, শারীরিক নির্যাতন, জরিমানাই ছিল মূল শাস্তির বিধান। প্রাচীন ও মোগল আমলের মতোই শাস্তির বিধান ছিল এ সময়ে। দুর্গে বন্দি বা আদাবখানা নামে পরিচিত কিছু কক্ষ ছিল কারাবাসের জন্য। কারাবন্দিদের এ যুগে শ্রাদ্ধের মতো অনুষ্ঠানে বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হতো। তবে কারাবন্দি থাকা অবস্থায় আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ বন্ধ থাকত। তবে রাষ্ট্র তখন থেকেই কারাগারের অভ্যন্তেরর সব কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থ জোগান দিত।ঔপনিবেশিক আমলকারাদণ্ডের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা ভারতীয় ইতিহাসের এসব যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবণতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। ইংরেজ শাসকরা একটি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা মোগল শাসকদের থেকে পেয়েছিল, যার শাস্তি ব্যবস্থাগুলো ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ব্রিটিশ শাসন আমলের শুরুতেও শাস্তির বিধানগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড প্রচলন ছিল না তেমন। মৃত্যুদণ্ড ছিল অপরাধের জনপ্রিয় শাস্তি। কারা প্রশাসকদের থেকে আশা করা হতো তারা কঠোর থেকে কঠোর নির্যাতনের মাঝে রাখবে কারাবন্দিদের। সিপাহি বিদ্রোহ-পরবর্তী যুগে কারাগার পুনর্গঠন করা হয়।
ভারতীয় আদালতে কারাগার বিধি লঙ্ঘনের জন্য আলাদা শাস্তির বিধান ও প্রণয়ন হয়। ১৮৫৯ ও ১৮৬০ সালে যথাক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রণীত হয়। ভারতীয় জেল আইন (১৮৯৪) অনুসারে বেশকিছু রাজ্যে কারাগার স্থাপন হয়, পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনায় জেল ম্যানুয়াল গঠন করা হয়। ভারতীয় ফৌজদারি আইন জেল আধিকারিকদের ক্ষমতা, কার্যাবলির বর্ণনা এবং কারা প্রশাসনকে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক ক্ষমতার অধীনে দেশের জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা সামগ্রিক কাঠামোর সঙ্গে জড়িত ছিল। আঠারো শতক ছিল শাস্তির ধারণাসহ প্রথাগত চিন্তাধারা ও রীতিনীতির জন্য চ্যালেঞ্জের বিষয়। ভারতে সমসাময়িক কারা ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার। ব্রিটিশদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এ অঞ্চলে নতুন নতুন প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর দেখা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অধীনে ১৪৩টি দেওয়ানি জেল, ৭৫টি ফৌজদারি কারাগার এবং বাংলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে ৭৫ হাজার ১০০ জনের থাকার ব্যবস্থাসহ ৬৮টি মিশ্র জেল তৈরি করা হয়। ১৮৩৪ সালে ভারতে ম্যাকলের উদ্যোগে আধুনিক কারা ব্যবস্থা দেখা যায়। ভারত সরকার এ নীতিতে সুপারিশ করেছিলেন যে প্রতিটি কারাগারে এক হাজারজনের বেশি বন্দি যেন না রাখা হয়। সুপারিশ অনুসারে ১৮৪৬ সালে আগ্রায় প্রথম ভারতীয় কেন্দ্রীয় কারাগার স্থাপন করা হয়। স্বাধীন ভারতের কারা ব্যবস্থার অনেক কিছুই ১৮৯৪ সালে ব্রিটিশদের প্রণীত আইন দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে।
লেখক: মুশফিকুর রহমান, তরুণ গবেষক ও অনুবাদক এবং শিক্ষার্থী, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
নোভা