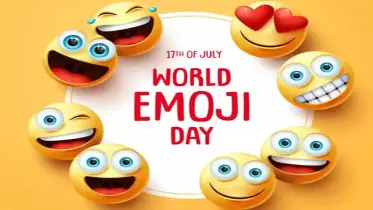সাগরদাঁড়িতে কবির আবক্ষ মূর্তি। মধু কবির সমাধিলিপি
বাংলা সাহিত্যে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম প্রচলনকারী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইশ’তম জন্মবার্ষিকী আজ ২৫ জানুয়ারি। সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি মধু কবি নামেই সমধিক পরিচিত। এ বছর কবির জন্মদিন পালন উপলক্ষে তার জন্মভূমি যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে গত ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে এখনো চলছে নয়দিনব্যাপী মধুমেলা।
যেকালে ডেপুটি হওয়া ছিল জীবনের লক্ষ্য, সেকালে তার ধ্রুব লক্ষ্য ছিল কবি হওয়া। যেকালে বাঙালিরা অহঙ্কারে ফেটে পড়তেন সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল হয়ে, সেকালে তিনি কেবল ব্যারিস্টার হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিলেত গেছেন এবং সে সময়ের তুলনায় বিত্তও উপার্জন করেছেন যথেষ্ট। কিন্তু তা দিয়ে অন্য পাঁচজনের মতো জমি কেনেননি। দু’হাতে তা উড়িয়েছেন।
তিনি এমন অসাধারণ ছিলেন যে, সে সময়ের লোকেরা কেউ তাকে ঘৃণা করেছেন, কেউ ভালোবেসেছেন, কেউ বা করুণা করেছেন। কিন্তু কেউ তাকে অস্বীকার করতে পারেনি। বলছিলাম মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা। এই মহা কবির শেষ জীবন কেটেছে অনাদর আর অবহেলায়। বলা যায় বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে।
১৮৭৩ সালের মার্চ মাসনাগাদ কবির স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, ‘ঢাকা থেকে ফেরার পর। হেনরিয়েটার স্বাস্থ্যও খারাপ হতে থাকে। এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন, সত্যি সত্যি মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে, বিশেষ করে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, তিনি ব্যাকুল হয়ে যান।
এতো আদরের দুই পুত্র এককালে বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয়ে শেষে কি অনাহারে মারা যাবে, অথবা ভিক্ষে করবে অন্যের দ্বারে? আর বয়ঃসন্ধিতে উপনীত আদরের কন্যা শর্মিষ্ঠার বা কি উপায় হবে? কন্যার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হেনরিয়েটাও শিউরে ওঠেন। এ পরিস্থিতিতে কবি মরিয়া হয়ে বালিকা কন্যার বিয়ে ঠিক করেন। মে মাসের ৭ তারিখে মাত্র ১৩ বছর ৭ মাস ২২ দিন বয়সে একটি প্রতিশ্রুতিতে ভরা এক কিশোরীর বিয়ে হলো তার ঠিক দ্বিগুণ বয়সী সামান্য-শিক্ষিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এক যুবকের সঙ্গে।
শর্মিষ্ঠার বিয়ের ঠিক পর ভাঙা মন আর অক্ষম দেহ নিয়ে সপরিবারে যান কলকাতার উত্তরপাড়ায়। চার বছর আগে যেখানে উঠেছিলেন, এবারেও উঠলেন সেই একই জায়গায় লাইব্রেরির ওপর তলায়। উত্তরপাড়ায় তার আশ্রয়দাতাদের অন্যতম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। কবি সেখানে ছিলেন ছয় সপ্তাহ। ওই বছরের গোড়ার দিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে গৌরদাস বসাক বদলি হয়ে এসেছিলেন হাওড়ায়। তিনি এ সময়ে একাধিক বার উত্তরপাড়ায় গিয়ে মাইকেলকে দেখে আসেন।
শেষ বার সেখানে তিনি যে দৃশ্য দেখতে পান, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি তার বিবরণ দিয়েছেন: ‘মধুকে দেখতে যখন শেষ বার উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগারের কক্ষে যাই, তখন আমি যে-মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখতে পাই, তা কখনো ভুলতে পারব না। সে তখন বিছানায় তার রোগযন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছিল। মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। আর তার স্ত্রী তখন দারুণ জ্বরে মেঝেতে পড়ে ছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মধু একটুখানি উঠে বসলো। কেঁদে ফেলল তারপর। তার স্ত্রীর করুণ অবস্থা তার পৌরুষকে আহত করেছিল।
তার নিজের কষ্ট এবং বেদনা সে তোয়াক্কা করেনি। আমি নুয়ে তার স্ত্রীর নাড়ি এবং কপালে হাত দিয়ে তার উত্তাপ দেখলাম। তিনি তার আঙুল দিয়ে তার স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিম্নকণ্ঠে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন: ‘আমাকে দেখতে হবে না, ওঁকে দেখুন, ওঁর পরিচর্যা করুন। মৃত্যুকে আমি পরোয়া করিনে।’ বাল্যবন্ধুর অন্তিম দশা দেখে গৌরদাস স্বভাবতই বিচলিত বোধ করেন।
তিনি যে তার জন্যে বেশি কিছু করতে পারতেন, তা নয়। তবু তিনি তাকে অবিলম্বে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। পরিবার নিয়ে কবি বজরায় করে পরের দিন কলকাতা যাত্রা করলেন। হেনরিয়েটাকে ওঠানো হলো তার জামাতা উইলিয়াম ওয়াল্টার এভান্স ফ্লয়েডের বাড়িতে, ইংরেজ আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাড়ায় ১১ নম্বর লিন্ডসে স্ট্রিটে। আর কবির নিজের ওঠার মতো কোনো জায়গা ছিল না। উত্তরপাড়ায় যাওয়ার আগেই তিনি তার এন্টালির বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে মনে হয়।
উঠলেন গিয়ে আলিপুরের জেনারেল হসপিটালে। তবে অচিরেই তার স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির দিকে যায়। যকৃৎ, প্লীহা এবং গলার অসুখে তার দেহ অনেক দিন আগেই জীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু যখন হাসপাতালে ভর্তি হন তখন যকৃতের সিরোসিস থেকে দেখা দিয়েছিল উদরী রোগ। হৃদরোগও ছিল তার। মারা যাচ্ছেন শুনে আলিপুরের হাসপাতালে মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য গুডিব চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়সহ অনেকে এসেছিলেন তাকে দেখার জন্যে। তার চরম দুরবস্থার খবর শুনেও এতদিন যারা খোঁজখবর নিতে পারেননি, তাদেরও অনেকে।
হাসপাতালে তিনি ছিলেন সাত অথবা আট দিন। এ সময়ে তিনি কিছু সেবাযতœ পেলেও, খুব মানসিক শান্তিতে ছিলেন বলে মনে করার কারণ নেই। পরিবার সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তা এবং হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার উদ্বেগ তাকে নিঃসন্দেহে খুব বিচলিত করেছিল। এরই মধ্যে ২৬ জুন (১৮৭৩) তারিখে এক পুরোনো কর্মচারীর কাছে খবর পেলেন হেনরিয়েটা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।
তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৭ বছর ৩ মাস ১৭ দিন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন মাইকেলের ভালোবাসার টানে। তিনি অনেক দিন থেকে মুমূর্ষু ছিলেন। সুতরাং তার মৃত্যুসংবাদ কবির কাছে খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবু কবি ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন: বিধাতা, তুমি একই সঙ্গে আমাদের দু’জনকে নিলে না কেন? হেনরিয়েটার ভালোবাসা এবং নীরব ত্যাগের কথা অন্য সবার চেয়ে তিনিই ভালো করে জানতেন।
সুতরাং যত অনিবার্য হোক না কেন, হেনরিয়েটার প্রয়াণে মৃত্যুপথযাত্রী কবি মর্মাহত এবং বিষণœ হয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালের ২৮ জুন সমস্ত আশা-ভরসাহীন, রোগ-কাতর, বিষণœ কবি যখন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন, তেমন সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী তার শেষ স্বীকারোক্তি আদায় করতে। তিনি কোন কোন পাপের কথা স্বীকার করে বিধাতার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, কেউ তা জানেন না।
জীবনকে যিনি যদ্দূর সম্ভব উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে সেই কবি কতটা আকুল হয়েছেন তাও আমাদের অজানা। কিন্তু কৃষ্ণমোহন এবং চন্দ্রনাথ যখন তাকে জানান যে, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং তাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হবে, তা নিয়ে গোলযোগ দেখা দিতে পারে, তখন কবি যে-নির্ভীক উত্তর দিয়েছিলেন, তা আমাদের জানা আছে। তিনি বলেছিলেন, মানুষের তৈরি চার্চের আমি ধার ধারিনে।
আমি আমার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে তার সর্বোত্তম বিশ্রামস্থলে লুকিয়ে রাখবেন। আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন- আপনাদের দরজার সামনে অথবা কোনো গাছ তলায়। আমার কঙ্কালগুলোর শান্তি কেউ যেন ভঙ্গ না করে। আমার কবরের ওপর যেন গজিয়ে ওঠে সবুজ ঘাস। ২৯ জুন রবিবার মাইকেলের অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে এলো।
তার হিতাকাক্সক্ষী এবং সন্তানরা এলেন তাকে শেষ বারের মতো দেখতে। এমন কি, জ্ঞাতিদেরও একজন এসেছিলেন তাকে দেখতে। জীবনের শেষ দু’বছর তার নিদারুণ দুর্দশায় সহায়তার হাত প্রসারিত না-করলেও, শেষ মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখে অনেকেই করুণায় বিগলিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্রামহীন এবং রোগজীর্ণ দেহ কবি আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। বেলা দুটোর সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন চিরদিনের জন্যে।
কৃষ্ণমোহনদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। তার মৃত্যুর পর সত্যি সত্যি তার শেষকৃত্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কলকাতার খ্রিস্টান সমাজ তার দীক্ষার ঘটনা নিয়ে ঠিক তিরিশ বছর আগে একদিন মহা হৈচৈ করলেও, মৃত্যুর পর তাকে মাত্র ছয় ফুট জায়গা ছেড়ে দিতেও রাজি হলো না। আষাঢ় মাসের ভ্যাপসা গরমের মধ্যে তার অসহায় মরদেহ মর্গেই পচতে থাকে। তখন সাহস নিয়ে এগিয়ে আসেন একজন ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজক। তিনি কবির মরদেহ সমাধিস্থ করার সংকল্প প্রকাশ করেন।
প্রায় একই সময়ে অ্যাংলিকান চার্চের একজন সিনিয়র চ্যাপলেইন রেভারেন্ড পিটার জন জার্বোও বিশপের অনুমতি ছাড়াই তার দেহ সামাধিস্থ করার উদ্যোগ নেন। ডক্টর জার্বো ছিলেন ৮৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত সেইন্ট জেমসেস চার্চের প্রধান পাদ্রী। ৩০ জুন বিকেলে-মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টারও পরে কবির মরাদেহ নিয়ে তার ভক্ত এবং বন্ধু বান্ধবসহ প্রায় হাজার খানেক লোক এগিয়ে যান লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্তানের দিকে।
তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে কলকাতার বাইরে থেকেও অনেক লোক এসেছিলেন বলে জানা যায়। নানা ধর্মের এবং বর্ণের লোক ছিলেন এদের মধ্যে। তবে একদিন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ নিজের গ্রন্থ উৎসর্গ করে কবি যাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত করেছিলেন, তাদের কেউ এই ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না। লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্তানে এর চার দিন আগে হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কবির জন্যে কবর খোঁড়া হয় তার কবরের পাশে। ডক্টর জার্বোই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন।
সেকালের দেশীয় সমাজে তার চারদিকে যারা বাস করতেন, তাদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক প্রতিভাবান। জনারণ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে তাকে চোখে পড়ার মতো গুণাবলী তিনি প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি একা যতটা এগিয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ তা করেননি। বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন।
জীবনের শেষ দুতিন বছরে তিনি ঈর্ষার অযোগ্য যে-করুণ পরিণতি লাভ করেছিলেন এবং তাকে সমাধিস্থ করার ঘটনা নিয়ে যে কুৎসিত নোংরামি দেখা দিয়েছিল, তা থেকে তার নিঃসঙ্গতার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তার অসামান্য প্রতিভা এবং আকাশচুম্বী আত্মবিশ্বাস তাকে যে সীমাহীন অহঙ্কার দিয়েছিল, তাও তার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।বিত্ত দিয়ে গত শতাব্দীতে অনেকেই জাতে উঠেছেন, সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছেন।
যতদিন মাইকেল সচ্ছল ছিলেন, ভোজ দিতেন, বিনে পয়সায় মামলা করে দিতেন, ততদিন দেশীয় সমাজে তাকে খাতির করার লোকের অভাব হয়নি। কিন্তু তিনি যখন নিস্ব রিক্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুণেছেন, তখন খুব কম লোকই তার খবর নিয়েছেন। তিনি যদি অনেক সঞ্চিত অর্থ রেখে মারা যেতেন, তা হলে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে সম্ভবত এতটা বিরোধিতা দেখা দিত না।
নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন তার সময়ের সবচেয়ে বড় কবি। এমন কি, এক শতাব্দীর ব্যবধানে আজও কবি হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা কিছু হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মৃত্যুর ঠিক আগে এবং পরে তার প্রতি বাঙালি সমাজ অবিমিশ্র প্রশংসা অথবা প্রীতি প্রদর্শন করেনি।