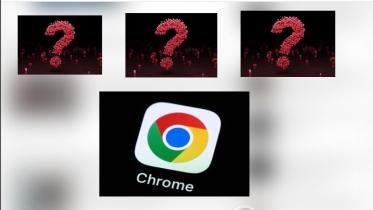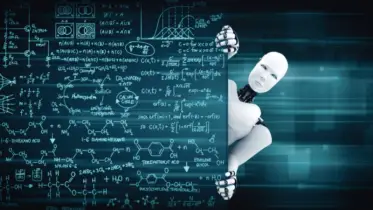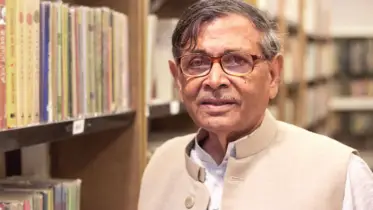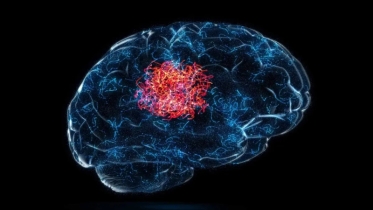জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা ভাবলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করেÑ ‘আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব/ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব’। ‘কোন কথা যে বলি!’ সিলেট অঞ্চলকে অসম থেকে আলাদা করে পূর্ববাংলার সঙ্গে ফিরিয়ে আনতে মুসলিম লীগের তরুণ কর্মী শেখ মুজিব বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। মাওলানাদের ফতোয়া উপেক্ষা করে সিলেটের গণভোট অনুষ্ঠানকালে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। আবার সেই মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্য কারাবরণ করেছেন। কারা-হাসপাতাল থেকে ভাষা-আন্দোলন চাঙ্গা রাখতে নির্দেশনা দিয়েছেন। পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন। বাঙালীর জাতিসত্তাকে শাণিত করতে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান উদ্ভাবন, বর্তমান রাজনৈতিক ভূখ-ের বাংলাদেশ নামকরণ, সত্তরের নির্বাচন; একাত্তরে সাতই মার্চের ভাষণ, ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা, পাকিস্তান কারাগারে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার প্রশ্নে অনমনীয়তা, দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ, অসাম্প্রদায়িক সংবিধান প্রণয়ন, শিল্প-সেবা-বীমা-প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ, বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দান, বিজ্ঞানমুখী শিক্ষানীতি গ্রহণ, আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণ ইত্যাদি; এর কোনো একটায় যদি ব্যত্যয় ঘটতো তবে আমাদের অবস্থান কোথায় থাকতো ভাবা যায় কি? ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আপাতত তাঁর বাংলা ভাষা-ভাবনার কথাই বলি। বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধুর বিবেচনায় বাংলা ভাষা আর বাঙালী জাতীয়তাবাদ যে অভিন্ন তা আজ আর কারো অজানা নয়।
বঙ্গবন্ধুর জন্মের বছরেই (১৯২০) ভারতের সাধারণ ভাষা (লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা) নির্ধারণের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক প্রবন্ধের মাধ্যমে হিন্দির বিরোধিতা করে বাংলা ভাষার দাবি উপস্থাপন করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মকৌশল নির্ধারণ করেন জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সে সময় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা বলে। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে বাংলার স্থান অষ্টম। বাংলার আগে যে ক’টি ভাষা আছে তারমধ্যে ভারতীয় কোনো ভাষা নেই। তবুও সুনীতিকুমার ‘হিন্দুস্থানী (হিন্দী উর্দু) ভাষার স্থান অবশ্য ভারতবর্ষে বাঙ্গালার উপরে’Ñএ কথা অস্বীকার করবার উপায় খুঁজে পাননি। রবীন্দ্রনাথও সুনীতিকুমারের সমর্থক রইলেন। ফলে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দেও শহীদুল্লাহর অব্যর্থ অবলোকন: ‘হিন্দু জাতীয়তার স্থানে বোঝেন বর্ণগত জাত। ... ধর্মগত জাতীয়তা মুসলমানদের অত্যন্ত প্রবল। মধ্যযুগে ইউরোপের খ্রিস্টানদের এইরূপ ছিল।’ শহীদুল্লাহ তাই তাঁর ‘এক জাতি গঠন’ প্রবন্ধে লিখেন, ‘আমরা দেশগত জাতীয়তা কামনা করি।’ অথচ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আমরা পেয়ে গেলাম ভাষাগত জাতীয়তাÑযা বঙ্গবন্ধুর সমগ্র সংগ্রামী জীবনের বীজমন্ত্র। তিনি এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই স্লোগান সৃষ্টি করলেন ‘জয়বাংলা’। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায় বঙ্গবন্ধুর ভাষা আন্দোলনে জড়িত হওয়ার প্রসঙ্গ আছে এভাবে- ‘শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি, ‘বাংলাদেশের আইডিয়াটি প্রথম কবে আপনার মাথায় এলো?’ ‘শুনবেন?’ তিনি (বঙ্গবন্ধু) মুচকি হেসে বললেন, ‘সেই ১৯৪৭ সালে। আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালীর এক দেশ।... দিল্লী থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাদের প্রস্তাবে।... তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নিই কিন্তু আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা।... হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলাভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞেস করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে, পাক বাংলা। কেউ বলে, পূর্ব বাংলা। আমি বলি, না বাংলাদেশ। তারপর আমি স্লোগান দিই, ‘জয়বাংলা’।... ‘জয় বাংলা’ বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জয় বা সাম্প্রদায়িতকার উর্ধে।’ এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল ফজল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন: ‘জয়বাংলা স্লোগান কে তুলে দিয়েছিল বাঙালীর মুখে? শেখ মুজিব নয় কি? জিন্দাবাদে সে জোর, সে চেতনা, সে উদ্দীপনা কোথায়? জয়বাংলা প্রদীপ্ত শিখা, জিন্দাবাদ ধার করা এক মৃত বুলি।’ এভাবে পাকিস্তানপন্থী পশ্চাৎপদতা আর ধর্মান্ধতাকে পেছনে ফেলে বাঙালীর জয়গানে মুখরিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাকে তিনি বাঙালীর সামনে আলোকিত করে তোলেন অবলীলায়।
ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় প্রণিত হয়েই ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮-এ ঢাকায় পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসে সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান এ কথা যেমন সত্য, তার চেয়েও বড় সত্য আমরা বাঙালী। এটা কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন, তা মালা-তিলক-টিকি কিংবা লুঙ্গি-টুপি-দাড়িতে ঢাকার জো নেই।’ এই সত্যকে সামনে রেখে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল সর্বধর্ম-বর্ণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে। অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের জোয়ারে উত্তাল একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-র ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। আজ কেউ অস্বীকার করেন না যে একুশের চেতনা থেকেই অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। প্রবল বামপন্থী বলে পরিচিত অধ্যাপক-লেখকও স্বীকার করেন: ‘দেশভাগ ঘটেছিল জাতি সমস্যা মীমাংসা না করতে পারার কারণে। ভরতবর্ষ ছিল বহুজাতির দেশ। কংগ্রেস বলেছে জাতি একটা, মুসলিম লীগ বললো একটা নয়, দুইটা। সেই ঝগড়াতেই দেশভাগ। জাতিগত বিভাজনটা ছিল ভাষাভিত্তিক; পুঁজিপন্থীরা তাকে দাঁড় করিয়েছিল ধর্মভিত্তিক হিসেবে। একাত্তরে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জয় ঘটেছে এবং তদ্বিপরীতে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সেটা একটা বড় অর্জন।’ এই অর্জন যে, বঙ্গবন্ধুর বদৌলতে বাস্তবায়িতÑতা মানতে বামপন্থী বাঙালীগণ আজও বড্ড কুণ্ঠিত। অথচ আরও আগে অধ্যাপক আবুল ফজল লিখেন, ‘বাঙালী জাতীয়তার জন্মদাতা আর সে চেতনার উদ্বোধক শেখ মুজিব।’ বঙ্গবন্ধু বিষয়ক আলোচনা তাই বাংলা ভাষা, বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে অবাস্তব। একইভাবে বাংলা ভাষা বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ বিষয়ক বিশ্লেষণও বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে অসম্ভব।
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গতিপথ বেয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরুর অব্যবহিত আগে ১৯৭১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘১৯৫২ সালের আন্দোলন কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এ আন্দোলন ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথেষ্ট রক্ত দিয়েছি। আর আমরা শহীদ হওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করব না এবার আমরা গাজী হব। সাত কোটি মানুষের অধিকার আন্দোলনের শহীদানদের নামে শপথ করছি যে, আমি নিজের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করব।’ ১১ মার্চ ১৯৭১ টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান সাতকোটি বাঙালীর নেতা, তাঁর নির্দেশ পালন করুন।’ এভাবে আওয়ামী লীগ নেতা থেকে বঙ্গবন্ধু বাঙালীর নেতাতে পরিণত হন। শুধু বাংলাদেশে নয়, ‘বিশ্ব ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতার দৃষ্টান্ত বিরল’। বাঙালী জাতীয়তাবাদের মন্ত্রেই বঙ্গবন্ধু জাগিয়ে তোলেনÑসমবেত করেন সাতকোটি বাঙালীকে। শামসুজ্জামান খানের ভাষায়: ‘বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে কয়েক শ বছরে যে বাঙালী জাতি গড়ে ওঠে তা ছিল একটি নৃগোষ্ঠী মাত্র। একই ভাষা ও সাধারণ আর্থ-সামাজিক জীবনধারার বিকাশের ফলে এবং শারীরিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক গড়নের সাজুয্যে ইে নৃগোষ্ঠী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বহু ক্ষেত্রের নানা মনীষীর স্ব স্ব ক্ষেত্রে চিন্তার নব নব বিন্যাসে একটি উন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। প্রায় তিন দশকের স্বাধিকার ও সুপরিকল্পিত স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তা একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই জাতিরই মূল ¯্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান।’ বাঙালীকে তিনি কেবল মুক্তি-স্বাধীনতা দেননি, বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করে গেছেন সংবিধানও। উনিশশো বাহাত্তরের ৪ নবেম্বর জাতীয় সংসদে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হবার মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। সহজ ও সাধারণ ভাষায় বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন: ‘ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকলের সঙ্গে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি। ...এই সংগ্রাম হয়েছিল যার উপর ভিত্তি করে সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালী, আমার বাঙালী জাতীয়তাবাদ।’ একই সঙ্গে পাকিস্তানপন্থী ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের বিরোধিতার কথা আন্দাজ করেÑআরব দেশগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন: ‘অনেক দেশে আছে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছেÑতারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর’। একটু সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেই দেখা যায় পৃথিবীতে একই ধর্মের লোক বিভিন্ন দেশে আছে কিন্তু তাদের ভাষা-সংস্কৃতির কোনো মিল নেই বলে তারা একই জাতি হতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর লেখায় এবং বিভিন্ন ভাষণে জাতীয়তাবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।
জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে আমাদের অবস্থান ফিরে দেখা যাক। বাংলা ভাষায় মধ্যযুগ পর্যন্ত জাতি বলতে প্রাণি-প্রজাতি, পেশাগত শ্রেণিপরিচয়, স্বগোত্র, বর্ণভেদ, শ্রেণি ইত্যাদি বোঝাত। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত ওগু¯েঁÍ ওসাঁর বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ -এ প্রথম জাতি মানে লেখা হয়: ‘নির্দিষ্ট ভূখ-ে বসবাসকারী অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক জনগোষ্ঠী; নেশন। একই অর্থে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেন: ‘জয়পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়’ (অক্ষয়, ১৮৪৮)। রবীন্দ্রনাথের বদৌলতে বাংলা ভাষা আধুনিক ভাব-ভাবনা প্রকাশে সক্ষম, সহজ-সুন্দর ও সাবলীল হয়ে উঠলেও তিনি প্রথম প্রথম ধর্মাবলম্বী অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার করেন। যেমনÑ‘এই তো খ্রিষ্টান জাতি!’ (রবীন্দ্র, ১৮৮১)। তবে বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) প্রেক্ষাপটে বাঙালী জাতীয়তাবাদ উন্মেষের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ ‘বাঙালী জাতি’ কথাটি ব্যবহার করে লিখেন: ‘বাঙালী জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না’ (রবীন্দ্র, ১৮৮৩)। এমনকি ‘জাতীয়তা’ এবং ‘জাতীয়তাবাদ’ শব্দ দুটিও রবীন্দ্রনাথের আগে আর কেউ বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথ লিখেন: ‘য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সংকটাপন্ন হইয়াছে’ (রবীন্দ্র, ১৮৯৫)। ‘আত্মসর্বস্ব পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের নিষ্ঠুরতা প্রলয়ংকার বিপদের দিকে চলিয়াছে’ (রবীন্দ্র, ১৯৩১)। উদ্ধৃতিগুলো বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (২০১৩) থেকে নেওয়া। অথচ বইটির ভূমিকায় এর সম্পাদক লিখেন: ‘জিঙ্গোবাদের প্রবল প্রভাবে জাতীয়তাবাদ শব্দটি এখন অতন্দ্র প্রহরীর সঙিনের মতো সর্বক্ষণ মাথা উঁচিয়ে থাকে, এবং তার নামে থেকে থেকে সারা বিশ্বে রক্তারক্তি হয়ে যায়। অথচ বিশ শতকের আগে বাংলা ভাষায় এ শব্দের অস্তিত্ব ছিলো না। এমনকি, নেশন, ন্যাশনালইজম ইত্যাদি ধার-করা শব্দ দিয়ে কাজ চালিয়েছেন, নেশন-স্বাতন্ত্র্যের মতো শব্দ তৈরি করেছেন, তবু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ শব্দটা ব্যবহার করেননি অথবা ব্যবহারের সুপারিশ করেননি।’ উদ্ধৃতি পাঠ থেকে পাঠক পেয়েছেন নিশ্চয়ই আমাদের প্রাজ্ঞ-প-িতগণ ‘জাতীয়তাবাদ’এর প্রতি কী প্রচ- বিদ্বেষ পোষণ করেন! আর তাঁদের পা-িত্যের স্বরূপ কেমন তাও স্পষ্ট হয় সম্পাদকের ভূমিকা আর সম্পাদিত বইয়ের ভেতরের বৈপরীত্ব অবলোকনে। অবশ্য আশার কথা এই যে, বিজ্ঞ বাঙালীগণের ব্যঙ্গমিশ্রিত তিরস্কারকে উপেক্ষা করে জাতীয়তাবাদ শব্দটি বাংলা ভাষায় এবং সাধারণ বাঙালীর মনে পুরোপুরি প্রচলিত শব্দ ও ধারণারূপে পাকাপোক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। তবে অনেকের কাছেই আজও জাতি শব্দের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট নয় বলেই এতো বিপত্তি। এই বিপত্তি দূর করতে প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর জাতি ও জাতীয়তাবাদ ভাবনার বিশ্লেষণ, অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।
বায়ান্নর পরবর্তী তেপ্পান্নর প্রথম একুশে উদযাপনের বিরাট শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিব। সন্দেহ নেই, ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছিল বামপন্থীরা। কিন্তু তাদের আন্দোলনের মধ্যে বাঙালী জাতীয়তাবাদী শক্তিটা ছিল না। এটা যোগ করেন বঙ্গবন্ধু। ভাষার দাবিতে বেড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে তিনি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন করেননি, অসীম অধ্যবসায় নিয়ে একে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। শেখ মুজিবের বিশেষ অবদান তিনি বাঙালীকে আত্মসচেতন করে তুলেছেন, বাঙালী জাতীয়তাকে দিয়েছেন ভাষা। অন্যভাবে বলা যায়, এই জাতীয়তাবাদী তরুণ নেতার মূল শক্তিটা ছিল মাতৃভাষা-প্রেম। বঙ্গবন্ধু ১৯৫২-র ২ অক্টোবর চীনের রাজধানী পিকিং-এ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীর ৩৭টি দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা করেন। সে ঘটনা তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং আমার দেখা নয়া চীন-এ লিখে রেখেছেন: ‘বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষার বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু কিছু জানে। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি। ... আমি দেখেছি ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন খুব ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করলেন চীনা ভাষায়। একটা ইংরেজি অক্ষরও তিনি ব্যবহার করেন নাই।
এমন আদর্শ আঁকড়ে যিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করলেন তাঁর সুযোগ্য কন্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ মন্তব্য: ‘ঢাকা শহরে গুলশান, বারিধারা বনানীতে ইদানীং দেখা যায় ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। বাংলা শিক্ষা একেবারেই দেওয়া হয় না। অর্থশালী, সম্পদশালী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। আর যদি হঠাৎ পয়সাওয়ালা হয় তাহলে তো কথাই নেই। মনে হয় বাংলা বলতে যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে।’ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পয়সাওয়ালা পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে; আর বাড়ছে বাংলা বলতে কষ্ট-হওয়া লোকসংখ্যা। ফলে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব যে ক্রমে সংকটে পতিত হচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন-সতর্ক হবার এবং ভাববার লোক ক্রমে কমছে।
চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের খসড়া নিয়ে আলোচনার সময় আবুল মনসুর আহমদকে শেখ মুজিব বলেন, কেবল ভোট লাভের জন্য একুশের নাম ব্যবহার করলে চলবে না, ভাষা আন্দোলনের দাবিগুলো, যেমন সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করা, বাংলা ভাষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, বাংলার লোকসাহিত্য ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ ইত্যাদি দাবি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত করতে হবে। শেখ মুজিবের দাবিতে ভাষা আন্দোলনের এই দাবিগুলো যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে যুক্ত হয়। পাকিস্তানের গণপরিষদে (২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো ছাড়াও তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দাবি করে বলেন: ‘আমরা ইংরেজি বলতে পারবো, তবে বাংলাতেই আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। যদি পরিষদে আমাদের বাংলায় বক্তৃতার সুযোগ না দেওয়া হয় তবে আমরা পরিষদ বয়কট করবো। ... বাংলাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করবো।’ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতা সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও শেখ মুজিব তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ‘এটা বাংলা ভাষাকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার এক ধাপ মাত্র। এই ভাষা জাতীয় জীবনে ও সরকারী কাজকর্মের সর্বস্তরে ব্যবহার না করা হলে, শিক্ষার মাধ্যম না করা হলে কেবল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কেতাবি স্বীকৃতি দ্বারা কোনো লাভ হবে না।’ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা থেকে আজ বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কিন্তু কেতাবি স্বীকৃতির গ-ি পেরিয়ে কতটুকু স্থান পেয়েছে বাংলা ভাষাÑসে প্রশ্ন পাঠকের প্রতি রইলো।
বঙ্গবন্ধু বাংলাকে ব্যবহারিক ভাষা করার ওপর বার বার জোর দিয়েছিলেন। এরপর তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক নতুন দিন পত্রিকায় নিজের নামে প্রকাশিত প্রবন্ধে লেখেন, ‘মোগলরা ফার্সিকে রাজভাষা করেছিল। সাত শ বছর তা রাজভাষা হিসেবে চালু থাকলেও জনজীবনে প্রতিষ্ঠা পায়নি। ভারতের মানুষ এক শ বছরের মধ্যে তা ভুলে গেছে। বাংলাকে তেমন সরকারী ভাষা করলে চলবে না। তার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা চাই। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক কার্যক্রমে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা দরকার। ওষুধের একটা প্রেসক্রিপশন বাংলায় লেখা যায় না। ভাষার এই দুর্বলতা দূর করা দরকার। আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কাজকর্মে ফার্সি, উর্দু, আরবির বদলে বাংলা ভাষা ব্যবহার সর্বজনীন করা দরকার।’
বঙ্গবন্ধুর সেই চিন্তার বাস্তবায়ন দূরের কথাÑআমরা ক’জন বাঙালী আজ সেই স্বপ্ন দেখার সৎসাহস রাখি তা ভাবতে হবে। ভাষার সঙ্গে ধর্মের যে কোনো সম্পর্ক নেই সেকথা মধ্যযুগের বাঙালী কবি আবদুল হাকিমও বলেছেন, যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ / নেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন॥’ (বঙ্গবাণী)। শেখ মুজিবও তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তে লিখেন: ‘উর্দু কি করে যে ইসলামিক ভাষা হল আমরা বুঝতে পারলাম না। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বিভিন্ন ভাষায কথা বলে। আরব দেশের লোকেরা আরবি বলে। পারস্যের লোকেরা ফার্সি বলে, তুরস্কের লোকেরা তুর্কি ভাষা বলে, ইন্দোনেশিয়ান লোকেরা ইন্দেনেশিয়ান ভাষায় কথা বলে, মালয়েশিয়ার লোকেরা মালয়া ভাষায় কথা বলে, চীনের মুসলমানরা চীনা ভাষায় কথা বলে।’
এভাবে তিনি প্রমাণ করে দেন ধর্মের সাথে ভাষা বা জাতীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মীয় ভাষা বা ধর্মীয় জাতি সম্পর্কিত ভুল ধারণা না ভাঙলে আমাদের মুক্তি অসম্ভব। ছয় দফা আন্দোলন চলাকালেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নাম আগের বাংলাদেশ রাখার ঘোষণা দেন এবং বলেন, ‘আজ থেকে আমাদের জাতি পরিচয় হবে বাঙালী।’ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী থাকাকালে বাঙালী ডাক্তারের মুখে বাংলা ভাষার অনুপস্থিতি তাঁকে পীড়া দেয়; তিনি লিখেন, ‘একদিন আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, বোধ হয় বাংলা ভুলে গেছেন তাই উর্দু বলেন।’
উনিশশো একাত্তরের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন- ‘আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার প-িতরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তারপর বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।’ ঐদিনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন : ‘মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর ¯্রােতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলেন।’ ভাষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর এই উপলব্ধি ও স্বচ্ছ ধারণা-ভাবনা পাঠে, তাঁকে একজন ভাষাতাত্ত্বিককের মতোই মনে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসাই তাঁকে ভাষা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। আর এই ভাষা-ভাবনার সাথে বাঙালী-সংস্কৃতিও যে জড়িত তার প্রমাণ পাই সে বছর ২৪ জানুয়ারিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট ঢাকাতে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন: ‘একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা।’ আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে আপন আয়নায় তাকালে দেখা যাবে বিনোদনের জন্যে আমরা হিন্দি ভাষা শিখছি, অর্থের জন্যে ইংরেজি আর ধর্মের জন্যে আরবি আওড়াচ্ছি। এতে করে আমরা একদিকে বাংলা ভাষা চর্চায় উদাসীন-অনগ্রসর; আরেক দিকে বাঙালী সংস্কৃতি ভুলে বিজতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে অস্থির-বধির হচ্ছি।
আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের আনন্দে আমরা ভুলে থাকিÑস্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেই ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছিলেন ‘ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও আমি বলব আমি বাঙালী, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।’ বাংলা ভাষার প্রতিটি রক্তস্নাত অক্ষরে মিশে আছে বঙ্গবন্ধুর নাম, আর সেই একেকটি অক্ষর একেকটি বাঙালীর জীবন। ১৯৭২ সালে দেশের প্রথম সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত ৭৩ জাতি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় বক্তৃতা দেন। কারণ তিনি বলতেন, ‘আমি বাঙালী, বাংলা আমার ভাষা। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা, বাংলার ইতিহাস, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার আবহাওয়া, তাই নিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ।’ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪) এবং বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা করার উদ্যোগ নেন। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশে^র দরবারে অন্য আঙ্গিকে পৌঁছে দেন তিনি। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালী হিসেবে যা কিছু বাঙালীদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়।’ সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলনে বঙ্গবন্ধু জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর লেখনীতে, বক্তব্যে রাজনৈতিক বাণীতে মাতৃভাষা বাংলার সারল্য-সাবলীলতা ও প্রকাশক্ষমতা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য সে-বাংলা ভাষাকে তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তবে আশার কথা ঘাতকের বুলেট-গ্রেনেট সে সংগ্রাম থামিয়ে দিতে পারেনি, বিরোধিতা ও বিরূপ বিশ্ববাস্তবতাকে মেনে নিয়েও বাঙালীর বাংলাদেশ বজায় রাখবার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের সংগ্রাম চলমান।
বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিরোধিতা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেও ছিল না এমন নয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার অবমাননা-অসম্মানে অসহ্য হয়ে ২৫ এপ্রিল ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ জারি করে লিখেন, ‘আমি কিছুদিন যাবৎ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের উপর্যুপরি সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী, অন্যান্য দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে এখনো বাংলা ভাষা ব্যবহার হচ্ছে না।...এখন থেকে আমার নির্দেশ রইল যে, সর্বস্তরে সকল দপ্তরে ও প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে।’ বঙ্গবন্ধুর অনেক আদেশের মতো এই আদেশও তখন সার্বিকভাবে কার্যকর করা যায়নি, এমনকি ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রচলনের পরেও না। তাইতো, ১৯৭৫-র ১২ মার্চ স্বয়ং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে আরও একবার আদেশ জারি করতে হয়। এ-আদেশে তিনি লিখেন: ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার তিন বছর পরও অধিকাংশ অফিস আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি যে তাঁর ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালী কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথি লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না।’ সে উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের আগেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল আততায়ীর হাতে বঙ্গবন্ধুকে প্রাণ দিতে হয়। বঙ্গবন্ধুর শত্রুরা যে বাংলা ভাষা ও বাঙালীরও শত্রু তার প্রমাণ তারা ‘জয়বাংলা’ স্লোগানকেও বর্জন করে, পাল্টে দেয় বাঙালী জাতীয়তাবাদকে। তবে আশার কথা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের সংগ্রাম থেমে নেই। কর্পোরেট ব্যবসায়ীও তাদের বাজার ধরে রাখতে বাংলা ভাষায় (এমনকি বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়) বিজ্ঞাপন প্রচারে বাধ্য হচ্ছে। বিদেশী গণমাধ্যমও দর্শক-শ্রোতা পাবার লোভে বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান-সংবাদ সম্প্রচার করছে। খুবই ক্ষীণধারায় হলেও বাঙালী সংস্কৃতির ¯্রােত আজও বহমান; এ শ্রোতধারাকে সজীবতা দানের সংগ্রামও চলছে অবিরাম।
বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাও উপলব্ধি করেন: ‘বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি ছেলেমেয়েদের নিজেদের ভাষা না শিখিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজি অবশ্যই শিখবে, ইংরেজি ও আরবি এই দুটো ভাষা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে জীবন-জীবিকার জন্য এই দুটো ভাষার প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি অন্য ভাষাও শিখতে পারি কিন্তু তা অবশ্যই মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। ... প্রতিটি স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।... আমাদের ভাষার চর্চা বাড়াতে হবে।... আমাদের আরও যতœবান হতে হবে আমাদের ভাষাকে বিকশিত করার জন্য, চর্চা করার জন্য। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে যত সুন্দর সহজভাবে বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি অন্য কোনো বিজাতীয় ভাষায় কি তা আমরা বুঝতে পারি? শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চা করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে অন্য ভাষাও শিখতে হবে।’ অথচ আমরা দেখি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সে উপলব্ধির আঠারো-উনিশ বছর পরও অনাবশ্যক অন্য ভাষা শেখা আর বাংলা ভাষা অবহেলা আরও বেড়েছে বৈ-কমেনি। অন্যদিকে জাপান-জার্মান-ব্রাজিল ও ভারতকে ডিঙ্গিয়ে আমরা বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করতে আগ্রহী আর নিজ দেশে ইংরেজি মিডিয়ামে প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা (বিসিএস) প্রচলনে পিছু হটিনি। নিজের দেশে বাংলাকে সর্বস্তরে দাপ্তরিক ভাষা না করে, প্রতি বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকা চাঁদা দিয়ে আমরা বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করেছি বলে মেকি উৎসবে মেতে উঠতে উদগ্রীব। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ আর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভ মুহূর্তে মন চায় কেউ বলুক- বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষা বিষয়ক আদেশ (১৯৭৫-র ১২ মার্চ জারিকৃত) অমান্য করা অপরাধ। তাহলে অচিরেই আমাদের অনেক বিচ্ছৃঙ্খলা বিদূরিত হবে; বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশে মুক্তির সুবাতাস বইবে। সর্বোপরি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাঙালী জাতীয়তাবাদ অমরতা পাবে, অমরতা পাবে বাংলাদেশ।