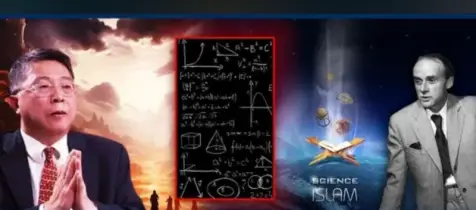ছবি: প্রতীকী
বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এই প্রযুক্তি দিয়ে এখন শুধু লেখালেখিই নয়, ভিডিও তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে "ডিপফেইক" নামে পরিচিত এক ধরনের ভিডিও এখন অনেক বেশি আলোচনায়। এই ভিডিওগুলোতে কোনো ব্যক্তির মুখ, কণ্ঠস্বর বা আচরণ কৃত্রিমভাবে তৈরি করে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন তা আসল বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এমন ভিডিও কি সত্য-মিথ্যা চেনা যায়?
সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে এখনকার অনেক এআই-ভিত্তিক ভিডিও থেকে আসল আর নকল আলাদা করা বেশ কঠিন। কারণ, আধুনিক প্রযুক্তি এতটাই উন্নত হয়েছে যে চোখে দেখে বোঝা প্রায় অসম্ভব। একজন রাজনীতিবিদের মুখে অন্য কথা বসানো, কোনো তারকার মুখ ব্যবহার করে ভুয়া ভিডিও তৈরি করা বা কোনো ব্যক্তির নামে অপপ্রচার চালানো—এসবই এখন সহজে সম্ভব। এই কারণে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং ভুল তথ্য বিশ্বাস করে বসে।
তবে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা একেবারে অসম্ভব নয়। কিছু কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ ধরনের ভিডিও বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, ভিডিওর ফ্রেমগুলো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে মাঝে মাঝে মুখমণ্ডলের হালকা বিচ্যুতি, অস্বাভাবিক চোখের পলক বা অঙ্গভঙ্গিতে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এ ছাড়া, শব্দের সঙ্গে ঠোঁটের নড়াচড়ার মিল না থাকা বা পটভূমির আলোছায়ার ত্রুটি থেকেও সন্দেহ জাগে।
তথ্য যাচাই করার বিশেষ সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন এখন বাজারে রয়েছে। গুগল, মাইক্রোসফট, মেটা সহ অনেক বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এআই-জালিয়াতি ঠেকাতে নানা প্রযুক্তি তৈরি করছে। কিছু ভিডিও বিশ্লেষণকারী টুল এমনভাবে কাজ করে যাতে ভিডিওর প্রতিটি ফ্রেম স্ক্যান করে দেখা যায় কোনো ডিজিটাল কারসাজি আছে কি না। আবার কিছু গবেষক ভিডিওর মেটাডেটা বিশ্লেষণ করে এটি আসল না নকল তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন।
এছাড়া, যেকোনো ভিডিও দেখার পর বিশ্বাস করার আগে তার উৎস যাচাই করা জরুরি। কে বা কারা ভিডিওটি শেয়ার করছে, প্রথম কোথা থেকে এটি এসেছে, সেটি নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্থা বা গণমাধ্যম কিনা—এসব বিষয় চিন্তা করতে হবে। সন্দেহজনক ভিডিও বেশি শেয়ার বা মন্তব্য পাওয়া মানেই তা সত্য নয়। বরং কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেয়, যাকে বলা হয় "ভুয়া প্রচারণা" বা "মিসইনফরমেশন"।
একইসঙ্গে আমাদের সচেতন হতে হবে। প্রযুক্তি যেমন সুবিধা দেয়, তেমনি বিপদও তৈরি করতে পারে। তাই যে কোনো ভিডিও বা তথ্য পাওয়ার পর একটু থেমে যাচাই করা ভালো। আমরা যদি সবাই একটু বেশি সচেতন হই এবং যাচাই-বাছাই করে তথ্য গ্রহণ করি, তাহলে সহজে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারব।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এআই ভিডিও সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো দরকার। তরুণ প্রজন্মকে শেখাতে হবে কীভাবে ভুয়া ভিডিও চেনা যায় এবং মিথ্যা তথ্য থেকে দূরে থাকতে হয়। কারণ প্রযুক্তির অপব্যবহার ঠেকাতে প্রযুক্তির সঠিক জ্ঞানই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।
এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও যে সবসময় মিথ্যা হবে তা নয়, আবার সব ভিডিও যে সত্য তা-ও নয়। কাজেই চোখ-কান খোলা রেখে যাচাই করে তথ্য গ্রহণ করাটাই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝে কাজ করা এবং অন্যদেরও সচেতন করা। প্রযুক্তি আমাদের হাতের মুঠোয়, কিন্তু বিবেচনা থাকা চাই মস্তিষ্কে।
এম.কে.