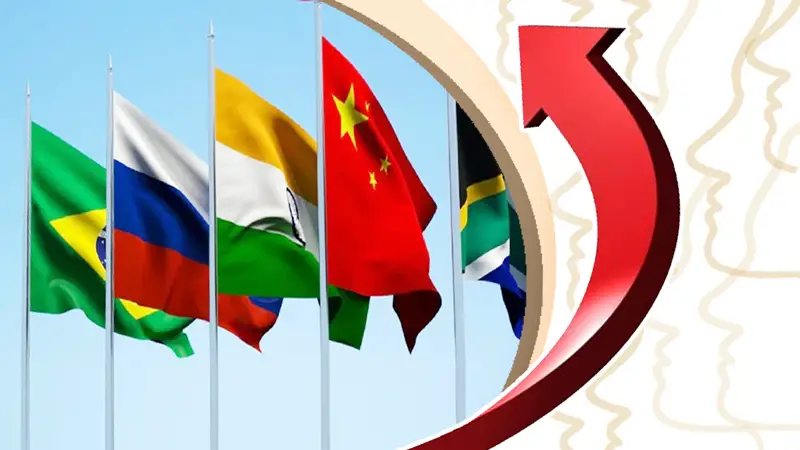
পঞ্চাশের দশক থেকে ১৯৮০’র দশকের শেষ দিক পর্যন্ত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
পঞ্চাশের দশক থেকে ১৯৮০’র দশকের শেষ দিক পর্যন্ত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমা বিশ্বের শত্রুতাকে বলা হতো শীতল যুদ্ধ কিংবা স্নায়ুযুদ্ধ। এখন আবারও নতুন এক শীতল যুদ্ধের সূচনার কথা উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু এই তুলনা কি যথার্থ? যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সংস্থা উইলসন সেন্টারের গবেষক মাইকেল কফম্যান বলেছেন, শীতল যুদ্ধ ছিল বিশ্বের দুই পৃথক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রেষারেষি, প্রতিযোগিতা। সে সময় দুই পরাশক্তি তাদের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তির বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিল। বিশ্বজুড়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের কারণে ঐ প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল তখন।
আরেকটি কারণ ছিল সামরিক শক্তির ভারসাম্য। তিনি আরও বলেন, এখনকার বিরোধের পেছনে সামরিক সেই ভারসাম্য নেই অথবা আদর্শের কোনো লড়াই নেই। এখনকার বিরোধের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে কিছু নেতার কিছু সিদ্ধান্ত, কৌশল এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে মতবিরোধ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, চীন ও রাশিয়া উভয়ের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র নতুন শীতল যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে। এই দ্বন্দ্বকে মার্কিন নেতারা গণতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদের সংঘাত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা গন্ধ শুঁকে যাচাইয়ের পরীক্ষায়ই ব্যর্থ হয়েছে।
এর কারণ হলো, তারা একদিকে চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনছেন, অন্যদিকে একই অভিযোগে অভিযুক্ত সৌদি আরবের মতো দেশের বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকছেন এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখছেন। এ ধরনের ভ-ামি ইঙ্গিত দেয়, যুক্তরাষ্ট্র আসলে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় নয় বরং বিশ্বব্যাপী তার আধিপত্য বিস্তারের মানসেই মানবাধিকার ইস্যুতে পক্ষপাতমূলকভাবে সোচ্চার হয়ে থাকে। চীন ও রাশিয়ার প্রভাবকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মিত্র দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতাদের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিডে বৈঠক করেছেন।
বিশেষ করে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোতে রাশিয়ার প্রভাবে যেভাবে একের পর এক অভ্যুত্থান হয়েছে, তা নিয়ে বাইডেন ও তার মিত্ররা উদ্বিগ্ন হয়ে এই ধারা কিভাবে ঠেকানো যাবে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আজকের দিনে পশ্চিমের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হলো চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়। পশ্চিমের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্রিকস, ওয়ারশ প্যাক্ট নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি এবং বার্লিন প্রাচীরের পতনের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নিজেদের মতো করে সংজ্ঞায়িত করা বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগতভাবে দ্বন্দ্বরত থেকেছে। এই দ্বন্দ্ব গোটা বিশ্বকে দুটো শিবিরে বিভক্ত করেছিল। এর জের ধরে বিশ্বে স্বাধীনতা চাওয়া দেশের সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা চাওয়া দেশের সংখ্যা ছিল ৫০।
১৯৮৯-৯১ সালে সেই সংখ্যা দেড়শ’র বেশি হয়ে দাঁড়ায়। যখন দুটি শক্তির মিথস্ক্রিয়া জারি ছিল, তখন মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব সামনের দিকে উঠে আসছিল। স্বাধীনতার সংগ্রামগুলো প্রায়ই প্রক্সিযুদ্ধে রূপ নিচ্ছিল এবং দেশগুলোকে হয় যে কোনো একটি শিবিরে যোগ দিতে হচ্ছিল, নয়তো তাদের নিজেদের জোটনিরপেক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে বাধ্য করা হয়েছিল। বর্তমানে ঠিক একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে শক্তিধর ও সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের মুখোমুখি হয়ে নিজ মিত্রদের নিয়ে বেজিংবিরোধী কৌশল অবলম্বন করছে।
সেই কৌশলের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা অর্থনৈতিকভাবে সম্পর্কছেদ করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন বাতিল করার নীতি গ্রহণ করেছে। এটি আদতে শীতল যুদ্ধের সময়কার নিয়ন্ত্রণ নীতিরই একটি অর্থনৈতিক সংস্করণ।
একদিকে যুক্তরাষ্ট্র আদর্শগত মেরুকরণের মধ্য দিয়ে আদল পেতে শুরু করা দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধের আশঙ্কা করছে। অন্যদিকে চীন বৈশ্বিক বিভক্তির ওপর বাজি ধরে সেটিকেই কাজে লাগাতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, চীন অ-পশ্চিমা দেশগুলোকে জি-৭ কিংবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো পশ্চিমা আধিপত্যের অধীনে থাকা সংস্থাগুলোর বিকল্প কিছু গড়ার চেষ্টা করছে। চীন একটি বহু মেরুভিত্তিক বিশ্ব চায়। চীন জানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন শিবিরের সঙ্গে তারা লড়াইয়ে পেরে উঠবে না। তবে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তারা অন্তত একটি খ-িত বৈশ্বিক ব্যবস্থায় একটি পরাশক্তি হিসেবে জায়গা করে নিতে পারবে।
মার্কিন নেতাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা জারি থাকার পরও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও মার্কিন ব্লক থেকে খ-িত হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। সম্প্রতি সবচেয়ে বড় চমক ছিল ব্রিকসের এই ঘোষণা : আর্জেন্টিনা, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত- এই ছয় দেশ আগামী বছরের শুরুতেই পূর্ণ সদস্য হয়ে উঠবে। চীনের নেতাদের মনে এটি নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই যে ব্রিকসের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো অধিকতর পশ্চিমাবিরোধী হয়ে উঠবে। এতে চীন তার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোবে। ব্রিকসে যোগদান এই দেশগুলোর জন্য কাজের স্বাধীনতা বাড়াবে।
এর মাধ্যমে তাদের অর্থায়নের বিকল্প উৎস বাড়বে। প্রকৃত অর্থেই মার্কিন ডলারের বিকল্প হিসেবে অন্য মুদ্রার ব্যবহার বাড়বে এবং বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। এই ধরনের সংগঠনের মাধ্যমে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা তৈরির স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, যা পশ্চিমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। তার মানে সেটি হবে চীনের ওপর নির্ভরশীল। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার বড় কারণ। তাই নতুন একটি শীতল যুদ্ধাবস্থা অনেকটাই ঘনিয়ে এসেছে। বিজ্ঞজন ও বিশ্লেষকরা বৈশ্বিক দক্ষিণের উত্থানের আলোচনা করছেন কিছুদিন ধরে। বিশেষত ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের কাল থেকে।
পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে অনেক দেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ধরে রেখে বৈশ্বিক শক্তির পুনর্বণ্টন ঘটাচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির ভরকেন্দ্র আশির দশকে ছিল আটলান্টিককেন্দ্রিক।
অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে। পরে সেটি ৪৮০০ মাইল সরে গিয়ে ২০০৮ সালের দিকে তুরস্কের ইজমিরে সরে যায়। ২০৫০ সালে এই ভরকেন্দ্র হয়তো ভারত ও চীনের মধ্যে কোথাও পৌঁছাবে। নতুন এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর সামনে নতুন বিকল্প হাজির করেছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে বিরোধ কিংবা প্রবল প্রতিযোগিতার সময় কী আচরণ করতে হবে, কী অবস্থান নিতে হবে- তা নিয়ে তারা এখন নতুন করে ভাবার অবকাশ পেয়েছে। শীতল যুদ্ধের সময় বিশ্বকে মোট তিনটি শিবিরে ভাগ করা হতো- পশ্চিমা ব্লক, সোভিয়েত ব্লক এবং কথিত জোট নিরপেক্ষ ব্লক।
শীতল যুদ্ধের পর পশ্চিমা ব্লকে থাকা দেশগুলো একটি নয়া ব্যবস্থার দিকে গেল, যেটিকে তারা বলছে উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা। নতুন এই একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় পুরনো প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন প্রতিষ্ঠান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ধরে নেওয়া হলো গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং বাণিজ্যিক উদারীকরণ সব শত্রুকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারবে। বিশ্বে নতুন শক্তির উত্থান বলছে যে সেটা হয়নি। ওয়াশিংটন যে বিশ্বব্যবস্থা জারি করেছে, তার প্রতিও বেজিং আস্থাশীল নয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় এই ব্যবস্থার সৃষ্টি। তার কিছু মিত্রও এই ব্যবস্থা থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়।
চীনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র হিংসার বশে এই প্রতিষ্ঠানগুলোয় তাদের বানানো নীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ফোরামে চীনের ভোটদানের ক্ষমতা অর্থনৈতিকভাবে সম অবস্থানে থাকা অন্য দেশগুলোর তুলনায় বেশ কম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশ্বব্যাংকে চীনের ভোটের হিস্যা মাত্র ৫ শতাংশ।
চীন ধারাবাহিকভাবে তার নিজের ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর ভোটের হিস্যা বাড়ানোর দাবি করে আসছে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। বৈশ্বিক দক্ষিণকে চীনের এই উদ্যোগ প্রলুব্ধ করেছে। কারণ, তারা মনে করছে বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোয় তাদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তারা খুব একটা পাত্তাও পায় না। আরও যে বিষয় আছে তা হলো- ব্রিকসের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে শীতল যুদ্ধের মতো কোনো একটি শিবিরের অনুসারী হতে হবে এমন কোনো প্রতিশ্রুতির বালাই নেই। অনেকটা আকস্মিকভাবেই ব্রিকসের সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ।
ব্রিকসে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিকভাবে খুব সুবিধা পাবে, এমন আশার কথা কারও কাছ থেকে শুনিনি। তখন এটা অনেকটাই পরিষ্কার ছিল যে, রাজনৈতিক কারণেই এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই রাজনৈতিক কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশের সামনের নির্বাচন। আমরা চাই বা না চাই, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গেছে। সেদিক থেকে দেখলে বাংলাদেশের এ সিদ্ধান্তের পেছনে শুধু রাজনৈতিক নয়, ভূরাজনৈতিক বিবেচনাও কাজ করেছে। বিশ্বের দূরবর্তী দেশগুলোর ওপর শক্তি খাটানো কিংবা দূরবর্তী অঞ্চলের বন্ধুদের নিরাপত্তা সহযোগিতা দেওয়ার মতো সামরিক শক্তি চীনের নেই।
জোটের রাজনীতিতে তাদের ইতিহাস সুখকর নয়। বেজিংয়ের অংশীদার আছে অনেক, এমনকি কৌশলগত অংশীদারও। কিন্তু তাদের কোনো মিত্র নেই। সম্প্রতি ব্রিকসভুক্ত দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার নেতারা জোহানেসবার্গে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পশ্চিমাদের খবরদারির তীব্র সমালোচনা করেছেন। শীতল যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা এর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা যে বাস্তব অবস্থায় চলে এসেছে, এখন তার প্রমাণ মিলছে।
লেখক : যুক্তরাজ্য প্রবাসী গবেষক








