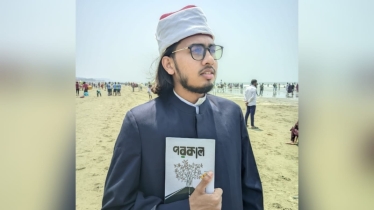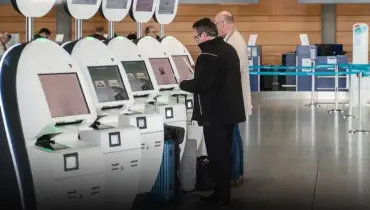ছবি: সংগৃহীত
মেধা হলো একটি উপকারী ও প্রতিরক্ষামূলক শক্তি, যা ভাল কাজ বা চিন্তার ফলে জমা হয়। কেতাবি ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, যে কর্মদক্ষতা অথবা চিন্তক দক্ষতা জন্মসূত্রে পাওয়া যায়, তাকে মেধা বলা হয়। একটি বিশেষ প্রাকৃতিক ক্ষমতা বা প্রবণতা, সাফল্য বা সাফল্যের ক্ষমতাকেও মেধা বলা যায়। উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ স্কুলে অ্যাপটিটিউড টেস্ট হয়, কার কোন দিকে মেধা আছে তা বের করার জন্য।
বাংলাদেশে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, কর্মক্ষেত্রে মেধাবীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ না থাকা, নিরাপত্তাহীনতা, ফসলের সুষম বণ্টন না হওয়াসহ অনেক কারণে প্রতিবছর হাজারো মেধাবী বিদেশে পাড়ি দিয়ে আর কখনো দেশে ফেরেন না। এর মাঝেও অনেক মেধাবী নিজ দেশে মেধা বিকাশ করার মানসিকতা নিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। মেধাহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দাপটে কর্মক্ষেত্র বিষিয়ে উঠলেও, নেওয়া হচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা। অন্যদিকে, এখানে তুচ্ছ বিষয়ে নেওয়া হচ্ছে মেধাবী, সৎ ও বাক্পটু অনভিজ্ঞ নবীন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অকল্পনীয় সব ব্যবস্থা। যেমন সাম্প্রতিক সময়ে একজন সহকারী কমিশনার, যার নাম তাপসী তাবাসসুম উর্মি, ফেসবুকে কয়েকটি শব্দ পোস্ট করার দায়ে তার বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ৭ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল তারিখে পালন করা হয়। জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ‘বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা’ ২০০০ সালে প্রথমবারের মতো এই দিবসটি পালন করেছিল। দৈনন্দিন জীবনের ওপর মেধাসম্পদের কৃতিস্বত্ব (পেটেন্ট), কপিরাইট, বাণিজ্যিক মার্কা (ট্রেডমার্ক) এবং ঔद्योगিক ডিজাইনের প্রভাবের বিষয়ে সজাগ করাই এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য।
মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিদ্যমান একটি আইনি অধিকার, যাতে কোনো মৌলিক সৃষ্টিকর্মের মূল সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কোনো পক্ষ সেই সৃষ্টিকর্ম ব্যবহার করতে পারবে কি না, কিংবা কোন শর্তে ব্যবহার করতে পারবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ মূল সৃষ্টিকর্তাকে একক ও অনন্য অধিকার প্রদান করা হয়।
মেধাস্বত্ব সাধারণত একটি সীমিত মেয়াদের জন্য কার্যকর হয়। ঐ মেয়াদ শেষে কাজটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্র বা জনক্ষেত্রের (পাবলিক ডোমেইন) অন্তর্গত হয়ে যায়। মেধাস্বত্ব ছাড়াও আরেক ধরনের মেধাসম্পদ অধিকার বা স্বত্ব আছে, সেটি হলো শিল্প সম্পত্তি স্বত্ব। এই অনন্য অধিকারগুলি পরম অধিকার নয়, বরং এগুলির সীমাবদ্ধতা ও ব্যতিক্রম আছে (যেমন, ন্যায্য ব্যবহার বা ফেয়ার ইউজ)। আমরা হয়তো ভাবতে পারি, উপকরণটি যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি অর্থনৈতিকভাবে ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির কারণে লাভবান হয়েছেন। বাস্তবতা হলো, মেধাস্বত্বের কারণে ব্যবহারকারী বেশি উপকৃত হচ্ছেন। কারণ, মেধাস্বত্ব ব্যবহারের নিয়ম মেনে চলাও একটা স্বত্ব।
বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধাভিত্তিক সৃষ্টিকর্মটি যদি কোনো গ্রন্থ হয়, তাহলে বাংলায় তার মেধাস্বত্বকে বিশেষ একটি পরিভাষা "গ্রন্থস্বত্ব" দ্বারা নির্দেশ করা হয়। এছাড়া, গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য রচনার জন্য সাধারণভাবে "লেখস্বত্ব", "রচনাস্বত্ব" ইত্যাদি পরিভাষাও প্রচলিত। ব্যাপক পরিসরে ছাপাখানার প্রসার হওয়ার আগে পর্যন্ত মেধাস্বত্ব উদ্ভাবিত হয়নি। আঠারো শতকের শুরুর দিকে ছাপাখানাগুলোর একচেটিয়া আচরণের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে ব্রিটেনে এরকম একটা আইনের ধারণা জন্ম নেয়।
ভারতীয় উপমহাদেশে কপিরাইট আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল ১৯১২ সালে। বাংলাদেশে কপিরাইট আইন প্রণয়ন করা হয় ২০০০ সালে এবং সর্বশেষ তা ২০০৫ সালে সংশোধন করা হয়।
আমরা একদিকে যেমন নিজেদের মেধা বিকাশ করতে সক্ষম হচ্ছি না, অন্যদিকে আমাদের মেধাসম্পদকেও রক্ষা করতে পারছি না অথবা রক্ষা করার প্রচেষ্টাও গ্রহণ করছি না। যার প্রকৃষ্ট কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।
আমরা বড় বড় স্বপ্ন দেখি। বাংলাদেশ জাপান হয়ে গেছে, সিঙ্গাপুর হয়ে গেছে, আরও কত কী কল্পনা করি। এ স্বপ্নে বিভোর হয়ে, অনেক ব্যয়বহুল জাপানি ইঞ্জিনের সংযুক্ত পার্টস নষ্ট হলে, যেহেতু মূল ইঞ্জিন তৈরি করার যোগ্যতা আমাদের হয় নাই, তাই নিজেদেরকে জাহির করার জন্য ঢাকার জিঞ্জিরায় নিজেরা পার্টস তৈরি করে জাপানি ইঞ্জিনের সঙ্গে জুড়ে দিই। এর ফলাফল হলো, অকালে মূল ইঞ্জিনটি বিকল হয়ে যাওয়া। আমরা পারি না—এই কথাটি স্বীকার করতে না পারার কারণে মূলত আমরা পারি না। আমরা ‘পারি না’ বলতে না চাইলেও, ‘পারিব না’ শব্দটি যেন আমাদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, যারা পারে, আমরা তাদের মেধাস্বত্বকেও সম্মান জানাতে পারি না। অন্যদিকে পৃথিবীর অনেক দেশ রয়েছে, যারা নিজেরা আবিষ্কার বা উৎপাদন না করতে পারলেও, মেধাস্বত্ব মেনে অন্যদের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার করেও আজ পৃথিবীর উন্নত প্রথম দশটি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন।
বাংলাদেশের বিখ্যাত টাঙ্গাইল শাড়ির উৎস পশ্চিমবঙ্গ বলে দাবি করেছে ভারত। দেশটির সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ভিত্তিহীন এ দাবি করা হয়েছে। তবে দেশটির এই অদ্ভুত দাবি ব্যাপক বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে পড়েছে। টাঙ্গাইল শাড়ির একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। এটি বাংলাদেশের অন্যতম পুরনো একটি কুটির শিল্প। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই শাড়ি বুননের ইতিহাস। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এর ব্যাপক প্রসার হয়। এছাড়া নাম থেকেই স্পষ্ট টাঙ্গাইল শাড়ির উৎপত্তি কোথায়। বিখ্যাত টাঙ্গাইল শাড়ির উৎস বাংলাদেশ হলেও, সম্প্রতি এর ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই স্বত্ব) বাগিয়ে নিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরে অবশ্য বাংলাদেশ সরকারের হুঁশ ফেরে এবং জিআই স্বত্ব গ্রহণ করে।
সুন্দরবনের মধুর ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বত্ব পেয়েছে ভারত। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব বিষয়ক সংস্থা ‘ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অর্গানাইজেশন’ (ডব্লিউআইপিও)-এর কাছ থেকে এ স্বত্ব পেয়েছে প্রতিবেশী দেশটি। অথচ সুন্দরবনের বেশিরভাগ অংশ যেমন বাংলাদেশের ভিতরে, তেমনি মধু আহরণের দিক দিয়েও এগিয়ে বাংলাদেশ।
১০ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের ৬৬ ভাগ অর্থাৎ ৬ হাজার ৫১৭ বর্গকিলোমিটার জায়গা বাংলাদেশের। আর ৩ হাজার ৪৮৩ বর্গকিলোমিটার জায়গা ভারতের। এই বনে মধু সংগ্রহের দিক থেকেও এগিয়ে বাংলাদেশ। গত বছরও ৪০০ মেট্রিক টন মধু আহরণ হয়েছে সুন্দরবন থেকে। সেখানে ভারতের আহরণ মাত্র ১৫৭ মেট্রিক টন। এই সুন্দরবন এবং মধু ভারত সরকার একচেটিয়াভাবে তাদের বলে বিশ্বে প্রচার করে। তারপরও বাংলাদেশ ভৌগোলিক নির্দেশক সনদ না পাওয়াকে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা হিসেবে দেখা হয়। এতে ক্ষিপ্ত সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিতরা। জিআই না পেলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের মধুর অবস্থান স্থিরিতেও সংকট হবে বলে তাদের আশঙ্কা। পরে অবশ্য বাংলাদেশের বন বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
টাঙ্গাইল শাড়ি এবং সুন্দরবনের মধু—এই গৌরবউজ্জ্বল আমাদের ইতিহাস থাকলেও, বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যালয় এসব বিষয়ে উদাসীন ছিল।
কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে, পণ্যগুলো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। এই পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে। ওই অঞ্চল বাণিজ্যিকভাবে পণ্যটি উৎপাদন করার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা পায়।
আমাদের সর্বক্ষেত্রে অবস্থা হয়েছে, ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মরে যাওয়ার মত। বাংলাদেশের বিদেশি মিশনগুলোর অনেক দুর্বলতা রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ ৫৪ বছর অতিক্রম করলেও এখনো অনেক দেশের নাগরিককে বাংলাদেশি পরিচয় দিলে, তারা প্রশ্ন করে—ইন্ডিয়া নাকি? অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে আমরা এখনো পরিচয় সংকটে রয়েছি। তাহলে প্রতিবছর হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি নিয়োগ করে কী লাভ হচ্ছে? টাকাগুলো তবে কি জলে ফেলা হচ্ছে না?
এ অবস্থায় বাংলাদেশের সকল ঐতিহ্যবাহী মেধাসম্পদ অপপ্রচার করার মাধ্যমে ভারত অথবা অন্য কোনো দেশ যেন নিজেদের দাবি করে, নিজ দেশে এবং বহির্বিশ্বে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে না পারে, এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং বিভাগকে সতর্ক থাকতে হবে। তাহলে আমাদের মেধাসম্পদ রক্ষা পাবে।
লেখক: প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী সংগঠন ফ্রিডম ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি অ্যালকোহল।
আসিফ